আলাপন I ‘বাংলা দ্বিখন্ডিত হওয়ার ঘটনা অভিশাপের মতো’ -প্রতীতি দত্ত (ঘটক)
 বাঙালির বড় একটা অংশকে উদ্বাস্তু করেছিল ১৯৪৭-এর বাংলা ভাগ। পশ্চিমবঙ্গ থেকে শিকড় ছিন্ন করে এপার বাংলায় চলে আসতে হয়েছিল বহু বাঙালি মুসলমান পরিবারকে। তেমনই এপার বাংলার অনেক বাঙালি হিন্দু পরিবারকে চলে যেতে হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গে। বাংলা চলচ্চিত্রের কিংবদন্তি ঋত্বিক কুমার ঘটক, তাঁর বড় ভাই, সাহিত্যিক মণীশ ঘটক, ঋত্বিকের যমজ বোন প্রতীতি ঘটক, মণীশ ঘটকের কন্যা মহাশ্বেতা দেবীসহ গোটা ঘটক পরিবারের অধিকাংশ ব্যক্তি অনেকের মতোই এপার বাংলা ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন ওপারের পশ্চিমবঙ্গে। কিন্তু পরে নিজের দেশে ফিরে আসেন প্রতীতি। তাঁর বিয়ে হয় ভাষা সংগ্রামী ও পূর্ব পাকিস্তানের মন্ত্রী ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের পুত্র সঞ্জীব দত্তের সঙ্গে। পুত্র রাহুল দত্ত ও কন্যা আরমা দত্তকে নিয়ে এই বাংলাতেই তিনি থেকে যান। মাঝে কিছুদিন ফের আগরতলা, কলকাতা ও পন্ডিচেরিতে তিনি অবস্থান করেছিলেন। কিন্তু নিজের মাটিকে ছেড়ে যাননি। তাঁর চোখের সামনে ১৯৭১ সালের ২৯ মার্চ কুমিল্লার নিজ বাসভবন থেকে পাক হানাদার বাহিনী ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ও তাঁর ছোট ছেলে দীলিপ কুমার দত্তকে ধরে নিয়ে যায়। বাংলা ভাষা, সংস্কৃতি ও বাংলাদেশ গড়ে ওঠার সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে রয়েছে প্রতীতি দেবীর পিতৃগৃহ ও শ্বশুরবাড়ির পরিবার। তিনি নিজেও নানা সাংস্কৃতিক ও সামাজিক কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত থেকেছেন। ঋত্বিক, ধীরেন্দ্রনাথ ও বাংলা প্রসঙ্গে প্রতীতি দেবীর সঙ্গে ক্যানভাসের এবারের আলাপন। সঙ্গে ছিলেন তাঁর কন্যা আরমা দত্ত, যিনি বাংলাদেশের মানবাধিকার কমিশনের সাবেক সদস্য ও বাংলাদেশে নারী ক্ষমতায়নের নানা কর্মকান্ডে যুক্ত। তাঁদের এই সাক্ষাৎকার নিয়েছেন অতনু সিংহ
বাঙালির বড় একটা অংশকে উদ্বাস্তু করেছিল ১৯৪৭-এর বাংলা ভাগ। পশ্চিমবঙ্গ থেকে শিকড় ছিন্ন করে এপার বাংলায় চলে আসতে হয়েছিল বহু বাঙালি মুসলমান পরিবারকে। তেমনই এপার বাংলার অনেক বাঙালি হিন্দু পরিবারকে চলে যেতে হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গে। বাংলা চলচ্চিত্রের কিংবদন্তি ঋত্বিক কুমার ঘটক, তাঁর বড় ভাই, সাহিত্যিক মণীশ ঘটক, ঋত্বিকের যমজ বোন প্রতীতি ঘটক, মণীশ ঘটকের কন্যা মহাশ্বেতা দেবীসহ গোটা ঘটক পরিবারের অধিকাংশ ব্যক্তি অনেকের মতোই এপার বাংলা ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন ওপারের পশ্চিমবঙ্গে। কিন্তু পরে নিজের দেশে ফিরে আসেন প্রতীতি। তাঁর বিয়ে হয় ভাষা সংগ্রামী ও পূর্ব পাকিস্তানের মন্ত্রী ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের পুত্র সঞ্জীব দত্তের সঙ্গে। পুত্র রাহুল দত্ত ও কন্যা আরমা দত্তকে নিয়ে এই বাংলাতেই তিনি থেকে যান। মাঝে কিছুদিন ফের আগরতলা, কলকাতা ও পন্ডিচেরিতে তিনি অবস্থান করেছিলেন। কিন্তু নিজের মাটিকে ছেড়ে যাননি। তাঁর চোখের সামনে ১৯৭১ সালের ২৯ মার্চ কুমিল্লার নিজ বাসভবন থেকে পাক হানাদার বাহিনী ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ও তাঁর ছোট ছেলে দীলিপ কুমার দত্তকে ধরে নিয়ে যায়। বাংলা ভাষা, সংস্কৃতি ও বাংলাদেশ গড়ে ওঠার সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে রয়েছে প্রতীতি দেবীর পিতৃগৃহ ও শ্বশুরবাড়ির পরিবার। তিনি নিজেও নানা সাংস্কৃতিক ও সামাজিক কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত থেকেছেন। ঋত্বিক, ধীরেন্দ্রনাথ ও বাংলা প্রসঙ্গে প্রতীতি দেবীর সঙ্গে ক্যানভাসের এবারের আলাপন। সঙ্গে ছিলেন তাঁর কন্যা আরমা দত্ত, যিনি বাংলাদেশের মানবাধিকার কমিশনের সাবেক সদস্য ও বাংলাদেশে নারী ক্ষমতায়নের নানা কর্মকান্ডে যুক্ত। তাঁদের এই সাক্ষাৎকার নিয়েছেন অতনু সিংহ
ক্যানভাস: প্রতীতি দেবী, আপনি ঘটক পরিবারের ঋত্বিকের প্রজন্মের জীবিত একমাত্র সদস্য, দত্ত পরিবারেরও একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। আপনার জীবনের কিছু স্মৃতি ভাগ করে নিতে চাই।
প্রতীতি দেবী: আমি আর ঋত্বিক একসঙ্গে বড় হয়েছি। আমরা দুজনেই প্রচন্ড দুরন্ত ছিলাম। আমি বেশি। ঋত্বিক একটু বড় হয়ে শান্ত হয়ে গিয়েছিল। ক্লাস সেভেনে পড়ার সময় থেকে নাটক, সাহিত্য এসবের প্রতি তার আগ্রহ তৈরি হয়েছে। ওই সময়ে সে নাটক লেখাও শুরু করেছিল। যা হোক, আমার যখন ৪ বছর বয়স, তখনকার একটা ঘটনা মনে পড়ছে। বাবা তখন ময়মনসিংহে, মা নিজেই আমাকে আর ঋত্বিককে মিশনারি স্কুলে ভর্তি করাতে নিয়ে গেলেন। ওই স্কুলের প্রিন্সিপাল ছিলেন এক ব্রিটিশ মহিলা, মিস হগবেন। উনি স্কুলের গেটে ছুটে এসে মাকে ভেতরে নিয়ে গেলেন। মা ওনার সঙ্গে কথা বলছেন, এমন সময় আমি আর ঋত্বিক টেবিলের নিচে… কথা শেষ হওয়ার পর টেবিল থেকে উঠে উনি মাকে বললেন, আপনি যে বলছেন আপনার ছেলেমেয়েদের ‘এ-বি-সি-ডি’ শেখানো যাচ্ছে না, এই দেখুন ওরা আমার মোজার গায়ে এ-বি-সি-ডি লিখে রেখেছে। এরপর তিনি মাকে বললেন, এদেরকেই আমার দরকার। পরে উনি যখন স্কুলের চাকরি ছেড়ে দেন, তখন আমাদের বাড়িতেও এসেছেন, থেকেছেন, আমাদের বাড়িতে সারা রাত গান গাইতেন, আমরা ভাবতাম মা গাইছেন। আমার মা-দিদিরা খুব ভালো গান গাইতেন, তাই ভাবতাম মা বোধ হয় গাইছেন। কিন্তু দেখলাম মিস গান গাইছেন, ইংরেজি আর ফরাসি ভাষায় গান গাইতেন উনি। এমনকি একটু ভাঙা ভাঙা বাংলাতেও উনি অসম্ভব ভালো গান গাইতেন। ওঁর কাছ থেকে আমি আর ঋত্বিক কী ভালোবাসাই যে পেয়েছি, তা আজও ভুলবার নয়। মহাশ্বেতাও ওঁর স্নেহ পেয়েছে। মৃত্যুর কিছুদিন আগে মহাশ্বেতা আমাকে বলেছে, ওই পুরোনো জায়গাগুলো একবার দেখে যেতে ইচ্ছে করে। মিস হগবেনের কথা ওরও মনে পড়তো। আর একটা কথা মনে পড়ছে, আমি ছবি তুলতে পছন্দ করতাম না। মনে হতো আমার অন্য ভাইবোনদের তুলনায় আমি কম সুন্দর। কিন্তু আমার ভাইয়েরা এসব শুনতো না, তারা কত আদর করতো আমাকে! ঋত্বিক হয় জোর করে, নয়তো লুকিয়ে লুকিয়ে আমার ছবি তুলতো।
ক্যানভাস: পূর্ব বাংলা থেকে আপনার গোটা পরিবারের বড় একটা অংশকে পশ্চিমবঙ্গে চলে যেতে হয়েছিল। উদ্বাস্তু হওয়ার এই বেদনা ঋত্বিক সারা জীবন বহন করেছেন। আচ্ছা, আপনার বাবা-মায়ের পরিবারের সদস্যরা ৪৭-এ ওপারে চলে যাওয়ার পর এই বাংলায় নিয়মিত আসতেন?
প্রতীতি দেবী: না, সে সুযোগ ছিল না। বাংলাদেশ স্বাধীনের পর ‘তিতাস একটি নদীর নাম’-এর শুটিং শুরু হওয়ার কিছুদিন আগে থেকে ফের এখানে ঋত্বিকের যাতায়াত শুরু হয়। আসলে আমার বাবা-মা কলকাতায় যেতে চাননি। কিন্তু রাজশাহীর বাড়িতে সব ফেলে রেখে ওঁদের চলে যেতে হয়েছিল।

১৯৭১ সালের ৩ এপ্রিল, সীমান্ত পার হয়ে আগরতলায়, সংবাদ সম্মেলনে প্রতীতি দেবী ও আরমা দত্ত।
ক্যানভাস: ‘তিতাস’-এর সূচনার কথা যদি একটু বলেন…
প্রতীতি দেবী: ‘তিতাস একটি নদীর নাম’ করার কথা ঋত্বিক ভাবেনি। ‘পদ্মা নদীর মাঝি’র ওপর ছবি করার ইচ্ছা নিয়ে ঢাকায় এসেছিল। তখন ১৯৭২ সাল। মাত্র কয়দিন হলো দেশ স্বাধীন হয়েছে, এই অবস্থায় ঋত্বিক ঢাকায় এলো। কিন্তু তখন ঢাকা থেকে রাজশাহী যাওয়ার মতো পরিস্থিতি ছিল না। যুদ্ধে ব্রিজগুলো ভেঙে গিয়েছিল। আমি বললাম, তুই ওখানে যাবি কী করে? শুট করবি কী করে? তার চেয়ে বরং কুমিল্লা চল। যদিও কুমিল্লার অবস্থাও খুব খারাপ ছিল। ওখানকারও সব ব্রিজ ভাঙা ছিল। তবু কোনোরকমে আমরা কুমিল্লা গেলাম। সার্কিট হাউজে বসে আছি, এমন সময় কুমিল্লার ডিসি সাহেব জানালেন, বাড়ির সামনে ধ্বংসস্তূপের মতো অবস্থা, ওখানে আর কোনো মানুষ যায় না। আমি বললাম, আমাদের তো একটু যেতেই হবে। বাড়ির পাশেই একটা জলা ছিল, তার পাশে বাড়ির সব জিনিসপত্র ছড়ানো, ওগুলো ঘাঁটতে ঘাঁটতে ‘তিতাস একটি নদীর নাম’ পেয়ে গেলাম। ওটা নিয়েই বাড়িতে ঢুকলাম। রাত্রে আমরা একসঙ্গে রয়েছি, ঋত্বিক বললো, পেয়েছি, সিনেমা খুঁজে পেয়েছি। সে আমাকে পেন আর সাদা কাগজ আনতে বললো। আমার ব্যাগে একটা পেন ছিল। কিন্তু গোটা বাড়িতে সাদা কাগজ ছিল না। আমি সাদা কাপড় পরতাম, আয়রন করা একটা কাপড় পেলাম, ওইটাই ঋত্বিককে দিলাম। তার তখন যা আনন্দ, সেই দৃশ্য আমার আজীবন মনে থাকবে। ঋত্বিক আমাকে বললো, তোর এত বুদ্ধি আগে তো জানতাম না! ওই সাদা কাপড়ের উপরে সেই রাতে ঋত্বিক ‘তিতাস’-এর স্ক্রিপ্ট লিখতে শুরু করলো।
ক্যানভাস: আপনি তো ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের পুত্রবধূ, তাঁকে কেমন দেখেছেন?
প্রতীতি দেবী: মানবোত্তর মানুষ বললেও কম বলা হয়। আমার দুই ভাই ওনাকে দেখে এসে মাকে বলেছিল, মানুষ কতটা মহান হয়, তা ওনাকে না দেখলে বোঝা যেতো না। পাকিস্তান আর্মি মেরে ফেলতে পারে, এই আশঙ্কা থেকে ধীরেন্দ্রনাথ দত্তকে কিছুদিনের জন্য ভারতে চলে যেতে বলা হয়েছিল। কিন্তু উনি যাননি, উনি ওনার বন্ধুদের বলেছিলেন, ‘আমি আমার চারপাশের মানুষকে ছেড়ে অন্য কোথাও যাবো না, তোমাদের চলে যেতে হয় তো যাও আর নয়তো যুদ্ধে শামিল হও, যুদ্ধ করে দেশকে স্বাধীন করো।’ ১৯৭১ সালের ২৯ মার্চ রাতে ওনাকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়। উনি তখন বিছানায় শুয়ে, একটু অসুস্থ ছিলেন, হাই ব্লাডপ্রেশার, এর মধ্যেই বাড়ির দরজায় নক করছে পাক সেনারা, আমি দরজা খুলতে গেলাম। আমার ছোট দেবর দিলীপ কুমার দত্ত আমাকে দরজা খুলতে দিল না, সে নিজে গিয়ে দরজা খুললো। তারপর আমাদের চোখের সামনে থেকে আমার শ্বশুরমশাই আর দেবরকে ওরা ধরে নিয়ে গেল। আমি বাধা দিতে চাইলাম, আমাকে একটা বড় রিভলবার উঁচিয়ে বাধা দেওয়া হলো। সারা বাড়ি ঘিরে রেখেছিল ওরা। পরদিন সকাল হলো, আমরা বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়লাম, একটু দূরে হিন্দু আর মুসলিমদের পরপর বাড়ি, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে কোনো সমস্যা ছিল না। কুমিল্লা আর ব্রাহ্মণবাড়িয়া ছিল সবচেয়ে অসাম্প্রদায়িক এলাকা। আমাদের খুব যত্ন করে সীমান্ত পার করে দেওয়া হলো। আমরা আগরতলা পৌঁছালাম। তারপর কলকাতায় গেলাম। ওখান থেকে আমার আরেক বোন পন্ডিচেরিতে নিয়ে গেল। সেখানে আরও মাস ছয়েক থাকলাম।
 ক্যানভাস: আরমা দেবী, আপনি তো ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের নাতনি আর ঋত্বিকের ভাগনি। বাংলার এই দুই কিংবদন্তি মানুষকে আপনি কীভাবে পেয়েছেন?
ক্যানভাস: আরমা দেবী, আপনি তো ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের নাতনি আর ঋত্বিকের ভাগনি। বাংলার এই দুই কিংবদন্তি মানুষকে আপনি কীভাবে পেয়েছেন?
আরমা দত্ত: আমরা পূর্ব পাকিস্তানে থাকতাম, আর আমার মামার বাড়ি ভারতবর্ষে। একসময় যেহেতু আমার দাদুর চলাফেরা রাজনৈতিকভাবে রেস্ট্রিকটেড ছিল, তাই ভারতবর্ষে মামাবাড়িতে আমাদের যাতায়াত একটা সময় অবধি সেভাবে ছিল না। ১৯৬০ সালে ছোট মামা ঋত্বিক ঘটককে আমি প্রথম দেখি, তখন আমার বয়স দশ। ‘মেঘে ঢাকা তারা’র রিলিজ উপলক্ষে আমি, আমার মা আর ছোট ভাই মিলে কলকাতায় ছোট মামার বাড়িতে গিয়েছিলাম। এক মাস সেখানে ছিলাম। তখন ছোট মামাকে খুব কাছ থেকে দেখেছি। ছোট মামা, ছোট মামি, তাঁদের দুই সন্তান টুনি, বুলি… ছোট মামাকে তখন দেখেছি ঋষিতুল্য মানুষ, কাজপাগল, ঋজু মেরুদন্ডের মানুষ… ছোট মামাদের বাড়ির সামনের ঘরে চেয়ার ছিল না, একটা শতরঞ্জি আর তাকিয়া ছিল। ছোট মামার খুব বন্ধু ছিলেন ওস্তাদ বাহাদুর খাঁ, উনি মামার অনেক ছবিতে সরোদ বাজিয়েছেন। মামার যেহেতু বাজনার ওপর আগ্রহ ছিল, খুব ভালো বাঁশি বাজাতেন। বাহাদুর খাঁর কাছে সরোদেরও তালিম নিতেন, দেখতাম শতরঞ্জিতে বসে বিভোর হয়ে সরোদ বাজাচ্ছেন। আমি আর আমার সেজ মামার ছেলে শুভঙ্কর ঘটক মুগ্ধ হয়ে সেই সরোদ শুনতাম। ছোট মামা খুব রাবড়ি খেতে পছন্দ করতেন। ওনার গাড়িতে করে গঙ্গার ঘাটে আমাদের নিয়ে যেতেন। সেই স্মৃতি আমার অম্লান হয়ে আছে। ছোট মামি তখন এমএ পরীক্ষা দেবেন, আমার মনে আছে, ছোট মামা দুই সন্তানকে পাশে নিয়ে রোজ রাতে মশারির ভেতরে মামিকে পড়াতেন। আমি খুব হাসতাম, মামিকে বলতাম, ওমা! তোমার স্কুল কি মশারির ভেতরে? আমাদের স্কুল তো দিনের বেলায়, তোমাদের স্কুল কি রাত্রিবেলায়? ছোট মামাকে দেখেছি অসাধারণ একজন স্বামী হিসেবে, অসাধারণ পিতা হিসেবে আর অসাধারণ একজন পরিচালক হিসেবে। একজন পূর্ণ মানুষ হিসেবে ১৯৬০ সালে তাঁকে দেখেছি, তাঁকে দেখেছিলাম গ্রিক দেবতা জিয়াসের মতন। আবার ১৯৭১ সালে তাঁকে দেখেছি, তখন তিনি ভেঙে খানখান হয়ে গেছেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় আমার দাদুকে, কাকুকে যখন মেরে ফেলা হলো, আমরা বর্ডার ক্রস করে আগরতলায় পৌঁছলাম। তারপর আমরা কলকাতায় গেলাম, ছোট মামা আমাকে নিয়ে গেল সাঁইথিয়াতে। মামি তখন সাঁইথিয়া স্কুলে পড়ান, আসার সময় শান্তিনিকেতনে নিয়ে গেলেন। চিত্রকর, ভাস্কর রামকিঙ্কর ওঁর বন্ধু ছিলেন, রামকিঙ্করের সঙ্গে খোয়াই নদীর কাছে ঘুরতে গেলাম। সেই নদীর জলে দাঁড়িয়ে ছোট মামার হাত ধরে কত যে গান আমি গেয়েছি। ১৯৭২ সালে ছোট মামা ঢাকায় এলেন। তারপর কুমিল্লায় আমাদের বাড়িতে। ধীরেন্দ্রনাথ দত্তর সঙ্গে ঋত্বিকের কোনো দিন দেখা হয়নি। কিন্তু তাঁর শহীদ হওয়ার ঘটনার কথা বলে বলে ছোট মামার সেকি আকুল কান্না… বহু কষ্ট করে ছোট মামাকে নিয়ে হাবিব ভাই, কাওসার ভাইসহ কিছু মুক্তিযোদ্ধা ব্রাহ্মণবাড়িয়া গেলেন। তারপর হাবিব ভাই সিদ্ধান্ত নিলেন তিতাসের প্রযোজনা করবেন। তখন ছোট মামা অনেক ঘন ঘন ঢাকায় এসেছেন। তারপর ‘তিতাস একটি নদীর নাম’ তৈরি হলো, সে এক ইতিহাস।
ক্যানভাস: আরমা দেবী, সাঁইথিয়ার স্কুলে আপনার মামি পড়াতেন, সেখানে আপনাকে নিয়ে গেলেন আপনার ছোট মামা… এই ঘটনাগুলোর সঙ্গে ঋত্বিকের শেষ ছবি ‘যুক্তি তক্কো আর গপ্পো’র দৃশ্যগুলো খুব মিলে যাচ্ছে, ওই যে নীলকণ্ঠের স্ত্রী দুর্গা শহর থেকে অনেক দূরের একটি স্কুলে পড়াতেন, পূর্ব বাংলা থেকে কলকাতায় আসা মেয়ে যাকে নীলকণ্ঠ নাম দিয়েছিল বঙ্গবালা, তাকে নিয়ে নীলকণ্ঠের দুর্গার স্কুলের গ্রামে যাওয়া… আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে, বঙ্গবালা চরিত্রটির উৎস আপনিই। ঋত্বিকের স্ত্রী সুরমা ঘটকের ছাপ যে ‘যুক্তি তক্কো’র দুর্গা চরিত্রের মধ্যে রয়েছে, তা নিয়ে আমরা তো নানা কথাই বলি। আপনি কী বলেন?
আরমা দত্ত: হ্যাঁ, এটা ঠিকমতোই ধরেছেন আপনি। বঙ্গবালা চরিত্রটিতে আমার জীবনের ছাপ রয়েছে কিছুটা। আর যুক্তি তক্কোর ওই যে নীলকণ্ঠ চরিত্র, বাস্তব জীবনে ছোট মামা সত্যিই নীলকণ্ঠ ছিলেন। নিজের জীবনটা শেষ ছবিতে তুলে ধরে তারপর তিনি অন্তরালে চলে যান। ১৯৭৫ সালে তাঁর সঙ্গে আমার শেষ দেখা হয় কলকাতার পিজি হাসপাতালে। আমি আর আমার বাবা সঞ্জীব দত্ত ওঁকে দেখতে গেলাম। ছোট মামা তখন ভীষণ অসুস্থ। ছোট মামা গাঙ্গুরামের মিষ্টি খেতে চাইলেন। আমরা মিষ্টি নিয়ে গেলাম। আমি তখন কানাডা চলে যাচ্ছি, ছোট মামা আমাকে বললেন- তুই আর রিনু (রিনু প্রতীতি দেবী ও ঋত্বিক ঘটকের বোন সম্প্রীতি দেবীর মেয়ে, পুরো নাম রীনা চক্রবর্তী) মাসে মাসে কিছু টাকা পাঠাস। ওই টাকা নিয়ে আমি আর সঞ্জীব হাওড়ার বালিতে একটা ঘর ভাড়া নিয়ে থাকবো, আমাদের কিছু লাগবে না, শুধু বাড়ি ভাড়া, আর সামান্য খাওয়া… রিনুকে বলবি মদের জন্য সামান্য টাকা দিতে… আমরা আর কিছুই করবো না, খালি লিখবো, লিখেই যাবো।
আমার দাদুর প্রসঙ্গে বলি, ধীরেন্দ্রনাথ দত্তকে ৪৭-এর পর ভারতে থাকতে বলা হয়। উনি কিন্তু নিজের দেশ ছেড়ে যাননি; বরং পাকিস্তানকে ধর্মীয়ভাবে একটা ভারসাম্যের জায়গা দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। তারপর পাকিস্তানের গণপরিষদে বাংলা ভাষার দাবি উত্থাপনের পাশাপাশি রাজনৈতিকভাবে বহু অবদান তিনি রেখে গেছেন। আমিও দাদুর শেষ দিন পর্যন্ত তাঁর স্নেহ, ভালোবাসা আর আদর পেয়েছি।
 ক্যানভাস: ঋত্বিকের ছবিতে ফুটে উঠেছে অখন্ড বাংলার লোকজীবন আর মানুষের যৌথ নির্জ্ঞান। এ ছাড়া বাংলা ভাগ হওয়ার বেদনা তাঁকে সারা জীবন তাড়া করে গেছে। মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে ঋত্বিককে কীভাবে দেখেছেন?
ক্যানভাস: ঋত্বিকের ছবিতে ফুটে উঠেছে অখন্ড বাংলার লোকজীবন আর মানুষের যৌথ নির্জ্ঞান। এ ছাড়া বাংলা ভাগ হওয়ার বেদনা তাঁকে সারা জীবন তাড়া করে গেছে। মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে ঋত্বিককে কীভাবে দেখেছেন?
আরমা দত্ত: বাংলাকে তিনি কীভাবে দেখতেন, এখানকার সাংস্কৃতিক বিষয়গুলোকে তিনি কীভাবে দেখেছেন, চলচ্চিত্রের ছাত্র হিসেবে অতনু আপনি এটা ভালোই জানেন। দেশটা তাঁর কাছে মায়ের মতো ছিল। আর সেই মাতৃরূপ তাঁর চলচ্চিত্রে বারবার ফুটে উঠেছে। শিকড় বিচ্ছিন্ন হওয়ার বেদনা ঋত্বিকের মধ্যে তাঁর শেষ নিঃশ্বাসের সঙ্গেও মিশে ছিল। মুক্তিযুদ্ধের সময় ছোট মামা বিশাল কাজ করেছেন। মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্যের জন্য জনসংযোগ, তাঁদের জন্য তহবিল গঠন ও অর্থ সংগ্রহের কাজ, শরণার্থী ক্যাম্পে ছুটে যাওয়া, মিসেস গান্ধীর সঙ্গে ওনার ব্যক্তিগত সখ্যের জেরে মুক্তিযুদ্ধে পূর্ণভাবে সামরিক সহযোগিতার জন্য দিল্লিকে চাপ দেওয়ার মতো কাজ করেছেন ঋত্বিক। এমনকি কলকাতা ও তৎকালীন বোম্বাই ফিল্ম জগতের পরিচালক ও অভিনেতাদের মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে এক প্ল্যাটফর্মে নিয়ে এসেছেন। মৃণাল সেন, ওয়াহিদা রাহমানও এতে অংশ নিয়েছিলেন। সেই জন্য বাংলাদেশ সরকারের তরফেও ঋত্বিক ঘটককে সম্মাননা দেওয়া হয়েছে।
ক্যানভাস: ঋত্বিকের শেষবারের মতো ঢাকা ছেড়ে যাওয়ার স্মৃতি আপনাদের মনে আছে?
প্রতীতি দেবী: ঋত্বিক ঢাকায় থাকতো পরীবাগের কাছাকাছি একটা হোটেলে। নাম গ্রিন হোটেল। আমি কিছুদিন অসুস্থ ছিলাম, একটু সুস্থ হয়েছি সবে, সময়টা ১৯৭৩ বা ৭৪ হবে, সেনাবাহিনীর দুজন আমার খুব ভালো বন্ধু ছিল, তারা এসে আমায় বললো, তাড়াতাড়ি চলুন, ঋত্বিক ঢাকা ছেড়ে চলে যাচ্ছে। আমি হোটেলে গেলাম, আরও কয়েকজনের বাড়িতে গেলাম। কোথাও সে নেই। আমি দৌড়ে এয়ারপোর্ট গেলাম। সেখানে ঋত্বিক আমাকে দেখে জড়িয়ে ধরে সে কী কান্না! সারা জীবন ও শুধু কেঁদেই গেল, কিছুই পেল না! ঋত্বিকের জন্য মিসেস গান্ধী বিশেষ বিমানের আয়োজন করেছিলেন। ওর জন্য ওই বিমান এয়ারপোর্টে অপেক্ষা করছিল। কিন্তু ঋত্বিক কিছুতেই আমাকে ছাড়ছিল না। সন্ধ্যা হয়ে যায়, ঋত্বিক আমাকে ছাড়ে না, আমাকেও তার সঙ্গে নিয়ে যেতে চায়। তারপর আমি আমার ছেলেমেয়েদের কথা বললাম। তখন সে একটু শান্ত হলো। এদিকে বিমান থেকে ওকে তাড়া দেওয়া হচ্ছিল বারবার। ঋত্বিক বলে দিল্লিতে ফোন করতে। এয়ারপোর্ট থেকে দিল্লিতে ফোন করা হলো। দিল্লি থেকে বলা হলো, ঋত্বিক যতক্ষণ না যেতে চাইছে, ততক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে। প্লেনের দরজায় দাঁড়িয়েও সে কাঁদতে থাকলো, আমি জোর করে ওকে প্লেনের ভিতরে পাঠালাম। আবারও তাকে নিজের জন্মভূমি ছেড়ে চলে যেতে হচ্ছে, তার চোখ দিয়ে পানি ঝরেই যাচ্ছে… ঢাকায় ওকে শেষবার ওভাবেই দেখেছি, কাঁদতে কাঁদতে চলে যেতে দেখেছি।
আরমা দত্ত: আমার মামাতো দিদি মহাশ্বেতার ছেলে বাপ্পা, মানে কবি নবারুণ ভট্টাচার্য, ওর একটা স্পিচ আছে, যেটা পরে লিখিত আকারে ছাপা হয়েছে, সেখানে নবারুণ পরিষ্কার জানিয়েছে যে ঋত্বিককে খুন করা হয়েছে। আমাদেরও মনে হয়, ঋত্বিককে খুন করা হয়েছে।
ক্যানভাস: মণীশ ঘটক আর মহাশ্বেতা দেবীর সঙ্গে আপনার সম্পর্ক কেমন ছিল?
প্রতীতি দেবী: মণীশ ঘটক আমাদের পিতৃতুল্য বড়ভাই। জন্মের পর আমি খুবই অসুস্থ ছিলাম, বলা যায় উনিই আমাকে বাঁচিয়েছেন। ওঁর কন্যা, মহাশ্বেতা আমাদের প্রায় সমবয়সী। ঋত্বিক আর আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল মহাশ্বেতা, আমার মেয়ে বুয়ার (আরমা) সঙ্গে মহাশ্বেতার ছেলে নবারুণের ঘনিষ্ঠতা ছিল। ওরা আজ আর কেউ নেই।
ক্যানভাস: ঋত্বিকের কোন কোন ছবি তাঁর সঙ্গে একত্রে দেখেছেন?
প্রতীতি দেবী: ‘মেঘে ঢাকা তারা’ আর ‘অযান্ত্রিক’। অনেক পরে ঋত্বিকের ছেলে আমাকে ‘যুক্তি তক্কো আর গপ্পো’ দেখিয়েছে। আর ‘তিতাস’-এর সঙ্গে আমি ছিলাম ওই স্ক্রিপ্ট লেখা শুরু করার মুহূর্তে। ‘অযান্ত্রিক’ যখন দেখতে গেলাম, তখন আমাকে ঋত্বিক তার বন্ধুদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলো, বললো, ‘এইটা আমার যমজ বোন, আমার ইটারনাল পেয়ার’।
ক্যানভাস: ‘তিতাস একটি নদীর নাম’ ছবির সঙ্গে মুক্তিযোদ্ধাদের অনেক আবেগ জড়িয়েছিল বলে শোনা যায়।
আরমা দত্ত: হ্যাঁ, আমি তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ি। গ্রিন হোটেলে গিয়ে দেখতাম ঋত্বিককে ঘিরে বসে আছে বিখ্যাত সব মুক্তিযোদ্ধা।
ক্যানভাস: দুই বাংলাকে আপনারা এখন কীভাবে দেখেন?
আরমা দত্ত: আমাদের গোটা পরিবার বাংলা ভাষা, সংস্কৃতি ও বাংলাদেশের স্বাধীনতার সঙ্গে সম্পৃক্ত। বাংলাদেশ গড়ে ওঠায় আমার দাদু ধীরেন্দ্রনাথের অবদান আর বাংলা সিনেমা, বাংলা সংস্কৃতিতে ঋত্বিকের অবদান, সাহিত্যে মণীশ ঘটক, মহাশ্বেতার অবদান, এমনকি নবারুণ… দুই বাংলার আগামী প্রজন্ম আশা করি মনে রাখবে।
প্রতীতি দেবী: বাংলা দ্বিখন্ডিত হওয়ার ঘটনা আমাদের কাছে অভিশাপের মতো। সেই অভিশাপ নিয়েই বেঁচে আছি।

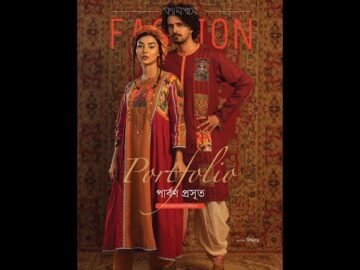







আমি একজন মুক্তিযোদ্ধা। আমরা বিক্রমপুর এর মানুষ।
আমার বাবা মরহুম হাজী আমজাদ আলী। তিনি বহুদিন
কলকাতায় ছিলেন, ওখানে বানিজ্য করতেন। ১৯৪৬ সালে রায়েটের পর বাবা ততকালিন পূর্ব পাকিস্থানে এসে মিরকাদিম বন্দরে বানিজ্য শুরুকরেন। ১৯৬৫ সালে ওনার কলকাতার বানিজ্য বন্ধ হয়ে যায়, ভারত ও পাকিস্থানের
যুদ্ধকালে।
আমার বাবা অবিভক্ত বাংলা কে কোন দিন মেনেনিতে
পারেনি। আমার বাবা ৯৬ বছর বয়েসে ১৯৯৪ সনে ইন্তেকাল
করেন। আমার বাবার ৪ ছেলে ৯ মেয়ে এই ১৩ সন্তানের পিতা।আমরা ৩ ভাই মুক্তিযোদ্ধা, এ কারনে আমার বাবাকে পাকবাহিনী ধরেনিয়ে গিয়েছিল। আল্লাহ্ র অনেক রহমতে বাবাকে কিছুকরতে পারেনি। আমরা বাবার নামে স্কুল, কলেজ বানিয়েছি, যেন আমার বাবাকে দেশের মানুষ কোন
দিন ভুলতে না পারে।