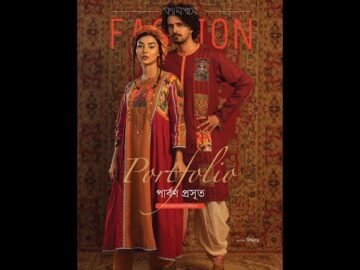ছুটিরঘণ্টা I দ্রাবিড়ীয়
দক্ষিণ ভারতে বঙ্গোপসাগর ঘেঁষে পুরাণজড়িত এক শহর মহাবালিপুরাম। সেখানকার পাথুরে পাহাড় আর মন্দিরের শোভা তুলনারহিত। লিখেছেন ফাতিমা জাহান
রাজা নরসিংহবর্মণ পায়চারি করছেন নিজ কক্ষে, একটু চিন্তিত মনে হলো তাঁকে। দক্ষিণ ভারতের বিশাল অংশের রাজা তিনি, অনেক আক্রমণকারীর হাত থেকে রক্ষার জন্য তাঁকে নিত্য প্রস্তুত থাকতে হয়। পাল্লাভা রাজবংশ তাদের, শৌর্যে-বীর্যে তুলনাহীন। প্রজারাও বেশ অনুগত। বছর পঞ্চাশেক আগে ‘পঞ্চ রথ’ নামে মন্দির নির্মাণ করা হয়েছিল পঞ্চপা-বকে উৎসর্গ করে; তবে সাগরের আশপাশে ভগবানকে সন্তুষ্ট করবার জন্য এখনো কোনো মন্দির তৈরি হয়নি, চিন্তাটা রাজার সে কারণেই। তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন, সাগরপাড়ে মন্দির হবে সাগরদেবতাকে তৃপ্ত রাখার জন্য। সময়টা সপ্তম শতাব্দী। রাজার ইচ্ছে অনুযায়ী তৈরি হলো সাত-সাতটা মন্দির, সাগরপাড়ে।
এবারের ভ্রমণ পাল্লাভা রাজবংশের রেখে যাওয়া নিদর্শন ‘মহাবালিপুরাম’-এর বিভিন্ন মন্দির ও কীর্তিস্তম্ভ দর্শন। আর খানিকটা সাগরের সঙ্গে মিতালি।
‘মহাবালিপুরাম’ বা স্থানীয় ভাষায় ‘মামাল্লাপুরাম’ নামকরণ করা হয় রাজা নরসিংহবর্মণের নামে। মামাল্লা মানে মল্ল বা মল্লযুদ্ধ। রাজা নরসিংহ (রাজ্যকাল ৬৩০-৬৬৮ খ্রিস্টাব্দ) ছিলেন মল্লযুদ্ধে পারদর্শী। তাকে হারানোর শক্তি তার বা আশপাশের রাজ্যের কারও ছিল না। তিনি ছিলেন শিব ঠাকুরের ভক্ত। শিল্পানুরাগীও ছিলেন। ভারতের মোট ১২ জন রাজা, যাদেরকে শত্রু কখনোই পরাস্ত করতে পারেনি তাদের একজন এই নরসিংহ।
মহাবালিপুরাম স্থানটি দক্ষিণ ভারতের তামিলনাড়ু রাজ্যের কাঞ্চিপুরাম জেলায় অবস্থিত। চেন্নাই থেকে ৬০ কিলোমিটার দূরে। মহাবালিপুরামের উল্লেখ আছে টলেমির সময়কার পেরিপ্লাস পুস্তকে, তা খ্রিস্টপূর্ব কয়েক শ বছর আগের কথা। মহাবালিপুরাম সেই সময় থেকে দক্ষিণ ভারতের বাণিজ্যিক শহর হিসেবে পরিচিত। এখানে খ্রিস্টপূর্ব কয়েক শ বছর আগের চীন ও রোমান মুদ্রার সন্ধান এটাই প্রমাণ করে যে মহাবালিপুরাম একটি সমৃদ্ধিশালী জনপদ ছিল।
 মহাবালিপুরাম পৌঁছুতে সড়কপথে ঢাকা থেকে কলকাতা হয়ে ট্রেন ধরে যেতে হয় চেন্নাই, উড়োজাহাজেও ঢাকা বা কলকাতা থেকে চেন্নাই যাবার ব্যবস্থা আছে। চেন্নাই থেকে বাসে বা ট্যাক্সি করে মহাবালিপুরাম যেতে সময় লাগে এক ঘণ্টা।
মহাবালিপুরাম পৌঁছুতে সড়কপথে ঢাকা থেকে কলকাতা হয়ে ট্রেন ধরে যেতে হয় চেন্নাই, উড়োজাহাজেও ঢাকা বা কলকাতা থেকে চেন্নাই যাবার ব্যবস্থা আছে। চেন্নাই থেকে বাসে বা ট্যাক্সি করে মহাবালিপুরাম যেতে সময় লাগে এক ঘণ্টা।
হিন্দু পুরাণে আছে, যুবরাজ হিরণ্যকশিপু ভগবান বিষ্ণুকে সম্মান প্রদর্শন করতে বা তাঁর পূজা অর্চনা করতে অস্বীকৃতি জানান। এই বিমুখতায় পিতাকে ভর্ৎসনা করেন প্রহ্লাদ। হিরণ্যকশিপু ক্রুদ্ধ হয়ে প্রহ্লাদকে রাজ্য থেকে বের করে দেন; কিন্তু পরবর্তী সময়ে আবার তাকে গ্রহণ করেন। পিতা-পুত্রের মাঝে বাগ্বিত-া শুরু হয় ভগবান বিষ্ণুর অসীম ক্ষমতা নিয়ে। প্রহ্লাদ বলেন, ভগবান বিষ্ণু সব স্থানে বিদ্যমান এমনকি গৃহের দেয়ালেও। হিরণ্যকশিপু স্তম্ভে লাথি মারেন, তখনই স্তম্ভ থেকে ভগবান বিষ্ণু মানব শরীর আর সিংহের মাথা নিয়ে আবির্ভূত হন এবং হিরণ্যকশিপুকে বধ করেন। প্রহ্লাদ রাজা হন। রাজা প্রহ্লাদের পৌত্র ‘বালি’ পরবর্তীকালে মহাবালিপুরাম নগরী গড়ে তোলেন।
ইউনেসকো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইটের অন্তর্ভুক্ত এই দর্শনীয় স্থানটি এক দিনের সফরেই দেখে ফেলা যায়। তবে আমি তিন দিনের জন্য গিয়েছিলাম। হোটেল আগে থেকেই অনলাইনে বুক করে রেখেছিলাম। সমুদ্রতীরে বিশাল বারান্দা আর বিশাল জানালাসহ এক কটেজ। সেখানে ব্যাগপত্র রেখে মন তো আর চায় না সাগরের হাতছানি উপেক্ষা করে পাল্লাভা রাজবংশের নিদর্শনের অভিযানে যাই। তবে মনটা ছিল বেশ বিভক্ত, আরেক অংশ তাড়া দিয়ে বলল, অনেক শখ করে এসেছ তো পুরাকীর্তি দেখতে, এত জলদি সাগরে মজে গেলে হবে!
বেরিয়ে পড়লাম রাজাবাদশাহদের জৌলুশ দেখতে। হোটেল থেকে সব দর্শনীয় স্থান ছিল হাঁটা দূরত্বে। প্রথমে গেলাম জঙ্গলের ভেতর ১৫টি গুহামন্দির দেখতে, যা পাহাড় খোদাই করে তৈরি। উল্লেখ্য, দক্ষিণ ভারতের বেশির ভাগ পাহাড়ই আস্ত বিশাল বিশাল পাথরে গঠিত। যা কেটে গুহা বানিয়ে রাজাদের ইচ্ছে অনুযায়ী মন্দির বানানো হতো, বা পূজার জন্য তৈরি করা হতো দেবতা। ১৫টি মন্দিরের একেকটা একেক দেবতাকে উৎসর্গ করে তৈরি করা হয়েছিল ৬ষ্ঠ থেকে ৯ম শতাব্দীতে। প্রতিটি গুহামন্দির ১০ থেকে ৩০ মিটার জায়গাজুড়ে আর উচ্চতা ৪ থেকে ১০ মিটার। উল্লেখযোগ্য গুহামন্দির হলো বরাহ দেবতার মন্দির, পঞ্চপা-বের মন্দির, গণেশ দেবতার মন্দির, ইন্দ্রদেবতার মন্দির ইত্যাদি। কয়েকটি মন্দিরের কাজ অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে। ইতিহাস বলে, এসব গুহামন্দিরের কাজ সাধারণত করত স্থাপত্যকলার ছাত্ররা, তারা কিছু কাজ করে অন্যত্র হাত দেওয়ায় এগুলো অসম্পূর্ণ অবস্থায় পড়ে রয়েছে। স্থানীয় মানুষজন বলেন, কাঞ্চিপুরাম দখলের জন্য যুদ্ধবিগ্রহ লেগেই থাকত, তাই রাজা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মন্দির নির্মাণের কাজও অসম্পূর্ণ থেকে যায়।
বরাহ দেবতার মন্দিরটি খুঁজে পেতে বেশ বেগ পেতে হয়। কারণ, মন্দিরটি একে তো পাহাড়ের গুহার ভেতরে, তার ওপর প্রবেশদ্বার আরেকটি প্রস্তরখ-ে আবৃত। রাজা নরসিংহবর্মণের পিতা রাজা মহেন্দ্রবর্মণ শিল্পকলার বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। তাঁর নির্দেশে তৈরি হয় বরাহ দেবতার মন্দির। এর ভেতরে অনেক কক্ষ রয়েছে। সেগুলোর মধ্যে প্রধান কক্ষে রয়েছে ভগবান বিষ্ণুর বরাহ অবতার, পাথরের ওপর খোদাই করা ভাস্কর্য। পুরাণে আছে যে বসুন্ধরা যখন মনুষ্যজাতির অবহেলার কারণে অভিমান করেছিলেন, তখন ভগবান বিষ্ণু বরাহ অবতারে বসুন্ধরাকে কোলে তুলে নিয়েছিলেন। সে ঘটনাই খোদিত আছে এ মন্দিরে। বরাহ দেবতা দুহাতে ধরে আছেন বসুন্ধরাকে আর অন্য দুটি হাতের একটিতে শঙ্খ এবং অন্যটিতে চক্র শোভা পাচ্ছে। একই মন্দিরে অন্য কক্ষ গজলক্ষ্মী। যেখানে দেবী লক্ষ্মীর প্রতীক আঁকা রয়েছে দেয়ালে। অন্য কক্ষটি দুর্গার জন্য উৎসর্গিত। যেখানে মহিষাশুরকে বধ করার দৃশ্য চিত্রায়িত। উত্তর দিকের কক্ষ শিবঠাকুর বা গঙ্গাধরের জন্য।
 এরপর পাহাড়ের উপরে অবস্থিত মন্দির ও রাজারানির স্নানের জন্য নির্মিত পুকুর দেখতে গেলাম। চট করে কাঞ্চিপুরাম এলাকা ৩৬০ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে দেখে ফেললাম। পাহাড় থেকে নামলাম খানিকটা জঙ্গলের ভেতর দিয়ে। পাখির কলতানে অতিথি আপ্যায়নটা বেশ হয়েছিল।
এরপর পাহাড়ের উপরে অবস্থিত মন্দির ও রাজারানির স্নানের জন্য নির্মিত পুকুর দেখতে গেলাম। চট করে কাঞ্চিপুরাম এলাকা ৩৬০ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে দেখে ফেললাম। পাহাড় থেকে নামলাম খানিকটা জঙ্গলের ভেতর দিয়ে। পাখির কলতানে অতিথি আপ্যায়নটা বেশ হয়েছিল।
নেমেই চোখে পড়ল কৃষ্ণগোলক। মনে হচ্ছিল একটি বিশাল গোলাকার পাথরখ- পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে ধেয়ে আসছে আমার দিকে। আসলে কিন্তু পাথরটি একটুও নড়ছিল না। মাধ্যাকর্ষণ শক্তির বলে পাহাড়ের গায়েই আটকে ছিল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মাখন খেতে ভালোবাসতেন। এ পাথরের নামকরণ সে সূত্রেই।
১৪০০ বছরের বেশি সময় ধরে ঝড়, বন্যা, জলোচ্ছ্বাসেও একইভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে এই গোলাকৃতি বিশাল পাথরখ-। ওজন প্রায় ২৫০ টন। রাজা নরসিংহবর্মণ চেষ্টা করেছিলেন পাথরটি সরাতে; কিন্তু বিফল হয়েছিলেন। ব্রিটিশ শাসনামলে গভর্নর হ্যাভলক সাতটি হাতি দিয়ে প্রস্তরখ-টি অপসারণের চেষ্টা করেছিলেন, তিনিও বিফল হয়েছিলেন।
সেখান থেকে দুই মিনিট হাঁটলেই ‘অর্জুনের প্রায়শ্চিত্ত’ নামক গুহাটি। আস্ত পাথরে তৈরি গুহাটির গায়ে দেবদেবীসহ সাধারণ মানুষের বন্দনার চিত্র ফুটে উঠেছে।
পুরাকথা বলে, দেবতা অর্জুনকে বধ করতে অসুর যখন একটি বরাহ প্রেরণ করেন, সেই মুহূর্তের শিবঠাকুর এক সাধারণ শিকারির বেশে আসেন অর্জুনকে রক্ষা করতে। শিবঠাকুর ও অর্জুন একই সঙ্গে বরাহটিকে বধ করেন এবং দুজনে রণে লিপ্ত হন। অর্জুনের পরাজয় ঘটে এবং শিবঠাকুর নিজ অবতারে ফিরে আসেন। শিবঠাকুরকে দেখে অর্জুন ভীষণ অনুতপ্ত বোধ করেন। শিবঠাকুর অর্জুনকে বর স্বরূপ তাঁর অস্ত্রটি দেন। এই কাহিনি বিভিন্ন আঙ্গিকে গুহার ভেতরের এবং বাইরের দেয়ালে খোদাই করা আছে। গৌতম বুদ্ধকে নিয়েও কিছু ভাস্কর্য রয়েছে গুহার ভেতরে এবং কিছু রয়েছে পাহাড়ের ওপরে।
পুরাকীর্তি দেখতে দেখতে বিকেল হতে চললো। খাওয়ার কথা মনে নেই। ভারতীয় সামুদ্রিক খাবারের খোঁজ পেলাম এক রেস্টুরেন্টে। সেখানেই দুপুরের খাওয়া সারলাম। দক্ষিণ ভারতীয় রন্ধনপ্রণালি বাঙালিদের চেয়ে একেবারে ভিন্ন। মাছ তারা পেঁয়াজ, রসুন দিয়ে রান্না করেন আর তেঁতুল, বাটা নারকেল হচ্ছে রান্নার অপরিহার্য উপাদান। খেয়ে ছুটলাম মহাবালিপুরাম সমুদ্রসৈকতে, যা আমার কটেজের সামনেই বঙ্গোপসাগরের করম-ল উপকূলে অবস্থিত।
যত দূর চোখ যায় সৈকত ধরে হাঁটলাম। যখন ক্লান্ত হলাম, তখন কটেজে গিয়ে বারান্দায় বসে সোনালি তটে সফেন ঢেউয়ের মাতামাতি দেখলাম। আহা, কী গর্জন! আর কী ঠান্ডা বাতাস! দূরে জেলেরা ততক্ষণে সাগরের উত্তাল ঢেউ সামলে মাছের নেশায় মাঝসাগরে মত্ত।
কটেজটি জেলেদের গ্রামের মধ্যে। আমাদের দেশে গ্রাম বলতে যা বোঝায়, এটি তা নয়। প্রতিটি বাড়ি পাকা একতলা অথবা দোতলা আর সবার ঘরেই টিভি-ফ্রিজ আছে, সব শিশু স্কুলে যায়। রাস্তাঘাটও পাকা। জেলেরা বিকেলে মাছ ধরতে যায় গহিন সাগরে। দিনে জাল বোনে, আলস্যে কাটায় বা ঘুমায়। সাগরপাড়ের জায়গাগুলো হোটেলমালিকেরা কিনে নিয়েছে। পেছনের জায়গাগুলোতে জেলেদের সুখের আবাস।
মহাবালিপুরামে দ্বিতীয় দিন। খুব ভোরে উঠলাম সূর্যোদয় দেখার জন্য। আমার বারান্দা থেকেই। সূয্যিমামা তার লালিমা ছড়াতেই চলে গেলাম ‘সমুদ্রতটের মন্দির’ দেখতে।
 দক্ষিণ ভারতের সব মন্দির দ্রাবিড়ীয় স্থাপত্যকলায় নির্মিত। চারপাশ ঘেরা উঁচু প্রাচীর, বিশাল আকৃতির প্রবেশদ্বার, যাকে বলা হয় গোপুরা এবং যার মাথায় রয়েছে পিরামিড আকৃতির কাঠামো, মন্দির প্রাঙ্গণে পুকুর, যাকে বলা হয় কল্যাণী, মূল মন্দিরের চূড়ার পিরামিডাকৃতি ইত্যাদি এই স্থাপত্যকলার বৈশিষ্ট্য।
দক্ষিণ ভারতের সব মন্দির দ্রাবিড়ীয় স্থাপত্যকলায় নির্মিত। চারপাশ ঘেরা উঁচু প্রাচীর, বিশাল আকৃতির প্রবেশদ্বার, যাকে বলা হয় গোপুরা এবং যার মাথায় রয়েছে পিরামিড আকৃতির কাঠামো, মন্দির প্রাঙ্গণে পুকুর, যাকে বলা হয় কল্যাণী, মূল মন্দিরের চূড়ার পিরামিডাকৃতি ইত্যাদি এই স্থাপত্যকলার বৈশিষ্ট্য।
সপ্তম শতাব্দীতে সমুদ্রতটে সাতটি মন্দির নির্মিত হয়েছিল। এখন দুটি মাত্র দাঁড়িয়ে আছে। বাকিগুলো বৈরী আবহাওয়ায় কালের গর্ভে হারিয়ে গেছে। রাজা নরসিংহবর্মণ মন্দিরটি স্থাপন করেছিলেন মূলত শিবঠাকুরের পূজা দেবার জন্য। গ্রানাইট পাথরের মন্দিরটির ভেতরে তিনটি প্রার্থনাগৃহ আছে, দুটি শিবঠাকুরের আর একটি ভগবান বিষ্ণুর পূজার জন্য। সমুদ্রতট মন্দিরটি সমুদ্রের দিকে মুখ করে হয়েছিল, যাতে সূর্যকিরণ সরাসরি এসে মন্দিরে অবস্থিত শিবলিঙ্গে পড়ে। মন্দিরচত্বরটিও বিশাল। ঢোকার মুখেই সারি সারি নন্দী যেন মন্দির পাহারা দিচ্ছে। মূল মন্দিরের দেয়ালে ব্রহ্ম, বিষ্ণু, শিবঠাকুর ও দুর্গার ভাস্কর্য খোদাই করা আছে।
মহাবালিপুরামের প্রায় সব মন্দিরই পুরাকালে বিশাল আকারের আস্ত পাথরখ- থেকেই তৈরি। দক্ষিণ ভারতে পাথরের পাহাড়ের অভাব নেই। তাই স্থাপত্য ও ভাস্কর্য চর্চার সুযোগ অন্যান্য স্থান থেকে বেশি।
দ্রাবিড়ীয় শিল্পকলাকে আরও সম্প্রসারিত করার কাজটি পাল্লাভা রাজবংশ খুব নিষ্ঠার সঙ্গেই করে গেছে, সেই সঙ্গে স্বতন্ত্র শিল্পকলা যা পাল্লাভা শিল্পকলা (বিশেষত গুহামন্দির, একপ্রস্তরশিলায় ভাস্কর্য, মন্দিরের স্তম্ভের গোড়ায় সিংহের মূর্তি) নামে পরিচিত, তাকেও নিয়ে গিয়েছিল বহুদূর।
সমুদ্রতটের মন্দির দেখে চললাম ‘পঞ্চ রথ’ দেখতে। পঞ্চপা-বের স্মৃতিতে নির্মিত পাঁচটি আলাদা রথ আকারের গোলাপি গ্রানাইট পাথরের একপ্রস্তরে তৈরি স্মৃতিস্তম্ভ পাশাপাশি দাঁড়িয়ে। এখানে পূজা অর্চনা কখনোই করা হয়নি। কারণ, রাজা নরসিংহবর্মণ দেবতাসেবায় নিজেকে উৎসর্গ করার আগেই গত হয়েছিলেন। তাই এ স্থান কীর্তিস্তম্ভ হিসেবেই রয়ে গেছে। পঞ্চপা-বের নামানুসারে রথগুলো হলো ধর্মরাজ, ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব আর দ্রৌপদী।
 এগুলোর সঙ্গে আছে একপ্রস্তরে নির্মিত গজ।
এগুলোর সঙ্গে আছে একপ্রস্তরে নির্মিত গজ।
পঞ্চ রথ দেখে হাঁটতে হাঁটতে ফিরছিলাম পাথরে খোদাই করা মূর্তি, শোপিস ইত্যাদির সারি সারি দোকানের সামনে দিয়ে। কিনে ফেললাম ঐতিহ্যবাহী লাল মার্বেল আর গ্রানাইট পাথরে সূক্ষ্ম কারুকার্যময় দুটি শোপিস আর কয়েকটা সাদা, লাল মার্বেল পাথরে খোদাই করা ক্ষুদ্র পেন্ডেন্ট। মহাবালিপুরামের ঐতিহ্যবাহী পাথরে খোদাই করা শোপিসের খ্যাতি ভারতজুড়ে। তাই স্মৃতি হিসেবে কিনে নিয়ে যেতে ভুলবেন না যেন।
ফিরে এসে বাকি সময় সাগরপাড়ে কাটালাম। অন্যান্য সমুদ্রসৈকত থেকে ভ্রমণার্থী কম থাকার কারণে এখানে সাগর দেখার আনন্দ আলাদা। জেলেরা জাল বুনছেন বা নৌকা ঠিকঠাক করছেন, খানিক বাদেই সাগর পাড়ি দেবেন বলে। কয়েকজন জেলের সঙ্গে কথা হলো। নাইলনের পাতলা দড়ি দিয়ে যে জালটা বোনা হচ্ছিল, সেটা পমফ্রেট মাছ ধরার জন্য আর মোটা দড়ি দিয়ে যে জালটা, সেটা টুনা মাছ ধরার জন্য। অনেক জেলেই ইংরেজিতে কথা বলতে পারেন। এখানকার মোটামুটি সবাই ইংরেজি বোঝেন এবং বলতে পারেন, তাই দর্শনার্থীদের অসুবিধা তেমন হয় না। সবচেয়ে বন্ধুবৎসল জেলেটির নাম পরিমল। আরও ছিলেন মুরগান, বালা, শক্তি।
তৃতীয় এবং শেষ দিন মহাবালিপুরামে। পুরাকীর্তিগুলোকে আরও দৃঢ়ভাবে মনের খাঁচায় বন্দি করে রাখার জন্য আধবেলা পথের সঙ্গে বন্ধুত্ব করলাম।
বাকি আধাটা দিন কাটিয়ে দিলাম তীব্র অথচ শীতল হাওয়ার করম-ল উপকূলে। সাগরপাড়ের অনিন্দ্য সৌন্দর্য ফেলে যাবার ইচ্ছে একেবারেই ছিল না, তবু অন্য আরেক অচেনা গন্তব্যের টানে বিদায় জানালাম এই পুরাকীর্তির অল্প চেনা আর বেশি বন্ধুত্ব হয়ে যাওয়া স্থানটিকে।
উল্লেখযোগ্য তথ্য: ঢাকা থেকে কলকাতা যেতে হয় বাস, ট্রেন বা বিমানে। কলকাতা থেকে চেন্নাই যাবার জন্য ট্রেনের (ভ্রমণ সময় ২৬-২৮ ঘণ্টা ট্রেনভেদে) ভাড়া ৬৫০-৪৫০০ রুপি (এসি, নন-এসি ইত্যাদি ভেদে) ওয়ান ওয়ে। বিমান (ভ্রমণ সময় ২ ঘণ্টা কলকাতা থেকে) ভাড়া ৩০০০ রুপি থেকে শুরু (ওয়ান ওয়ে, তবে চাহিদা এবং লভ্যতা অনুসারে যেকোনো রুটের বিমান ভাড়া কম বা বেশি হওয়া অস্বাভাবিক নয়)।
মহাবালিপুরামে সব ধরনের হোটেল পাওয়া যাবে, বাজেট থেকে শুরু করে পাঁচ তারা। অনলাইনে ভিসা অথবা মাস্টার কার্ড ব্যবহার করে টাকা পরিশোধ করে সহজেই যেকোনো মানের হোটেল রুম বুকিং দেওয়া যায়। হোটেল বুকিং করা না থাকলে, সেখানে গিয়েও পছন্দমতো হোটেল পাওয়া যায়।
রেস্টুরেন্ট আছে প্রচুর। দক্ষিণ বা উত্তর ভারতীয় খাবারের সঙ্গে আমেরিকান বা ইউরোপিয়ান খাবারের রেস্টুরেন্ট অগুনতি।
ছবি: লেখক