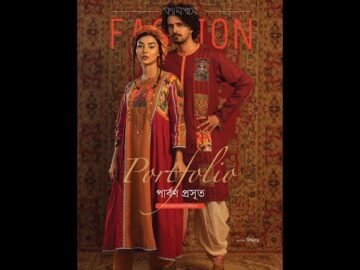বিশেষ ফিচার I চিত্রিত মৃৎশিল্প
মাটির তৈরি পাত্রে আঁকা ছবি। বাংলার লোকজ শিল্পকলা। বংশপরম্পরাই যার চালিকাশক্তি। লিখেছেন উদয় শংকর বিশ্বাস
বাঙালির মৃৎশিল্প গৌরবময়। জনজীবনের সর্বত্র মাটির ব্যবহার রয়েছে। পানি-হাওয়া-মাটি বাঙালিকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রেখেছে আবহমানকাল ধরে। ঐতিহ্যবাহী মৃৎশিল্পের মধ্যে চিত্রিত লোকশিল্প বিশেষ এক স্থান নিয়ে আজও টিকে আছে। সামাজিক-ধর্মীয় বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সরাচিত্র, মনসার ঘট, শখের হাঁড়ি, দেবপ্রতিমা—এমন সব চিত্রিত মৃৎশিল্পের উপস্থিতি এখনো চোখে পড়ে। এগুলোর মধ্যে বঙ্গ-সংস্কৃতির প্রবহমানতা লক্ষ করা যায়। বাঙালি জাতির স্বকীয়তা ও নান্দনিকতা একাকার হয়ে আছে এসব শিল্পকলা। জনরুচির পরিবর্তন, কাঁচামালের অভাব, দক্ষ কারিগর না থাকা ইত্যাদি প্রতিকূলতা পাড়ি দিয়ে এখনো টিকে আছে বেশ কিছু চিত্রিত মৃৎশিল্প। যেমন:

লক্ষ্মীসরা
লক্ষ্মীর সরা: মাটির সরা সাধারণত হাঁড়ির ঢাকনা হিসেবে আবহমান বাংলায় ব্যবহৃত হয়ে আসছে। আকৃতি ও ব্যবহারভেদে সরার ভিন্ন নাম আছে, যেমন: ঢাকনাসরা, ফুলসরা, ধূপসরা, মুপিসরা, তেলনিসরা, আমসরা, এয়োসরা, আঁতুরসরা, গাজীর সরা, লক্ষ্মীসরা ইত্যাদি। তবে সব সরাই চিত্রিত নয়। অঙ্কিত বা চিত্রিত সরা বাংলার মৃৎশিল্পের ঐতিহ্যে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। কোজাগরী লক্ষ্মীপূজায় বিশেষ করে দক্ষিণবঙ্গের বাঙালি সনাতন সম্প্রদায়ের লোকজন লক্ষ্মীসরায় তাদের আরাধ্য ধনদেবী লক্ষ্মীর পূজা করে থাকেন। এটি নানা আকারের হয়। বড় আকারের লক্ষ্মীসরা ১৬ ইঞ্চি, মাঝারি ১০ ইঞ্চি এবং ছোটগুলো ৬ ইঞ্চি। আকার যা-ই হোক, বাজারে চলতি অর্ধগোলাকৃতি সরা এটি নয়, এর এক পিঠ সামান্য উত্তল, অনেকটা কচ্ছপের পিঠের মতো। কুমারেরা এ সরা তৈরি করেন। তাদের কাছ থেকে সরাশিল্পীরা সংগ্রহ করে তাতে আঁকার মূল কাজটি করেন। লক্ষ্মীপূজার তিন-চার মাস আগে থেকেই সরা চিত্রণের কাজ শুরু হয়। বাড়ির মেয়েরা সরা চিত্রণের কাজের সঙ্গে যুক্ত হন পুরুষের সঙ্গে। একসময় আচার্য ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের লোকজনই বেশি মাত্রায় যুক্ত ছিলেন এই কাজে। এখন সূত্রধর শ্রেণির শিল্পীরা করেন। সরা চিত্রণের শুরুতে উত্তল আকৃতির পিঠটিকে ঘষে মসৃণ করে নেওয়া হয়। এর উপরে খড়িমাটির প্রলেপ দেওয়া হয়। এবার সরাশিল্পী তার উপরে বলিষ্ঠ কালো রেখা টেনে একে কয়েক ভাগে ভাগ করে নেন। তারপর রেখাচিত্র আঁকার কাজটি করেন। প্রাথমিক রঙ শুকিয়ে গেলে সরায় আঁকা হয় লক্ষ্মী, লক্ষ্মীপেঁচা, ধানের শিষ, কড়ি ইত্যাদি মোটিফ। লক্ষ্মীর কাপড়, চুল, চোখ, গয়না ইত্যাদির উপর শিল্পী রঙ লাগান বিশেষ দক্ষতায়। সবশেষে রঙের ঔজ্জ্বল্য বাড়াতে সাবুর আঠা বা তেঁতুলের বিচির গাদার প্রলেপ দেওয়া হয়। তৈরি হয়ে যায় লক্ষ্মীসরা।
কোজাগরী পূর্ণিমায় অর্থাৎ আশ্বিনী পূর্ণিমায় বাংলাদেশের ঘরে-ঘরে লক্ষ্মীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। এর প্রধান অনুষঙ্গ হলো চিত্রিত লক্ষ্মীসরা। সরা চিত্রের বিষয়বস্তু মূলত ধনদেবী মা লক্ষ্মীকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত। তবে, লক্ষ্মী ছাড়া বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তি আঁকা হয় ভিন্ন-ভিন্ন নামের সরাতে। কোনো সরায় দেখা যায় লক্ষ্মী একা আছেন, বাহন হিসেবে পায়ের কাছে পেঁচা। কোনো সরায় যুগল লক্ষ্মী-নারায়ণ, কোথাও প্যানেল ভাগ করা হয়েছে—নিচে লক্ষ্মী, উপরে রাধাকৃষ্ণ। কোথাও মূল জায়গাটি নিয়েছেন দুর্গা, দুপাশে আছেন লক্ষ্মী-সরস্বতী। কোথাও প্যানেলের নিচে একা লক্ষ্মী, উপরে দেবী দুর্গা অসুর বধরত ইত্যাদি। লক্ষ্মীর মাথায় কোথাও মুকুট পরানো থাকে। কোথাও চুল থাকে বেণি বাঁধা। লক্ষ্মীর চেহারার মধ্যে দেবীসুলভ মহিমার বদলে একজন সুখী গৃহী রমণীর ভাবটিই ফুটে উঠতে দেখা যায়। প্রতিকৃতি হিসেবে সরস্বতী, নারায়ণ, দুর্গা, রাধাকৃষ্ণ—যা-ই থাকুক, সব সরায় একটি জিনিস সর্বজনীন, তা হলো দেবী লক্ষ্মীর অবস্থান। সে জন্যই এর নাম লক্ষ্মীসরা।

কারুশিল্পী সুশান্ত পাল
আঁকার ক্ষেত্রে কিছু নিয়ম মানা হয়। অঞ্চলভেদে যদিও সরার জমিনের রং, দেবদেবীর রূপ বা অলংকরণের বৈচিত্র্য দেখা যায়। এমনকি নির্মাণকৌশলের দিকে থেকেও বিভিন্ন অঞ্চলের সরার মধ্যে ভিন্নতা আছে। বাংলাদেশের চিত্রিত সরাকে ঢাকাই, ফরিদপুরী, আচার্য বা গণকী এবং সুরেশ্বরী—এই চার শ্রেণিতে ভাগ করা হয়। গণক ঠাকুরেরা যেগুলো তৈরি করেন, সেগুলোর নাম গণকা সরা বা আচার্যি সরা। এ সরা শরীয়তপুরের কাইলারা গ্রামের সরাশিল্পীরা এগুলো তৈরি করেন। ফরিদপুরে সুরেশ্বরী গ্রামে আরেক ধরনের সরা আছে, যা ‘সুরেশ্বরী সরা’ নামে পরিচিত। এর মূর্তিগুলো থাকে পৃথক-পৃথক কক্ষভুক্ত, স্পষ্ট ও জাঁকজমকপূর্ণ। ফরিদপুরের চান্দ্রা-মুখডোবা অঞ্চলের কুমারেরা এটি তৈরি করেন। লক্ষ্মীসরা এখন যে অঞ্চলেই তৈরি হোক না কেন, শৈলীর দিক থেকে এগুলো ‘ঢাকাই সরা’ এবং ‘ফরিদপুরী’ বা ‘সুরেশ্বরী সরা’ বলেই বেশি পরিচিত। ঢাকাই সরা অঙ্কন ও শৈলী ফরিদপুরের সরার মতন। তবে, এতে দেবী লক্ষ্মীকে ময়ূরপঙ্খিতে উপবিষ্ট অবস্থায় আঁকা হয়। এ ধরনের সরা তৈরির মূল কেন্দ্র বিক্রমপুরের বাসাইল ও আবিরপাড়া। বিক্রমপুরে দেখা মেলে ‘একলক্ষ্মী সরা’, ‘তিনপুতুল সরা’, ‘পাঁচপুতুল সরা’র। ঢাকার নবাবগঞ্জ, ধামরাই, কাশিমপুর ও মানিকগঞ্জে সরা তৈরি হয়। বিশেষত মানিকগঞ্জেও ‘জয়া-বিজয়া সরা’ নামে এক বিশেষ ধরনের লক্ষ্মীর সরার দেখা মেলে। এখানকার বেতিলা-মিতরা অঞ্চলের কুম্ভকারেরা তা তৈরি করেন। রং দেখেই নিশ্চিত হওয়া যায় এটি সেখানকার সরা। এর একটিতে থাকে দেবী লক্ষ্মী (হলুদ) এবং অন্যটিতে দেবী সরস্বতী (সাদা)। ঢাকার দোহারে একে বলা হয় ‘লক্ষ্মী-সরস্বতী সরা’। এ ছাড়া মানিকগঞ্জের সদর উপজেলার নবগ্রাম, ঘিওরের জাব্রা, শিবালয়ের তেওতা বা দৌলতপুরের চকমিরপুর অঞ্চলে যে রিলিফবিহীন সরার ঐতিহ্য দেখা যায়, এখানকার মানুষেরা তার নাম দিয়েছেন ‘সাদা সরা’। এর জমিন হয় সাদা। ঢাকাই বা ফরিদপুরী সরার জমিন থেকে তা ভিন্ন। এ দুই অঞ্চলের সরাতে খড়িমাটির সাদা আস্তর থাকে, তবে তা বার্নিশের প্রলেপের কারণে খানিকটা ঘিয়ে হয়ে যায়। অন্যদিকে মানিকগঞ্জের সাদা সরা নিরাভরণ অর্থাৎ সাদামাটা। রঙের ব্যবহারও কম। চাকচিক্য কম বলে মূল্য কম হয়। সরার বড় জোগান আসে এসব অঞ্চল থেকে।
মনসার ঘট: মাটির ছোট কলসকে সাধারণত ‘ঘট’ বলে। বাংলার সর্বত্র নানা প্রকরণের ঘট আছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য মঙ্গলঘট, দেবীঘট, শীতলাঘট, নাগঘট, লক্ষ্মীঘট, কার্তিকঘট, দ্বারঘট, ইতুঘট, ধর্মেরঘট, বারাঘট, মনসাঘট ইত্যাদি। চিত্রিত ঘটের মধ্যে আছে মনসা ও নাগঘট। নানারূপে-নানা নামে মনসা বাংলাদেশের সর্বত্রই পূজিত হয়। দক্ষিণবঙ্গে বিশেষত ফরিদপুর-বরিশাল অঞ্চলে মনসাকে প্রতিমার পরিবর্তে ঘটের মাধ্যমে পূজা করা হয়। দীর্ঘকাল ধরে ঘটপূজার মাধ্যমে মনসা শ্রাবণসংক্রান্তিতে এখানে ঘরে-ঘরে পূজিত হয়। মনসাঘটের আকৃতি খানিকটা লম্বাটে। ঘটের গায়ে উৎকীর্ণ চিত্রও বেশ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। কুম্ভকারদের তৈরি এই ঘটের উপর শিল্পীরা মনসার মূর্তি চিত্রণ করেন গঠনভঙ্গিমার সঙ্গে মিলিয়ে। উপরের ঘটের মুখের প্রসারিত কানা অংশটি হয়ে ওঠে দেবীর এক শিরোভূষণ। মনসার দুটি হাতের মুঠিতে ধরা থাকে একটি করে সাপ। একটানে দ্রুত রেখা টেনে আঁকা হয় ঠোঁট ও চিবুকের ভাঁজ, নাকে নথ, চোখের ভ্রু, ত্রিনয়ন এবং হাতের আঙুল। দেবীর গয়না হিসেবে উৎকীর্ণ করা হয় সাপ ও সাপের ফণার নকশা। দেবীর গায়ের রঙ হয় হলুদ এবং ঠোঁট আঁকা হয় সিঁদুরের বর্ণে। তবে দেবীর পরিধেয় বস্ত্রের রঙ কোনো কোনো ঘটে দেখা যায় সবুজ, বেশির ভাগই লাল। অক্ষিগোলকসহ দেবীর চোখ দুটি বিস্ফারিত এবং হাতের উপর কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা যায় বৃশ্চিকসদৃশ উল্কিরেখা। ঘটের নিচের অংশে অনেক সময় চিত্রিত হয় পদ্ম ফুলের অলংকরণ, যার উপরে থাকে দেবীর অধিষ্ঠান। এসব মিলিয়ে মনসার ঘটটি বেশ অর্থবহ ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এক লোকচিত্রকলার উদাহরণ। ঘটে দেবী মনসাকে পাওয়া যায় গর্ভবতী নারীরূপে। বরিশালের মৃৎশিল্পীরা মনসাঘট আঁকেন বিশেষ দক্ষতায়। দেশভাগের পরে প্রসিদ্ধ ঘটশিল্পীরা ভারতের মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও নদীয়ায় স্থানান্তরিত হন। সেখানে তাঁরা এ শিল্পের প্রসার ঘটান।
মনসাঘটের মতোই আরেক ধরনের চিত্রিত ঘট আছে যা ‘নাগঘট’ নামে পরিচিত। নাগঘটে এক বা একাধিক ফণাযুক্ত সাপের উপস্থিতি দেখা যায়। ফণার সংখ্যার উপরে ঘটের নামকরণ আলাদা হয়, যেমন— পাঁচটি নাগের ফণাযুক্ত ঘট ‘পঞ্চনাগঘট’ বা আট সাপের ফণাযুক্ত ঘটকে বলা হয় ‘অষ্টনাগঘট’। নাগঘটে শিল্পী নিপুণভাবে সাপের ফণা যুক্ত করেন এবং ঘটকে রঙিন করে তোলেন। নাগমূর্তিকে ত্রিমাত্রিকভাবে মাটি দিয়ে তৈরি করে ঘটের গায়ে জুড়ে দেওয়া হয়। তারপর খড়ি মাটির সাদা অথবা হলুদ রঙের প্রলেপ দেওয়া হয়। এই ঘটে কোনো আকৃতিই শুধু রঙ দিয়ে আঁকা হয় না। কালোর উপর লাল ও সাদা রঙের রেখা দিয়ে সাপের দেহকান্ড ও ফণাযুক্ত মাথা চিত্রিত করা হয়। ঘটের মাঝ বরাবর পরস্পর সম্পৃক্ত পদ্মদল এমনভাবে আঁকা হয় যেন ঘটের মুখটি প্রস্ফুটিত পদ্ম থেকে উদ্গত এবং ভেতর থেকেই নাগরাজ বেরিয়ে আসছে— এমনটা মনে হয়। নাগঘট বেশির ভাগ ক্ষেত্রে গাছের তলায় স্থাপিত থাকে, একে বিসর্জন দেওয়া হয় না।

মনসার ঘট ও শখের হাঁড়ি
শখের হাঁড়ি: বাংলার চিত্রিত মৃৎশিল্পের প্রধান একটি উদাহরণ ‘শখের হাঁড়ি’, যা বর্তমানে ‘রাজশাহীর শখের হাঁড়ি’ নামেই বেশি পরিচিত। এমন নামের সুনির্দিষ্ট কারণ অবশ্য জানা যায়নি, তবে রাজশাহীতেই তৈরি হওয়ায় এমনটা হয়েছে বলে মনে করা হয়। বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় একসময় শিল্পকলাটির প্রচলন ছিল। চাঁপাইনবাবগঞ্জের বারঘরিয়া, ঢাকার নয়ারহাট, রাজবাড়ীর গোয়ালন্দ, ফরিদপুরের কোয়েলজুড়ি, হাসরা, টাঙ্গাইলের কালীহাতি, জামালপুরের বাজরাপুর, ময়মনসিংহের বালাসুর, চট্টগ্রামের সীতাকুন্ড ইত্যাদি জায়গার কুমারেরা তৈরি করতেন নকশা করা নানা রকমের হাঁড়ি। এসবের কোনোটার ঢাকনা থাকতো, কোনোটার থাকত না। হাতলযুক্ত চিত্রিত হাঁড়িও ছিল। সামাজিক চাহিদা না থাকায় দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের কুমারেরা এখন এসব হাঁড়ি আর তৈরি করেন না। শত প্রতিবন্ধকতা পাড়ি দিয়ে বর্তমানে রাজশাহীতেই কেবল কয়েকজন হাঁড়িশিল্পী একে টিকিয়ে রেখেছেন। অঞ্চলভেদে শখের হাঁড়ি ‘শখের চুকাই’, ‘মঙ্গল হাঁড়ি’, ‘জাগরণ হাঁড়ি’, ‘আইবুড়ো হাঁড়ি’, ‘ফুল হাঁড়ি’, ‘ছিকার হাঁড়ি’, ‘রঙ্গের হাঁড়ি’ বা ‘রঙ্গের পাতিল’ ইত্যাদি নামে পরিচিত ছিল। এখন রাজশাহীতে মাত্র দুটি জায়গায় স্বল্প পরিসরে শখের হাঁড়ি তৈরি হয়। একটা রীতিকে বলা হয় পুঠিয়ার বাঙালপাড়ারীতি এবং অপরটি পবার বায়ার বসন্তপুররীতি। হাঁড়ির আকার-আকৃতি, রঙের ব্যবহার, মোটিফ ইত্যাদি দিক থেকে অঞ্চল দুটির রীতির মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। যদিও উভয় জায়গার শখের হাঁড়ির প্রধান অবলম্বন কুমারদের তৈরি মধ্যম আকৃতির হাঁড়ি। বিশেষ এ হাঁড়ির পেট হয় খানিকটা স্ফীত ও গলার কাছটা সামান্য বাঁকা, অনেকটা ভাতের হাঁড়ির মতন। তবে আকারে ছোট এবং ভাতের হাঁড়ির মুখটা যতটা প্রশস্ত হয় তার চেয়ে এর ঘের অনেক কম। বাঙালপাড়ার হাঁড়ির জমিন হলো লাল, তাতে সাদা-কালো রঙে সরিষা ফুল, রঙিন মাছ, চিরুনি ও পদ্মের মোটিফ আঁকা থাকে। অন্যদিকে বহুল পরিচিত বসন্তপুরের হাঁড়ির জমিন হলুদ রঙের। তার উপরে আঁকা হয় লাল, সবুজ, কালো ও নীল রঙের মাছ, পাখি ইত্যাদি। এ ছাড়া রাজশাহীর হরগ্রামে আরেকটি রীতি একসময় ছিল। সেখানকার হাঁড়ির জমিন হতো সাদা। পরে অন্যান্য রঙ দিয়ে সাদার ওপরে নানা ধরনের চিত্র আঁকা হতো হরগ্রামের হাঁড়িতে। শখের হাঁড়িতে যেসব মোটিফ দেখা যায়, সেগুলোর ভিন্ন-ভিন্ন তাৎপর্য আছে। যেমন পাখি প্রেম, মাছ উর্বরতা, পদ্ম সৌন্দর্য, চিরুনি রোমান্সের প্রতীক হিসেবে গণ্য। শখের হাঁড়ি চিত্রিত করার কাজটি বেশ জটিল। প্রথমে পোড়ামাটির হাঁড়িতে খড়িমাটি-গোলা তরল রঙ লাগিয়ে সাদা অথবা পিউরির (হালকা হলুদ) জমিন তৈরি করা হয়। এরপর কানা ও গলার কাছে একটি বা দুটি মোটা রেখা—যাকে শিল্পীরা তাঁদের ভাষায় বলেন ‘কশিটানা’, আঁকা হয়। মোটা কশি বা রেখা সর্বজনীনভাবে লাল রঙেরই হয়। এরপর কশিটানা হয় হাঁড়ির পেটের কাছে—মাঝামাঝি একটা আর একটা আধা ইঞ্চি নিচে। হাতের আঙুলের সাহায্যে তা করা হয়। কশিটানার পর হাঁড়ির গায়ে যে তল বা ফাঁকা জায়গা থাকে, সেখানে প্রয়োজনীয় মোটিফগুলো শিল্পীরা আঁকেন। সাবুর আঠা দিয়ে পাতিলের গা মুছে দেওয়া হয় রঙের ঔজ্জ্বল্য বাড়ানোর জন্য। জমিনে রঙের কাজ শেষ হলে পাতিলে বার্নিশ দেওয়া হয়। ধর্মনিরপেক্ষ এ শিল্পকলায় আগে প্রাকৃতিক রং ব্যবহার করা হতো, তবে এখন বাজার থেকে কেনা রং দিয়েই তা করা হয়। হাঁড়ির গায়ে প্রথমে প্রলেপের কাজটি সাধারণত বাড়ির মেয়েরা করেন। তবে, ছবি আঁকা ও নকশার যাবতীয় কাজ পুরুষ শিল্পীরা করেন। হরেন্দ্রচন্দ্র পাল, গোপালচন্দ্র পাল, চিত্তরঞ্জন পাল, লাল্টু পাল, নয়নাবালা পাল, লক্ষ্মীনারায়ণ পাল প্রমুখ ছিলেন এ শিল্পকলার স্বনামধন্য শিল্পী। তবে, বর্তমানে রাজশাহীর শখের হাঁড়ির সঙ্গে যে শিল্পীর নাম ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে, তিনি হলেন বসন্তপুরের সুশান্ত পাল। তাঁর হাতের জাদুতে রাজশাহীর শখের হাঁড়ি নতুন করে প্রাণ পেয়েছে। ছোটবেলা থেকে তিনি এ কাজের সঙ্গে যুক্ত। দেশব্যাপী রাজশাহীর শখের হাঁড়ির প্রসারে তিনি বড় ভূমিকা রেখে চলেছেন। দাদু ঘনেশ্বর পাল তাকে পরম মমতা দিয়ে শখের হাঁড়িতে অঙ্কনের জটিল কাজ শিখিয়েছিলেন। দাদুর কাছ থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা এবং নিজের উদ্ভাবনী গুণ এ দুয়ের সমন্বয়ে শখের হাঁড়িকে সুশান্ত পাল অন্য মাত্রায় নিয়ে গেছেন। শৌখিন এ শিল্পকলাকে বাঁচিয়ে রাখতে ছেলে সঞ্জয়কুমার পালকে দীক্ষিত করেছেন।
একসময় রাজশাহীতে মেয়ে বিদায়ের সময় কিংবা কন্যার প্রথম সন্তান হওয়ার পর বাপের বাড়ি থেকে যেসব উপহার পাঠানো হতো, তার প্রধান একটি অনুষঙ্গ ছিল শখের হাঁড়ি বা শখের চুকাই। এ ছাড়া শখের হাঁড়ি ব্যবহার করা হতো কুটুমবাড়িতে মিষ্টান্ন বা খই-চিড়া-মুড়ি-কদমা-চিনির সাজ ইত্যাদি মন্ডা-মিঠাই নেওয়ার জন্য। আজ তা আশ্রয় নিয়েছে শহুরে শিল্পবোদ্ধাদের ড্রইং রুমে। এমন করেই লোকশিল্প টিকে থাকে বৈকি!
লেখক: সহযোগী অধ্যাপক, ফোকলোর বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ও ডাকটিকিট সংগ্রাহক
ছবি: লেখক