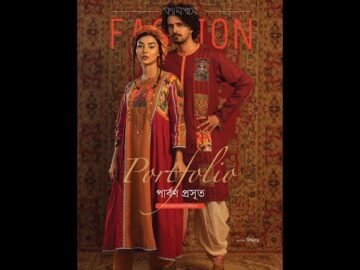বিশেষ ফিচার I পয়লার নয়া-পুরাণ পাঠ্য
বছরের প্রথম দিনে খাবারের উৎসবও মন ভরিয়ে দেয়। বাঙালির হেঁশেল থেকে আসা বিচিত্র মজাদার পদ যেন হারানো দিনের গৌরব এবং সৌরভ নিয়ে স্বাদেন্দ্রিয়ে ধরা দেয়। লিখেছেন পাঞ্চালি দত্ত
 দূষণ কেড়ে নিয়েছে শীত ও গ্রীষ্মের মাঝখানের ঋতুটি; তবু রঙের উৎসবে মেতে ওঠে দেশের আনাচকানাচ। মাস গড়িয়ে আসে বাঙালির নববর্ষ বা পয়লা বৈশাখ। বাংলায় নবাবি আমলে নববর্ষের দিনে ‘পুণ্যাহ’বা ‘পুণ্য উৎসব’উদযাপন করা হতো। তবে তার জন্য নির্দিষ্ট কোনো দিন ছিল না। সুবিধে-অসুবিধেয় মাসের তারিখ পাল্টে যেত। সেদিন রাজ্যের জমিদারদের ডেকে আনা হতো রাজধানীতে। দরবারে নবাব নিজে এবং তার দেওয়ান ও খাজাঞ্চি উপস্থিত থাকতেন। সেখানে নির্ধারিত রাজস্বের টাকা নিয়ে হাজির হতে হতো জমিদারদের। যিনি খাজনার টাকা জুটিয়ে উঠতে পারতেন না, তাঁকে কারাগারে বন্দি করে রাখা হতো। খাজনার টাকা নবাবের কাছে জমা করার পর জমিদার মুক্তি পেতেন। কেউ পালানোর চেষ্টা করলে, তাকে ধরে আনা হতো। ফলত তিনি জেল খাটতেন ও জমিদারি হারাতেন। তখনকার যুগে বাংলা নববর্ষ ছিল অনাড়ম্বর একটি উৎসব, যা সীমাবদ্ধ ছিল ব্যবসায়ীদের হালখাতার মধ্যেই। দোকানে সেদিন গণেশ পূজা, নতুন খাতায় সিঁদুর লাগানো ও মুদ্রার ছাপ দিয়ে শুরু হতো নতুন বছরের নতুন হিসাব-নিকাশ। পুরোনো লেনদেন পর্ব সেদিন মিটিয়ে ফেলা হতো। এই উৎসবের ফলে ব্যবসাকে দেনার হাত থেকে যেমন বাঁচানো যেত, তেমনি নিয়মিত খদ্দেরদের সেদিন মন্ডা-মিঠাই সহযোগে আপ্যায়ন করিয়ে ‘ক্রেতা-বিক্রেতা’ সম্পর্ককে আরও জোরালো করা হতো। আজও সে প্রথা টিকে আছে। বাংলা নববর্ষ উৎসব সম্পর্কে কালীপ্রসন্ন সিংহ ‘হুতোমপ্যাঁচার নক্সা’য় লিখেছেন, ‘আজ বৎসরের শেষ দিন। আজ বুড়োটি বিদায় নিলেন, কাল যুবটি আমাদের উপর প্রভাত হবেন।… ইংরেজরা নিউ ইয়ারে বড় আমোদ করেন। আগামীকে দাড়াগুয়া পান দিয়ে বরণ করে ন্যান-নেশার খোঁয়ারির সঙ্গে পুরাণকে বিদায় দেন। বাঙালির বছরটি ভালো রকমেই যাক আর খারাপেই শেষ হক, সজনে খাড়া চিবিয়ে ঢাকের বাদ্দি আর রাস্তার ধুলো দিয়ে পুরাণকে বিদায় দ্যান। কেবল কলসী উচ্ছুগগু কর্তারা আর নতুন খাতাওয়ালারাই নতুন বৎসরের মান রাখেন।’
দূষণ কেড়ে নিয়েছে শীত ও গ্রীষ্মের মাঝখানের ঋতুটি; তবু রঙের উৎসবে মেতে ওঠে দেশের আনাচকানাচ। মাস গড়িয়ে আসে বাঙালির নববর্ষ বা পয়লা বৈশাখ। বাংলায় নবাবি আমলে নববর্ষের দিনে ‘পুণ্যাহ’বা ‘পুণ্য উৎসব’উদযাপন করা হতো। তবে তার জন্য নির্দিষ্ট কোনো দিন ছিল না। সুবিধে-অসুবিধেয় মাসের তারিখ পাল্টে যেত। সেদিন রাজ্যের জমিদারদের ডেকে আনা হতো রাজধানীতে। দরবারে নবাব নিজে এবং তার দেওয়ান ও খাজাঞ্চি উপস্থিত থাকতেন। সেখানে নির্ধারিত রাজস্বের টাকা নিয়ে হাজির হতে হতো জমিদারদের। যিনি খাজনার টাকা জুটিয়ে উঠতে পারতেন না, তাঁকে কারাগারে বন্দি করে রাখা হতো। খাজনার টাকা নবাবের কাছে জমা করার পর জমিদার মুক্তি পেতেন। কেউ পালানোর চেষ্টা করলে, তাকে ধরে আনা হতো। ফলত তিনি জেল খাটতেন ও জমিদারি হারাতেন। তখনকার যুগে বাংলা নববর্ষ ছিল অনাড়ম্বর একটি উৎসব, যা সীমাবদ্ধ ছিল ব্যবসায়ীদের হালখাতার মধ্যেই। দোকানে সেদিন গণেশ পূজা, নতুন খাতায় সিঁদুর লাগানো ও মুদ্রার ছাপ দিয়ে শুরু হতো নতুন বছরের নতুন হিসাব-নিকাশ। পুরোনো লেনদেন পর্ব সেদিন মিটিয়ে ফেলা হতো। এই উৎসবের ফলে ব্যবসাকে দেনার হাত থেকে যেমন বাঁচানো যেত, তেমনি নিয়মিত খদ্দেরদের সেদিন মন্ডা-মিঠাই সহযোগে আপ্যায়ন করিয়ে ‘ক্রেতা-বিক্রেতা’ সম্পর্ককে আরও জোরালো করা হতো। আজও সে প্রথা টিকে আছে। বাংলা নববর্ষ উৎসব সম্পর্কে কালীপ্রসন্ন সিংহ ‘হুতোমপ্যাঁচার নক্সা’য় লিখেছেন, ‘আজ বৎসরের শেষ দিন। আজ বুড়োটি বিদায় নিলেন, কাল যুবটি আমাদের উপর প্রভাত হবেন।… ইংরেজরা নিউ ইয়ারে বড় আমোদ করেন। আগামীকে দাড়াগুয়া পান দিয়ে বরণ করে ন্যান-নেশার খোঁয়ারির সঙ্গে পুরাণকে বিদায় দেন। বাঙালির বছরটি ভালো রকমেই যাক আর খারাপেই শেষ হক, সজনে খাড়া চিবিয়ে ঢাকের বাদ্দি আর রাস্তার ধুলো দিয়ে পুরাণকে বিদায় দ্যান। কেবল কলসী উচ্ছুগগু কর্তারা আর নতুন খাতাওয়ালারাই নতুন বৎসরের মান রাখেন।’
আজকাল বাঙালিরা ‘বাংলিশ’ বলুক কিংবা ইংরেজি আদব-কায়দাকে রপ্ত করার যত চেষ্টা করুক, বছরের এই দিনটিতে নিজেকে বাঙালিয়ানায় ভরিয়ে তুলতে চায় এক শ ভাগ। সেটা ভোজন, সাজপোশাক কিংবা রবীন্দ্রনাথকে ঘিরেই হোক না কেন! পশ্চিমবঙ্গের প্রায় প্রতিটি কালচারাল হলে চলে অনুষ্ঠান। ‘এসো হে বৈশাখ’ গানের সুরে আমন্ত্রণ জানানো হয় নতুন বর্ষকে। রাস্তাঘাটে ভিড়, রিলিজ হওয়া নতুন সিনেমা দেখার উৎসাহ, রেস্তোরাঁয় বাঙালি খাবারের হিড়িক ইত্যাদিতে শহর ব্যস্ত হয়ে পড়ে। হুতোমের সেকালের নববর্ষ থেকে একালের নববর্ষের উদ্যাপনে জাঁকজমক অনেক বেশি, কিন্তু সময়াভাবে হারিয়ে গেছে সেই সব ছোট্ট ছোট্ট রীতি। অফিশিয়াল ভাষা ইংরেজি ও হিন্দি হওয়ায় বাংলা ভাষা আপাতত যেন শীর্ণকায় নদীর রূপ ধারণ করতে চলেছে। বাঙালির নানা বিশেষণ যেমন ল্যাদখোর, আঁতেল, রাজনীতি ‘বিশেষ’অজ্ঞ ইত্যাদির মধ্যে একটি বিশেষ পরিচিতি হলো ভোজনরসিক বা পেটুক। বাকি উৎসবের মতোই ভোজনরসিক বাঙালির সেদিন চলে ভরপুর খানাপিনা। ফর্দ কিন্তু পুরোপুরিভাবেই বাঙালি। যাদের হাত পুড়িয়ে খাবারের ইচ্ছে নেই, তাদের জন্য রয়েছে বাঙালি রেস্তোরাঁ; যেখানে শুক্তো, অম্বল, পাতুরি, শাক, বড়ি ভাজা, গন্ধরাজ ঘোল, কষা মাংস এবং আরও অনেক খাবার, বিশেষভাবে যেগুলোর রান্না সময়াভাবে আজকাল বাড়িতে প্রায় করাই হয় না। শীর্ণকায় নদীটির দিকে তাকিয়ে কোথাও রক্তের টানে আজও আমরা গান গাই: ‘বাংলা আমার সর্ষে ইলিশ চিংড়ি কচি লাউ, বাংলা পারশে মাছকে ধুয়ে জিরার বাটায় দাও। বাংলা ভুলি কি করে, বাংলা বুকের ভিতরে …।’ গিয়াসুদ্দিনের লেখা এই কবিতা এবং কল্যাণ সেন বরাটের সুর দেওয়া এই গান রসনাকে যেভাবে ছুঁয়ে থাকে, ঠিক তেমনি বারবার প্রেমে পড়তে ইচ্ছে করে বাঙালির গুণ, দোষ সবটুকুকে নিয়ে।
একটু ফিরে তাকালে দেখতে পাই হাজার বছর আগে বাঙালির ভোজ্য, রুচি বা কীভাবে এ ধরনের খাদ্যগুলো পাতে জায়গা করে নিয়েছিল, তার কোনো লিখিত বিবরণ নেই। তবে সুকুমার সেন ও নীহাররঞ্জন রায় উল্লেখ করেন যে প্রাচীনকালে সাধারণ বাঙালির খাদ্যাভ্যাস বা খাদ্যরুচির খবর পাওয়া গিয়েছিল প্রাকৃত পৈঙ্গলে। খুবই সাধারণ উপকরণ দিয়ে তৈরি সেসব খাবার যা বর্তমানে লুপ্তপ্রায়। অথচ সেসব খাবারের এক টুকরো সুখানুভূতির স্বাদ স্পর্শ করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠি। সবজি, ফল, মাছ, মাংসে নানা রকম সার ও কেমিক্যাল প্রয়োগের ফলে আমরা সেই অমৃত স্বাদের সুখ থেকে বঞ্চিত। খেয়াল করলে দেখা যায়, এখন আমরা অনেক বেশি রকম মসলা ব্যবহার করি রান্নায় শুধু ‘জোলো’ স্বাদে আরেকটু চমক আনতে। বাঙালির সহজ-সরল খাদ্যাভ্যাসের খবরটি প্রাকৃত ভাষায় পাই:
ওগগর ভত্তা রম্ভও পত্তা গাইক ঘিত্তা দুগ্ধ সঞ্জুত্তা মোহিলি মচ্ছা নালিচগচ্ছা দিমুই কন্তা খায় পুনবন্তা।
অর্থাৎ কলাপাতায় গব্য ঘৃতসহকারে ফেনা ওঠা গরম দুধ সংযুক্ত ভাত, নালিতা শাক, মৌরলা মাছ … এই খাদ্য যার স্ত্রী তাকে পরিবেশন করেন, তিনি পুণ্যবান (শ্রীহর্ষ রচিত ‘প্রাকৃত পৈঙ্গল’)।
আহা! সাধারণ উপকরণ; কিন্তু স্বাদ ও পরিবেশনের গল্প শুনে ভরা পেটেও খিদে চাগিয়ে ওঠে। মনে পড়ে যায় মাটির রান্নাঘরে মা পিঁড়ি পেতে দিতেন। এক পাশে জ্বলত মাটির দুই উনুন। একটাতে হয়তো বসানো ভাতের হাঁড়ি, অপরটায় দুধ। গাইয়ের দুধ ফুটিয়ে ঘন করা হতো দই পাতার জন্য। অথবা তৈরি হতো ক্ষীর। কাঁসার থালায় মা বেড়ে দিতেন ধোঁয়া ওঠা ভাত, সঙ্গে নিমবেগুন (চৈত্র ও বৈশাখ মাসের তেতো ছিল নিত্যনৈমিত্তিক পদ)। তখন খুব রাগ করতাম তেতো খাব না বলে। আজকাল মন টানে সেই তেতো খাবারটির জন্য। হয়তো হাসছেন শুনে যে, এ আবার কী আহামরি পদ। হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন। নিমতেতো আমার হেঁশেলেও হয়, কিন্তু কোথাও যেন কিছু একটা অপূর্ণতা, শূন্যতা থেকে যায়; ছোটবেলায় অন্তঃকরণে লেগে থাকা সেই স্বাদকে ছুঁতে অসমর্থ হয় বারবার। নেই সেই ঘিয়ের দূর থেকে ভেসে আসা সৌরভ, নেই কলাপাতার সেই কোমল সবুজ গন্ধ, নেই সেই চালের ম-ম সুবাস … তেতোর কথা যখন চলে এলো, এ বিষয়ে একটু না লিখলে মন সায় দেয় না। কারণ, বাঙালির অনুষ্ঠানে খাবারের ফর্দে শুক্তো একটি বিশেষ জায়গা অধিকার করে থাকে, যাতে তেতোর একটি উপকরণ আমরা যোগ করি। বঙ্গদেশে ব্যবসাসূত্রে বণিকদের দীর্ঘদিন সমুদ্রযাত্রা করার ফলে ভাঁড়ারে পড়ত টান। সেই ভাঁড়ারের বন্দোবস্ত করতে নানা রকম পাতা শুকিয়ে বস্তাবন্দী করা হতো। যখন রসদ শেষ হওয়ার পথে, এই শুকনো পাতাগুলো ফুটিয়ে তৈরি করা হতো ঝোল। সেটাই আদি শুক্তো। কখনোসখনো বিশেষ কিছু সবজিও শুকিয়ে রাখা হতো ভাঁড়ারে। এভাবেই ধীরে ধীরে বাঙালির রুচির পরিবর্তন ঘটে। ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা রেসিপিগুলোকে একত্র এবং সুব্যবস্থিত করার জন্য বাংলায় প্রথম রান্নার বই প্রকাশিত হয়, যার নাম ‘পাক রাজেশ্বর’। শ্রী বিশ্বেশ্বর তর্কালঙ্কার ছিলেন বর্ধমান রাজবাড়ীর সদস্য। তিনি এই উদ্যোগ নেন এবং ১৮৩১ সালের ১ অক্টোবর তৎকালীন মহারাজ শ্রী মেহতাবচন্দের উৎসাহে ও ব্যয়ে প্রকাশিত হয় পাক রাজেশ্বর। বইটিতে মাংস রান্নায় কোথাও পেঁয়াজ ব্যবহার করা হয়নি। তখনকার যুগে মাছেও পেঁয়াজ ছিল ব্রাত্য। এর প্রায় ২৭ বছর পর ‘ব্যঞ্জন রত্নাকর’ নামে আরেকটি বই তিনি লেখেন। প্রায় আড়াই হাজার পদ মিলিয়ে নিরামিষ ও আমিষে এক আলোড়ন সৃষ্টি হয় বাংলার হেঁশেলে। পরবর্তীকালে অর্থাৎ ১৮৫৭ সালে বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায়ের লেখা ‘মিষ্টান্ন পাক’ এবং ১৮৮৫ সালে তাঁর আরেকটি লেখা বই ‘পাক প্রণালী’ বাংলার রান্নাজগতে এক আলাদা মর্যাদা কুড়োয়। আরেকজনের কথা এ ক্ষেত্রে না উল্লেখ করলে বাংলার রান্না অসম্পূর্ণ থেকে যাবে; তিনি হলেন ঠাকুরবাড়ির মেয়ে প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী। এই ক্ল্যাসিক রান্নাগুলোকে আধার করেই পাতে চলে এসেছে আধুনিক বাঙালির রকমারি পদ।
নিরামিষ রান্নায় যেসব সুস্বাদু পদ ও স্টক রয়েছে, জানি না পৃথিবীর আর কোথাও আছে কি না! তার কারণ ছিল দুটো। এক. বাল্যবিবাহের ফলে অল্প বয়সে বিধবা হয়ে যেতেন মহিলারা এবং বিধবাদের কঠোরভাবে বারণ ছিল আমিষ খাবার। সেই থেকে সৃষ্টি নানা ধরনের নিরামিষ পদ। নিষেধ ছিল পেঁয়াজ ও রসুন ব্যবহারও। দুই. বৈষ্ণব উপাসকেরা ছিলেন নিরামিষাশী। ফলে এক বিশাল গোষ্ঠী নির্ভর ছিল নিরামিষ আহারে। বাটা, ভাজা, পুর, ডাল, অম্বল, শুক্তো, চচ্চড়ি, ঝোল, ঝাল, লাবড়া, বড়ি, ছেঁচকি, ঘণ্টা… অর্থাৎ দৈনন্দিন রান্নাকে নানাভাবে পাল্টে রুচিকর করে তুলতেন এই স্টাইলের ওপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে। চৈতন্য-চরিতামৃতে বিভিন্ন রকম নিরামিষ আহারের উল্লেখ পাই:
‘দশ প্রকার শাক নিম্ব সুকুতার ঝোল
মরিচের ঝাল ছেনাবড়া বড়ি ঘোল
দুগ্ধ তুম্বী দুগ্ধ কুষ্মান্ড বেশারি লাফরা
মোচা ঘণ্ট, মোচা ভাজা বিবিধ শাকরা
বৃদ্ধ কুষ্মান্ড বড়ির ব্যঞ্জন অপার
ফুলবড়ি ফল মূলে বিবিধ প্রকার’
এ রকম শুধু অজস্র নিরামিষ পদ নয়, সুজলা সুফলা নদীমাতৃক দেশে মৎস্যপ্রিয় বাঙালির ভাঁড়ারে রয়েছে মাছের সুস্বাদু অসংখ্য পদ। প্রাচীন ও মধ্যযুগে যেমন পাই মাছ ও মাংসের নানা উল্লেখ, মৃগ মাংস, চেং মাছ, ছাগ মাংস, কাতলার মুড়ার রসা, ভেকুট, কই ঝালভাজা, মাছের ডিমের বড়া ইত্যাদি। বর্তমানে মাছ ও মাংসে প্রচুর পরিমাণে পেঁয়াজ, রসুন, টমেটো, কাজুবাটা, চারমগজবাটা ব্যবহার করা হয়, এগুলো আদতে বাঙালি রান্নায় ছিল না। সময়ের স্রোতে পরিবর্তন স্বাভাবিক। তবে অনেক রান্না হারিয়ে গেছে এবং যাচ্ছে। কারণ, বহু উপকরণ লুপ্তপ্রায়। এ ছাড়া সময়াভাব; নিউক্লিয়ার পরিবারের ফলে সঠিক প্রণালিতে রন্ধনের পথপ্রদর্শক না থাকা।
ছোটবেলায় দেখতাম, বিভিন্ন জায়গায় চড়কের মেলা বসত। চলত পয়লা বৈশাখ পর্যন্ত। চড়কের সেই হাড় হিম করা খেলাগুলো দেখে বাড়ি ফেরার পথে প্রশ্নে কাহিল করে ফেলতাম বাবা-মাকে। এখন আর তেমন বিষয়গুলো চোখে পড়ে না। শুনেছি খাস কলকাতার বুকে এখনো চড়ক হয় ছাতুবাবু লাটুবাবুর বাজারে। চৈত্রসংক্রান্তি পর্যন্ত অর্থাৎ এক মাস ধরে চলে গাজনের নানা অনুষ্ঠান। চরকিতে গাজনেরা নানাভাবে খেলা দেখায়, যা দেখলে ভয় লাগে যে কেমন করে শরীরকে এত কষ্ট দিয়ে খেলাগুলো তারা অনায়াসে সম্পন্ন করে! পাপি পেট কা সওয়াল হ্যায়। কিন্তু তারা বিশ্বাস করে যে ঈশ্বর স্বপ্নাদিষ্ট করেন এবং সে ভাগ্য সবার কপালে জোটে না। যারা স্বপ্নাদিষ্ট হন, তারা এক মাস ধরে পালন করেন ব্রত। সে সময় পুকুরে নাকি ভেসে আসে কাঠ। সেই শাল কাঠের মাথায় বাঁশের দুই ধারে দুই গাজন নিজেদের বাঁধে। এরপর চরকিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়। তারা খেলা দেখাতে থাকেন কাঁটাঝাঁপ, বঁটিঝাঁপ, জিভে কাঁটা, পিঠে কাঁটা ইত্যাদি। মূলত ডোম, বাগদি, ক্যাওড় শ্রেণির লোকেরাই এতে অংশগ্রহণ করে। নামকরা বনেদিবাড়ি ছাতুবাবু লাটুবাবুর আমলে এই গাজনদের এক মাসের থাকা-খাওয়ার বন্দোবস্ত হতো তাঁদের বাড়ি থেকেই। কিন্তু আগের সেই ঠাটবাট নেই, তাই এখন চড়ক মিটে যাওয়ার পর পয়লা বৈশাখের দুপুরে এদের ‘আঁশপানা’ করানো হয়। অর্থাৎ এক মাসের সন্ন্যাস ব্রত ভেঙে ওই দিন মাছ-মাংসসহকারে ভরপেট খাওয়ানো হয় মোটামুটি ১৫০ থেকে ২০০ জনকে। এটা হয় ছাতুবাবু লাটুবাবুর বাড়িতে।
শেষ করছি আবার গিয়াসুদ্দিনের সেই কবিতার কয়েকটি লাইন দিয়ে:
‘শীতের ভোরে বেওরা পুকুর, টুসু গানের সারি
নতুন চালের ভাপা পিঠে সরুচাকলি আহামরি,
বাংলা ভুলি কি করে, বাংলা বুকের ভেতরে’
বাংলার ঐতিহ্যবাহী খাবার, পিঠে ইত্যাদিকে বাঁচিয়ে রাখতে বিভিন্ন খাদ্য উৎসব পশ্চিমবঙ্গের নানা জায়গায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এর সুফলও আমরা দেখতে পাচ্ছি। ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় যখন ঘুরতে যাই, উচ্চারণ শুনে বলে—আপ বেঙ্গলি হ্যায়? সম্মতি জানাতেই প্রথম কথা, বেঙ্গলি ভাষা বহত হি মিঠা হ্যায়। তারপর যথারীতি খাবারের গল্প ঢুকে পড়ে এবং প্রথম যে খাবারটির নাম উচ্চারিত হয়, সেটা হলো রসগুল্লা, মানে রসগোল্লা। স্বপ্ন দেখি, একদিন বাংলা ভাষা বিশ্বে দাপিয়ে বেড়াবে, ঠিক ওই রসগোল্লার রসের ধারার মতোই।
লেখক: কলকাতার হ্যাংলা হেঁশেলের সাংবাদিক