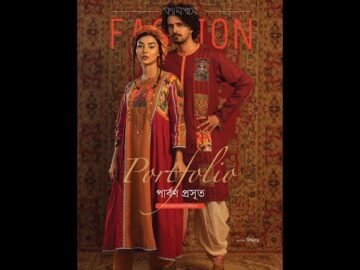কভারস্টোরি I মৎস্যকথা
বিবর্তনবাদী বিজ্ঞানীদের মতে, এটি থেকেই অন্যান্য জীবের উৎপত্তি। প্রায় একই ইঙ্গিত আছে আর্যপুরাণে। সভ্যতায় পৌঁছানোর গুটিকয়েক নিয়ামকের মধ্যে মাছ খেতে শেখাও একটি। ধারণা করা হয়, এই প্রাণী শিকার করতে করতে মানুষ ছড়িয়ে পড়েছিল বিশ্বব্যাপী। জাদুবিশ্বাসকে কেন্দ্র করে প্রাণীটি ঠাঁই পেয়েছে বিয়েশাদির আনুষ্ঠানিকতায়। এ নিয়ে রয়েছে বিচিত্র মিথ। লিখেছেন শিবলী আহমেদ
 তিরাশি বছর আগের কথা। দক্ষিণ আফ্রিকার একজন জেলের জালে ধরা পড়েছিল ‘অদ্ভুত’ একটি মাছ। গায়ের রং নীল, লম্বায় পাঁচ ফুট। সাধারণ মাছ মনে হওয়ায় জেলের কাছে সেটি আলাদা কদর পায়নি। ফেলে রাখা হয়েছিল অযত্নে। বরফ ছাড়া। ফলে পচন ধরতে সময় লাগল না। ঘটনাক্রমে মাছটি বৈজ্ঞানিকদের হাতে পৌঁছায়। ততক্ষণে সেটি পচে-গলে একাকার প্রায়। অবশিষ্ট ছিল কিছু হাড়গোড় ও ছাল। তা পরখ করেই গবেষকেরা নিশ্চিত হলেন- এটি সাধারণ মাছ নয়। এ হলো ‘কোয়েলাকান্থ’। তৎকালীন বিজ্ঞানীদের কাছে তা ছিল বিস্ময়কর। যে মাছের পাঁচ কোটি বছর পুরোনো ফসিল তারা পাথর খুঁচে পেয়েছেন এবং যেটির বিষয়ে বইপত্রে পড়েছেন, সেটিই এখন নাগালে। মাছের এই জাত ডাইনোসরের চেয়েও পুরোনো। মানুষের হিসাব থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেছে অনেক আগেই। কিন্তু জেলেরা জানিয়েছে, এ রকম আরও মাছ নাকি মেলে মাদাগাস্কারে। এরপর কোয়েলাকান্থ ধরা পড়লে সেটিকে যেন যত্নআত্তি করে গবেষকদের হাতে তুলে দেওয়া হয়, সে উদ্দেশ্যে ১৯৩৮ সালে একটি বিজ্ঞাপন ছাপা হয়েছিল। তাতে লেখা ছিল: এ রকম একটি মাছ আপনার ভাগ্য বদলে দিতে পারে। তাই তা ধরতে কিংবা জোগাড় করতে পারলে কাটাকুটি অথবা চাঁচাছোলা না করে মাছটিকে বরফে পুরে ফেলুন। কোনো দায়িত্বশীল কর্মকর্তার কাছে তা পৌঁছে দিন এবং তাকে বলুন অধ্যাপক জে. এল. বি. স্মিথ, রোডস বিশ্ববিদ্যালয়, গ্রেহাম্স্ টাউন, দক্ষিণ আফ্রিকা- এই ঠিকানায় টেলিগ্রাফ করতে।
তিরাশি বছর আগের কথা। দক্ষিণ আফ্রিকার একজন জেলের জালে ধরা পড়েছিল ‘অদ্ভুত’ একটি মাছ। গায়ের রং নীল, লম্বায় পাঁচ ফুট। সাধারণ মাছ মনে হওয়ায় জেলের কাছে সেটি আলাদা কদর পায়নি। ফেলে রাখা হয়েছিল অযত্নে। বরফ ছাড়া। ফলে পচন ধরতে সময় লাগল না। ঘটনাক্রমে মাছটি বৈজ্ঞানিকদের হাতে পৌঁছায়। ততক্ষণে সেটি পচে-গলে একাকার প্রায়। অবশিষ্ট ছিল কিছু হাড়গোড় ও ছাল। তা পরখ করেই গবেষকেরা নিশ্চিত হলেন- এটি সাধারণ মাছ নয়। এ হলো ‘কোয়েলাকান্থ’। তৎকালীন বিজ্ঞানীদের কাছে তা ছিল বিস্ময়কর। যে মাছের পাঁচ কোটি বছর পুরোনো ফসিল তারা পাথর খুঁচে পেয়েছেন এবং যেটির বিষয়ে বইপত্রে পড়েছেন, সেটিই এখন নাগালে। মাছের এই জাত ডাইনোসরের চেয়েও পুরোনো। মানুষের হিসাব থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেছে অনেক আগেই। কিন্তু জেলেরা জানিয়েছে, এ রকম আরও মাছ নাকি মেলে মাদাগাস্কারে। এরপর কোয়েলাকান্থ ধরা পড়লে সেটিকে যেন যত্নআত্তি করে গবেষকদের হাতে তুলে দেওয়া হয়, সে উদ্দেশ্যে ১৯৩৮ সালে একটি বিজ্ঞাপন ছাপা হয়েছিল। তাতে লেখা ছিল: এ রকম একটি মাছ আপনার ভাগ্য বদলে দিতে পারে। তাই তা ধরতে কিংবা জোগাড় করতে পারলে কাটাকুটি অথবা চাঁচাছোলা না করে মাছটিকে বরফে পুরে ফেলুন। কোনো দায়িত্বশীল কর্মকর্তার কাছে তা পৌঁছে দিন এবং তাকে বলুন অধ্যাপক জে. এল. বি. স্মিথ, রোডস বিশ্ববিদ্যালয়, গ্রেহাম্স্ টাউন, দক্ষিণ আফ্রিকা- এই ঠিকানায় টেলিগ্রাফ করতে।
 কোয়েলাকান্থ খুঁজে পাওয়া বিজ্ঞানীদের কাছে এতটাই গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে বিজ্ঞাপনটি যাতে কারও বুঝতে অসুবিধা না হয়, সেই উদ্দেশ্যে তিনটি ভাষায় তা ছাপা হয়েছিল। পাশাপাশি ঘোষিত হয় পুরস্কার। এ ধরনের মাছের প্রতিটির জন্য এক শ পাউন্ড দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয় কর্তৃপক্ষ; যা তৎকালীন প্রায় ৭০ হাজার টাকা। কিন্তু বিজ্ঞাপন দিয়েও দ্রুত ফল পাওয়া যায়নি। দ্বিতীয় কোয়েলাকান্থটি মেলে ১৯৫২ সালে। আফ্রিকার মাদাগাস্কারের কাছাকাছি। তারপর ১৯৫৬ সালের ৪ মে আরেকটি পাওয়া গেছে বলে সেই সময়ের পত্রিকায় খবর বেরিয়েছিল।
কোয়েলাকান্থ খুঁজে পাওয়া বিজ্ঞানীদের কাছে এতটাই গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে বিজ্ঞাপনটি যাতে কারও বুঝতে অসুবিধা না হয়, সেই উদ্দেশ্যে তিনটি ভাষায় তা ছাপা হয়েছিল। পাশাপাশি ঘোষিত হয় পুরস্কার। এ ধরনের মাছের প্রতিটির জন্য এক শ পাউন্ড দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয় কর্তৃপক্ষ; যা তৎকালীন প্রায় ৭০ হাজার টাকা। কিন্তু বিজ্ঞাপন দিয়েও দ্রুত ফল পাওয়া যায়নি। দ্বিতীয় কোয়েলাকান্থটি মেলে ১৯৫২ সালে। আফ্রিকার মাদাগাস্কারের কাছাকাছি। তারপর ১৯৫৬ সালের ৪ মে আরেকটি পাওয়া গেছে বলে সেই সময়ের পত্রিকায় খবর বেরিয়েছিল।
বিবর্তনবাদী বিজ্ঞানীদের কাছে কোয়েলাকান্থের গুরুত্ব ব্যাপক। তাদের বক্তব্য, কয়েক কোটি বছর আগে ডাঙায় কোনো প্রাণীই বাস করত না। তখন উভচরের উদ্ভবও হয়নি। ছিল শুধুই জলজ জীব। পাঁচ থেকে সাত কোটি বছর আগে পৃথিবীর জলবায়ু জলজ প্রাণীর প্রতিকূলে চলে গিয়েছিল। দীর্ঘ অনাবৃষ্টিতে ভূপৃষ্ঠ ধীরে ধীরে পানিশূন্য হয়ে পড়ে। ফলে কানকোযুক্ত জলজ প্রাণীর টিকে থাকা কঠিন হয়ে পড়েছিল। তবে কোনো প্রাণীই সহজে বিলুপ্ত হতে চায় না। বাঁচার জন্য সংগ্রাম করে, পরিবর্তিত পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজিত হতে চায়। নতুন জলবায়ুতে টিকে থাকার জন্য প্রাণীদের শরীরে প্রয়োজনীয় অঙ্গের সৃষ্টি হয়। তবে তা হুট করে নয়। এই বিবর্তন ঘটে লাখ লাখ বছর ধরে। পানি ঘাটতির পৃথিবীতে জলজ প্রাণীদের শরীরে ফুসফুস গজাতে শুরু করে। পাশাপাশি থাকল কানকোও। অর্থাৎ, পানি না পেলেও সেসব প্রাণী ডাঙায় এসে ফুসফুসের মাধ্যমে শ্বাস নেওয়ার যোগ্য হয়ে উঠেছিল। স্থলে চলাচলের জন্য এদের ডানার পেছনে ঢিপির মতো ‘লোব’ তৈরি হয়েছিল। ফুসফুসওয়ালা লোবযুক্ত তেমনই একটি মাছ হলো কোয়েলাকান্থ।
 মূলত আদি জলজ প্রাণী দুটি শাখায় বিবর্তিত হয়েছে। একটি হলো আজকের সাধারণ মাছ, আরেকটি ফুসফুসযুক্ত ঢিপিওয়ালা মাছ তথা ‘লোব ফিনড ফিশ’। এই লোবগুলোই বিবর্তিত হয়ে উন্নত প্রাণীর হাত, পা ও ডানা তৈরি হয়েছে বলে বিবর্তনবাদী বিজ্ঞানীদের অভিমত। কোয়েলাকান্থ একটি আদিম লোব ফিনড ফিশ। এ কারণেই বিজ্ঞানীদের কাছে সেটির এত কদর। ১৯৩৮ সালে প্রথম যেই কোয়েলাকান্থ পাওয়া যায়, বিজ্ঞানীরা সেটির নাম দেন ‘লাতিমারিয়া সালুম্নে’। ১৯৫২ সালেরটির নাম ‘ম্যালেনিয়া আঁজুয়ানে’। বিবর্তনের রেখা ধরে পিছু হাঁটলে হয়তো দেখা যাবে আজকের মানুষ, পাখি কিংবা বাঘ- সবারই আদি জীব ওই কোয়েলাকান্থ, যা বিশেষ এক প্রকার মাছ মাত্র। শুধু যে বিবর্তনবাদেই এসব ফিরিস্তি আছে, তা নয়। ভারতীয় আর্যদের পৌরাণিক মতে, ভগবান প্রথমে ‘মৎস্য’ অবতার হন, তারপর ‘কূর্ম’, এরপর ‘বরাহ’, পরে ‘নৃসিংহ’। মানে, ভগবান প্রথমে মাছ, তারপর কচ্ছপ, তৃতীয়তে শূকর এবং চতুর্থে নৃসিংহ। সৃষ্টির শুরুতে পৃথিবীতে পানির পরিমাণ বেশি থাকার ফলেই ভগবান মাছের অবতার হয়েছিলেন। পরে স্থলের উদ্ভব হলে কাছিম রূপে আবির্ভূত হন। যে জল-স্থল, উভয় স্থানেই বিচরণ করতে পারে। বিবর্তনতত্ত্বেও সকল প্রাণীর আদি হলো এক প্রকার মাছ। তারপর উভচর। এ কারণেই অনেকে ধারণা করেন, ডারউইন হয়তো তার গবেষণায় আর্যদের পুরাণের ছায়া অবলম্বন করেছেন।
মূলত আদি জলজ প্রাণী দুটি শাখায় বিবর্তিত হয়েছে। একটি হলো আজকের সাধারণ মাছ, আরেকটি ফুসফুসযুক্ত ঢিপিওয়ালা মাছ তথা ‘লোব ফিনড ফিশ’। এই লোবগুলোই বিবর্তিত হয়ে উন্নত প্রাণীর হাত, পা ও ডানা তৈরি হয়েছে বলে বিবর্তনবাদী বিজ্ঞানীদের অভিমত। কোয়েলাকান্থ একটি আদিম লোব ফিনড ফিশ। এ কারণেই বিজ্ঞানীদের কাছে সেটির এত কদর। ১৯৩৮ সালে প্রথম যেই কোয়েলাকান্থ পাওয়া যায়, বিজ্ঞানীরা সেটির নাম দেন ‘লাতিমারিয়া সালুম্নে’। ১৯৫২ সালেরটির নাম ‘ম্যালেনিয়া আঁজুয়ানে’। বিবর্তনের রেখা ধরে পিছু হাঁটলে হয়তো দেখা যাবে আজকের মানুষ, পাখি কিংবা বাঘ- সবারই আদি জীব ওই কোয়েলাকান্থ, যা বিশেষ এক প্রকার মাছ মাত্র। শুধু যে বিবর্তনবাদেই এসব ফিরিস্তি আছে, তা নয়। ভারতীয় আর্যদের পৌরাণিক মতে, ভগবান প্রথমে ‘মৎস্য’ অবতার হন, তারপর ‘কূর্ম’, এরপর ‘বরাহ’, পরে ‘নৃসিংহ’। মানে, ভগবান প্রথমে মাছ, তারপর কচ্ছপ, তৃতীয়তে শূকর এবং চতুর্থে নৃসিংহ। সৃষ্টির শুরুতে পৃথিবীতে পানির পরিমাণ বেশি থাকার ফলেই ভগবান মাছের অবতার হয়েছিলেন। পরে স্থলের উদ্ভব হলে কাছিম রূপে আবির্ভূত হন। যে জল-স্থল, উভয় স্থানেই বিচরণ করতে পারে। বিবর্তনতত্ত্বেও সকল প্রাণীর আদি হলো এক প্রকার মাছ। তারপর উভচর। এ কারণেই অনেকে ধারণা করেন, ডারউইন হয়তো তার গবেষণায় আর্যদের পুরাণের ছায়া অবলম্বন করেছেন।
দুই
সভ্যতায় পৌঁছাতে যা কিছু ধাপ হিসেবে বিবেচিত, মাছ সেগুলোর একটি। আদিম সমাজকে নিম্ন, মধ্য ও উচ্চ- এই তিনটি পর্যায়ে ভাগ করেন বিজ্ঞানীরা। আহার্য হিসেবে মাছকে গ্রহণের মাধ্যমে মানুষ ‘নিম্ন পর্যায়ের আদিম’ দশা থেকে উত্তীর্ণ হয়ে ‘মধ্য পর্যায়ের আদিম’ স্তরে উন্নীত হয়। তীর-ধনুক আবিষ্কারের আগ পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছে এই ধাপ। ধারণা করা হয়, আগুন আবিষ্কারের পরপরই মানুষ ভোজ্য হিসেবে মাছ খাওয়া শুরু করে। তাই মাছ ও আগুন- এ দুটির একটিকে অপরটির পরিপূরক ভাবেন তাত্ত্বিকেরা। কেননা, আগুনে ঝলসানোর মাধ্যমেই মাছ মানুষের জন্য পুষ্টিকর খাদ্য হয়ে ওঠে। এটি খেতে শেখার মধ্য দিয়েই মানুষের হাতে পানি, বাতাস ও স্থানের নিয়ন্ত্রণ আসে। ধারণা করা হয়, মাছের খোঁজে নদী ও সাগরের তীর ধরে এগোতে এগোতে মানুষেরা ছড়িয়ে পড়েছিল পুরো পৃথিবীতে।
তিন
 বাঙালি কবে থেকে মাছ খাওয়া শুরু করেছিল, তা অজানা। কিছু প্রস্তরখন্ডে সেটি খাওয়ার প্রাচীনতা বিষয়ে আঁচ করা যায়। যেমন চন্দ্রকেতুগড়ে মাছের ছবি আঁকা একটি ফলক পাওয়া গেছে। তা চতুর্থ শতকের। অষ্টম শতাব্দীর ময়নামতি ও পাহাড়পুরে পোড়ামাটির ফলকেও প্রাণীটির ছবি মেলে। তাতে মাছ কোটা ও ঝুড়িতে নিয়ে বহন করার চিত্রও আছে। তবে ভারতবর্ষের সব মানুষই যে মাছ পছন্দ করত, তা নয়। সেকালে নিন্দুকের কমতি ছিল না। এমনকি এখন পর্যন্ত অনেকে মাছ ছোঁয় না। আর্যসভ্যতা ও সংস্কৃতি কখনোই বাঙালির মৎস্যপ্রীতিকে ভালো চোখে দেখেনি। এই অঞ্চলের ধর্মভীরু ব্রাহ্মণেরা প্রাণীটি খেত না বলে জানা যায়। তবে এ বর্ণের কেউ কেউ বাছবিচার মেনে খেতে পারত। ব্রাহ্মণদের জন্য সব ধরনের মাছ খাওয়ার অনুমোদন ছিল না। যেসব মাছ কাদার গর্তে বাস করে, যেগুলোর মুখ দেখতে সাপের মতো এবং যেটির আঁশ নেই, সেগুলো খাওয়া বারণ ছিল। পচা ও শুকনা মাছও নিষেধ ছিল তাদের জন্য। তবে অব্রাহ্মণসমাজে মৎস্যপ্রীতি ছিল চরমে। প্রাচীনে ধর্মভীরু বৌদ্ধদের জলজ এই প্রাণী খাওয়া নিষেধ ছিল। খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ-পঞ্চম অব্দ থেকে ব্রাহ্মণ্যধর্মে খাওয়ার জন্য প্রাণী হত্যার ওপর নৈতিক আপত্তি দানা বেঁধেছিল। আর্য-ব্রাহ্মণ্য সমাজ নিরামিষ খাদ্যের দিকে ঝুঁকেছিল। ‘মাছে-ভাতে বাঙালি’ বিষয়টার নিন্দুক গজিয়েছিল এখানে-সেখানে। যেমন ‘সর্বানন্দ’ শুঁটকিকে নিম্নবর্গের মানুষের প্রিয় খাবার বলেছেন। বাঙালদের বলেছেন ‘শুঁটকি খেকো বচ্চার’। তবে মাছ খাওয়ার উল্লিখিত বারণগুলো হটিয়ে দিতে একাদশ শতাব্দীতে ভবদেব ভট্ট অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়েছেন। প্রমাণের চেষ্টা করেছেন জলজ এই প্রাণী খাওয়ার উপকারিতা। তৎকালে অনেক যুক্তি খাড়া করেছিলেন তিনি। মনু-যাজ্ঞবল্ক্য-ব্যাস, ছাগলেয় প্রভৃতি স্মৃতিকারদের মতামত উদ্ধার করে ভবদেব অভিমত দিয়েছেন, মাছ খাওয়ার নিষেধাজ্ঞা শুধু চতুর্দশী কিংবা এই ধরনের কিছু তিথির জন্য। অন্য সময় তা খাওয়া দোষের কিছু না। বাংলার অন্যতম স্মৃতিকার শ্রীনাথাচার্যও তা করেছেন। বিষ্ণুপুরাণ থেকে দুটি শ্লোক তুলে এনে দেখিয়েছেন যে কয়েকটি দিবস ছাড়া মাছ খাওয়া কোনো গর্হিত কাজ নয়। তা ছাড়া বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণেও এই প্রাণীর গুণকীর্তন আছে। বলা হয়েছে, রুই, পুঁটি, শোল ও সাদা আঁশওয়ালা মাছ ব্রাহ্মণেরাও খেতে পারবে। মাছের প্রশংসা করেছেন জীমূতবাহনও। ইলিশ ও এর তেলের স্তুতি লিখেছেন তিনি। বঙ্গদেশে যেসব মোগল কর্মকর্তা ছিলেন, তাদের অনেকেই মাছ-ভাতকে ঘৃণা করতেন। তবে স¤্রাট জাহাঙ্গীর মাছ পছন্দ করতেন; বিশেষ করে রুই। তার আত্মজীবনী থেকে জানা যায়, মালব থেকে গুজরাটে যাওয়ার পথে সর্দার রায়সান তাকে একটি বড় রুই দেন। তা পেয়ে তিনি এতই খুশি হয়েছিলেন যে সর্দারকে একটি ভালো ঘোড়া উপহার দিয়েছিলেন।
বাঙালি কবে থেকে মাছ খাওয়া শুরু করেছিল, তা অজানা। কিছু প্রস্তরখন্ডে সেটি খাওয়ার প্রাচীনতা বিষয়ে আঁচ করা যায়। যেমন চন্দ্রকেতুগড়ে মাছের ছবি আঁকা একটি ফলক পাওয়া গেছে। তা চতুর্থ শতকের। অষ্টম শতাব্দীর ময়নামতি ও পাহাড়পুরে পোড়ামাটির ফলকেও প্রাণীটির ছবি মেলে। তাতে মাছ কোটা ও ঝুড়িতে নিয়ে বহন করার চিত্রও আছে। তবে ভারতবর্ষের সব মানুষই যে মাছ পছন্দ করত, তা নয়। সেকালে নিন্দুকের কমতি ছিল না। এমনকি এখন পর্যন্ত অনেকে মাছ ছোঁয় না। আর্যসভ্যতা ও সংস্কৃতি কখনোই বাঙালির মৎস্যপ্রীতিকে ভালো চোখে দেখেনি। এই অঞ্চলের ধর্মভীরু ব্রাহ্মণেরা প্রাণীটি খেত না বলে জানা যায়। তবে এ বর্ণের কেউ কেউ বাছবিচার মেনে খেতে পারত। ব্রাহ্মণদের জন্য সব ধরনের মাছ খাওয়ার অনুমোদন ছিল না। যেসব মাছ কাদার গর্তে বাস করে, যেগুলোর মুখ দেখতে সাপের মতো এবং যেটির আঁশ নেই, সেগুলো খাওয়া বারণ ছিল। পচা ও শুকনা মাছও নিষেধ ছিল তাদের জন্য। তবে অব্রাহ্মণসমাজে মৎস্যপ্রীতি ছিল চরমে। প্রাচীনে ধর্মভীরু বৌদ্ধদের জলজ এই প্রাণী খাওয়া নিষেধ ছিল। খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ-পঞ্চম অব্দ থেকে ব্রাহ্মণ্যধর্মে খাওয়ার জন্য প্রাণী হত্যার ওপর নৈতিক আপত্তি দানা বেঁধেছিল। আর্য-ব্রাহ্মণ্য সমাজ নিরামিষ খাদ্যের দিকে ঝুঁকেছিল। ‘মাছে-ভাতে বাঙালি’ বিষয়টার নিন্দুক গজিয়েছিল এখানে-সেখানে। যেমন ‘সর্বানন্দ’ শুঁটকিকে নিম্নবর্গের মানুষের প্রিয় খাবার বলেছেন। বাঙালদের বলেছেন ‘শুঁটকি খেকো বচ্চার’। তবে মাছ খাওয়ার উল্লিখিত বারণগুলো হটিয়ে দিতে একাদশ শতাব্দীতে ভবদেব ভট্ট অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়েছেন। প্রমাণের চেষ্টা করেছেন জলজ এই প্রাণী খাওয়ার উপকারিতা। তৎকালে অনেক যুক্তি খাড়া করেছিলেন তিনি। মনু-যাজ্ঞবল্ক্য-ব্যাস, ছাগলেয় প্রভৃতি স্মৃতিকারদের মতামত উদ্ধার করে ভবদেব অভিমত দিয়েছেন, মাছ খাওয়ার নিষেধাজ্ঞা শুধু চতুর্দশী কিংবা এই ধরনের কিছু তিথির জন্য। অন্য সময় তা খাওয়া দোষের কিছু না। বাংলার অন্যতম স্মৃতিকার শ্রীনাথাচার্যও তা করেছেন। বিষ্ণুপুরাণ থেকে দুটি শ্লোক তুলে এনে দেখিয়েছেন যে কয়েকটি দিবস ছাড়া মাছ খাওয়া কোনো গর্হিত কাজ নয়। তা ছাড়া বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণেও এই প্রাণীর গুণকীর্তন আছে। বলা হয়েছে, রুই, পুঁটি, শোল ও সাদা আঁশওয়ালা মাছ ব্রাহ্মণেরাও খেতে পারবে। মাছের প্রশংসা করেছেন জীমূতবাহনও। ইলিশ ও এর তেলের স্তুতি লিখেছেন তিনি। বঙ্গদেশে যেসব মোগল কর্মকর্তা ছিলেন, তাদের অনেকেই মাছ-ভাতকে ঘৃণা করতেন। তবে স¤্রাট জাহাঙ্গীর মাছ পছন্দ করতেন; বিশেষ করে রুই। তার আত্মজীবনী থেকে জানা যায়, মালব থেকে গুজরাটে যাওয়ার পথে সর্দার রায়সান তাকে একটি বড় রুই দেন। তা পেয়ে তিনি এতই খুশি হয়েছিলেন যে সর্দারকে একটি ভালো ঘোড়া উপহার দিয়েছিলেন।
চার
 প্রাকৃতপৈঙ্গলে মাছ খাওয়ার রীতির প্রশংসা করা হয়েছে। তা খাবারের সহপদ হিসেবে মৌরলার ঝোল পরিবেশনকারী নারীর স্বামীকে পুণ্যবান বলেছে। চর্যাপদেও আছে মাছ ধরার বর্ণনা। সেটিতে উত্তাল মাঝনদীতে জাল ফেলে এই প্রাণী শিকারের বর্ণনা করেছেন কাহ্নপাদ। মধ্যযুগের সাহিত্যেও প্রাণীটির উল্লেখ মেলে। পদ্মপুরাণ, মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, ভারতচন্দ্র ও ঈশ্বর গুপ্তের রচনায়ও সে রকম বিবরণ আছে। সেকালের সাহিত্য থেকে বহুলভোজ্য মাছের নামের পাশাপাশি সেগুলোর রন্ধনপদ্ধতি সম্পর্কেও জানা যায়। মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলে শর্ষের তেলে চিতল মাছ ভাজা, কুমড়ার বড়ি দিয়ে রুইয়ের ঝোল, আদার রস ও শর্ষের তেলে কই মাছ ভাজা, কাতলের ঝোল, খরশোলা মাছ ভাজা, কাঁটা বের করা শোল দিয়ে আমের পদের রেসিপিও মেলে। বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গলে রুই দিয়ে কলতার আগা, মাগুর মাছ দিয়ে গিমা গাছ, শর্ষের তেলে খরসুন মাছ, চিংড়ির মাথার ভেতরে মরিচের গুঁড়া দিয়ে বিশেষ এক পদ এবং কই মাছ দিয়ে মরিচের ঝোল রান্নার উল্লেখ আছে।
প্রাকৃতপৈঙ্গলে মাছ খাওয়ার রীতির প্রশংসা করা হয়েছে। তা খাবারের সহপদ হিসেবে মৌরলার ঝোল পরিবেশনকারী নারীর স্বামীকে পুণ্যবান বলেছে। চর্যাপদেও আছে মাছ ধরার বর্ণনা। সেটিতে উত্তাল মাঝনদীতে জাল ফেলে এই প্রাণী শিকারের বর্ণনা করেছেন কাহ্নপাদ। মধ্যযুগের সাহিত্যেও প্রাণীটির উল্লেখ মেলে। পদ্মপুরাণ, মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, ভারতচন্দ্র ও ঈশ্বর গুপ্তের রচনায়ও সে রকম বিবরণ আছে। সেকালের সাহিত্য থেকে বহুলভোজ্য মাছের নামের পাশাপাশি সেগুলোর রন্ধনপদ্ধতি সম্পর্কেও জানা যায়। মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলে শর্ষের তেলে চিতল মাছ ভাজা, কুমড়ার বড়ি দিয়ে রুইয়ের ঝোল, আদার রস ও শর্ষের তেলে কই মাছ ভাজা, কাতলের ঝোল, খরশোলা মাছ ভাজা, কাঁটা বের করা শোল দিয়ে আমের পদের রেসিপিও মেলে। বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গলে রুই দিয়ে কলতার আগা, মাগুর মাছ দিয়ে গিমা গাছ, শর্ষের তেলে খরসুন মাছ, চিংড়ির মাথার ভেতরে মরিচের গুঁড়া দিয়ে বিশেষ এক পদ এবং কই মাছ দিয়ে মরিচের ঝোল রান্নার উল্লেখ আছে।
বাংলা সাহিত্যের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে আছে মাছ। প্রবেশ করেছে লোককথা, বাগধারা ও বচনে। কই মাছের প্রাণ, ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানে না, ঝাঁকের কই, মাছের মায়ের পুত্রশোক, গভীর জলের মাছ, রাঘব-বোয়াল, রুই-কাতলা, ধরি মাছ না ছুঁই পানি, চুনোপুঁটি, পুঁটি মাছের প্রাণ, মাছের তেলে মাছ ভাজা- এমন আরও উদাহরণ আছে। খনার বচনে পাওয়া যায়: মাছের রাজা রুই, শাকের রাজা পুঁই; লাউগাছে মাছের জল, ধেনো মাটিতে ঝাল প্রবল ইত্যাদি।
পাঁচ
 বাঙালির আমোদ-প্রমোদেও মাছের উপস্থিতি ব্যাপক। বিশেষ করে বিয়েতে। মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে জলজ এই প্রাণী খুবই আবশ্যিক অনুষঙ্গ। জাদুবিশ্বাস থেকে মাছের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে নারীর উর্বরতা শক্তির সম্পর্ক। এই প্রাণীর ডিম থেকে অসংখ্য পোনা জন্মায়। মানে, মাছের রয়েছে অধিক সন্তান উৎপাদনের ক্ষমতা। একসময় সন্তান জন্মদানই ছিল বিয়ে হওয়ার একমাত্র কারণ। নারীর উদরে মাছের উর্বরতা সঞ্চারের জন্যই বিয়েশাদিতে এই প্রাণীর উপস্থিতির চল। বাংলা সংস্কৃতিতে মঙ্গলাচরণের দিন বরপক্ষ আঁশযুক্ত মাছ নিয়ে কনের বাড়িতে উপস্থিত হয়। তাতে সিঁদুরের পাঁচটি ফোঁটা দেয় কনেপক্ষের লোকেরা। বাংলাদেশের কিছু অঞ্চলে এখনো বিয়েশাদিতে বিশেষ কয়েকটি মাছ খাওয়ানোর সংস্কৃতি আছে। যেমন চট্টগ্রামে রূপচাঁদা এবং খুলনায় বরযাত্রীদের চিংড়ি খাওয়ানোর চল। বাঙালি মুসলমান বিয়েতে মাছের উপস্থিতি খুব একটা না থাকলেও গায়ে-হলুদে কনের বাড়িতে এটি পাঠানোর প্রথা পালিত হয়। দেখা যায় একটি মাছকে নথ পরিয়ে লাল কাপড়ে মুড়ে কনে সাজাতে। বিয়ের পর জামাই শ্বশুরালয়ে গিয়ে বাজার থেকে বড় মাছ কিনে আনে। বউ সেটি কেটে সংসার জীবনের সূত্রপাত ঘটায়। দুই শতক আগেও বাঙালি বিয়েতে মাছের বাড়াবাড়ি রকমের উপস্থিতি ছিল। লেখক শরৎকুমারী চৌধুরাণী তৎকালীন বনেদি পরিবারের বিয়ে উৎসবের যে ভোজনের বর্ণনা করেছেন, সেখানেই প্রমাণ মেলে। তাতে চিংড়ির মালাইকারি, মাছ দিয়ে ছোলার ডাল, রুইয়ের মাথা দিয়ে মুগ ডাল, মাছের চপ, চিংড়ির কাটলেট, ইলিশ ভাজা ইত্যাদি পদের উল্লেখ আছে।
বাঙালির আমোদ-প্রমোদেও মাছের উপস্থিতি ব্যাপক। বিশেষ করে বিয়েতে। মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে জলজ এই প্রাণী খুবই আবশ্যিক অনুষঙ্গ। জাদুবিশ্বাস থেকে মাছের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে নারীর উর্বরতা শক্তির সম্পর্ক। এই প্রাণীর ডিম থেকে অসংখ্য পোনা জন্মায়। মানে, মাছের রয়েছে অধিক সন্তান উৎপাদনের ক্ষমতা। একসময় সন্তান জন্মদানই ছিল বিয়ে হওয়ার একমাত্র কারণ। নারীর উদরে মাছের উর্বরতা সঞ্চারের জন্যই বিয়েশাদিতে এই প্রাণীর উপস্থিতির চল। বাংলা সংস্কৃতিতে মঙ্গলাচরণের দিন বরপক্ষ আঁশযুক্ত মাছ নিয়ে কনের বাড়িতে উপস্থিত হয়। তাতে সিঁদুরের পাঁচটি ফোঁটা দেয় কনেপক্ষের লোকেরা। বাংলাদেশের কিছু অঞ্চলে এখনো বিয়েশাদিতে বিশেষ কয়েকটি মাছ খাওয়ানোর সংস্কৃতি আছে। যেমন চট্টগ্রামে রূপচাঁদা এবং খুলনায় বরযাত্রীদের চিংড়ি খাওয়ানোর চল। বাঙালি মুসলমান বিয়েতে মাছের উপস্থিতি খুব একটা না থাকলেও গায়ে-হলুদে কনের বাড়িতে এটি পাঠানোর প্রথা পালিত হয়। দেখা যায় একটি মাছকে নথ পরিয়ে লাল কাপড়ে মুড়ে কনে সাজাতে। বিয়ের পর জামাই শ্বশুরালয়ে গিয়ে বাজার থেকে বড় মাছ কিনে আনে। বউ সেটি কেটে সংসার জীবনের সূত্রপাত ঘটায়। দুই শতক আগেও বাঙালি বিয়েতে মাছের বাড়াবাড়ি রকমের উপস্থিতি ছিল। লেখক শরৎকুমারী চৌধুরাণী তৎকালীন বনেদি পরিবারের বিয়ে উৎসবের যে ভোজনের বর্ণনা করেছেন, সেখানেই প্রমাণ মেলে। তাতে চিংড়ির মালাইকারি, মাছ দিয়ে ছোলার ডাল, রুইয়ের মাথা দিয়ে মুগ ডাল, মাছের চপ, চিংড়ির কাটলেট, ইলিশ ভাজা ইত্যাদি পদের উল্লেখ আছে।
ছয়
 মাছ নিয়ে মিথও আছে অনেক। বগুড়ায় মহাস্থানগড়ের অদূরে শাহ সুলতান মাহমুদ বলখীর মাজার। লোকমুখে প্রচলিত আছে, তিনি বরেন্দ্রভূমিতে এসেছিলেন মাছের পিঠে চেপে। সিলেটে আছে হজরত শাহজালালের মাজার। সেখানকার একটি পুকুরে আছে গজার মাছ। ভক্তরা সেগুলোকে কদর করে। মহাভারতের রচয়িতা বেদব্যাসের মা সত্যবতী জন্মেছিলেন মাছের গর্ভে। তার গায়ে ছিল মাছের তীব্র গন্ধ। তাই তার আরেক নাম মৎস্যগন্ধা। তা ছাড়া সত্যবতী ও তার যমজ ভাইকে মাছের পেটেই পেয়েছিলেন ধীবরদের রাজা। অর্জুনকে দ্রৌপদীর স্বয়ংবরে তীর বিদ্ধ করতে হয়েছিল মাছের চোখে। ধর্মশাস্ত্রে উল্লেখ আছে, নবী ইউনূসকে যখন মাঝনদীতে ফেলে দেওয়া হয়, তখন তাকে একটি তিমি গিলে নেয়। পরে প্রাণীটি তাকে নদীর তীরে এনে উগরে দেয়। ফলে তিনি পেট থেকে বেরিয়ে আসেন।
মাছ নিয়ে মিথও আছে অনেক। বগুড়ায় মহাস্থানগড়ের অদূরে শাহ সুলতান মাহমুদ বলখীর মাজার। লোকমুখে প্রচলিত আছে, তিনি বরেন্দ্রভূমিতে এসেছিলেন মাছের পিঠে চেপে। সিলেটে আছে হজরত শাহজালালের মাজার। সেখানকার একটি পুকুরে আছে গজার মাছ। ভক্তরা সেগুলোকে কদর করে। মহাভারতের রচয়িতা বেদব্যাসের মা সত্যবতী জন্মেছিলেন মাছের গর্ভে। তার গায়ে ছিল মাছের তীব্র গন্ধ। তাই তার আরেক নাম মৎস্যগন্ধা। তা ছাড়া সত্যবতী ও তার যমজ ভাইকে মাছের পেটেই পেয়েছিলেন ধীবরদের রাজা। অর্জুনকে দ্রৌপদীর স্বয়ংবরে তীর বিদ্ধ করতে হয়েছিল মাছের চোখে। ধর্মশাস্ত্রে উল্লেখ আছে, নবী ইউনূসকে যখন মাঝনদীতে ফেলে দেওয়া হয়, তখন তাকে একটি তিমি গিলে নেয়। পরে প্রাণীটি তাকে নদীর তীরে এনে উগরে দেয়। ফলে তিনি পেট থেকে বেরিয়ে আসেন।
সাত
 পৃথিবীর সবচেয়ে দামি খাবার ক্যাভিয়ার। এটিও আসে মাছ থেকে। তা মূলত স্টারজিওন নামের একধরনের সামুদ্রিক মাছের ডিম। যেগুলোর প্রতি পাউন্ডের দাম ৪০ হাজার মার্কিন ডলার পর্যন্ত হতে পারে। এত উচ্চমূল্যের কারণ হলো ক্রেতাদের বিপুল চাহিদা এবং স্টারজিওন মাছের অপ্রতুলতা। ইউরোপের দেশগুলোতে ক্যাভিয়ার দৈনন্দিন একটি খাবার। এতে সামান্য লবণ মিশিয়ে কাঁচা অবস্থাতেই পরিবেশন করা হয়। চাটনি দিয়ে খাওয়ার চল। তবে পরিবেশন করতে হয় সোনার বাক্সে ভরে। কুকিজাতীয় বিস্কুটের ওপর ক্যাভিয়ার রেখে খেতে পছন্দ করেন অনেকে। কেউ কেউ হুইস্কি বা ভদকার সঙ্গে মিশিয়ে খায়। ক্যাভিয়ার মূলত কালো, ধূসর, বাদামি, হালকা হলুদ, গাঢ় হলুদ, কমলা ইত্যাদি রঙের হয়। বিশ্বের ৯০ শতাংশ ক্যাভিয়ার মেলে কাস্পিয়ান উপসাগরে। সেখানে বেশি বেশি স্টারজিওন মাছ পাওয়া যায়। একটি পূর্ণাঙ্গ মাছের মোট ওজনের ১২ শতাংশ ডিম থাকে। ডিম পাড়ে শীতকালে। পেট কেটে তা সংগ্রহ করতে হয়। কেননা, যে ডিম প্রাকৃতিকভাবেই বেরিয়ে আসে, তা খাওয়ার উপযোগী নয়।
পৃথিবীর সবচেয়ে দামি খাবার ক্যাভিয়ার। এটিও আসে মাছ থেকে। তা মূলত স্টারজিওন নামের একধরনের সামুদ্রিক মাছের ডিম। যেগুলোর প্রতি পাউন্ডের দাম ৪০ হাজার মার্কিন ডলার পর্যন্ত হতে পারে। এত উচ্চমূল্যের কারণ হলো ক্রেতাদের বিপুল চাহিদা এবং স্টারজিওন মাছের অপ্রতুলতা। ইউরোপের দেশগুলোতে ক্যাভিয়ার দৈনন্দিন একটি খাবার। এতে সামান্য লবণ মিশিয়ে কাঁচা অবস্থাতেই পরিবেশন করা হয়। চাটনি দিয়ে খাওয়ার চল। তবে পরিবেশন করতে হয় সোনার বাক্সে ভরে। কুকিজাতীয় বিস্কুটের ওপর ক্যাভিয়ার রেখে খেতে পছন্দ করেন অনেকে। কেউ কেউ হুইস্কি বা ভদকার সঙ্গে মিশিয়ে খায়। ক্যাভিয়ার মূলত কালো, ধূসর, বাদামি, হালকা হলুদ, গাঢ় হলুদ, কমলা ইত্যাদি রঙের হয়। বিশ্বের ৯০ শতাংশ ক্যাভিয়ার মেলে কাস্পিয়ান উপসাগরে। সেখানে বেশি বেশি স্টারজিওন মাছ পাওয়া যায়। একটি পূর্ণাঙ্গ মাছের মোট ওজনের ১২ শতাংশ ডিম থাকে। ডিম পাড়ে শীতকালে। পেট কেটে তা সংগ্রহ করতে হয়। কেননা, যে ডিম প্রাকৃতিকভাবেই বেরিয়ে আসে, তা খাওয়ার উপযোগী নয়।
আট
মাছকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে চিত্রকলাও। যেমন ফিশআর্ট ‘গিয়োতাকু’। প্রাচীন জাপানের চিত্রাঙ্কনের একটি ধরন। এই পদ্ধতিতে শুধু মাছের ছবিই আঁকা হয়। প্রাচীনকালে এই আর্টের উদ্ভব হয়েছিল জেলেদের হাতে। কিন্তু তা আবিষ্কৃত হয় ১৮০০ সালে। প্রাচীন জাপানের জেলেরা ধৃত মাছের আকার-আকৃতি সংরক্ষণের জন্য প্রাণীটির গায়ের এক পাশে ‘সুমি-ই’ নামের কালির প্রলেপ দিয়ে ‘রাইস’ নামের কাগজে ছাপ নিত। এই কাজ করার কারণ হচ্ছে, জাপানিরা কিছু মাছকে সমীহ করে। জালে আটকালে প্রাচীন জেলেরা সেগুলোর ছাপ রেখে আবার পানিতে ফেরত পাঠাত। ছাপ রাখার কারণ ছিল ডাঙায় এসে ধৃত মাছের গল্প বলা। কেউ প্রমাণ চাইলে ছাপ দেখিয়ে দেওয়া। তা ছাড়া কৌতূহলীদের স্পৃহাও মেটাত সেসব ছাপচিত্র। এ উদ্দেশ্যে কালি, ব্রাশ ও কাগজ নিয়েই মাছ শিকারে বেরোত জাপানি জেলেরা। ‘এডো’ পিরিয়ডে এই গিয়োতাকু আর্ট বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। তৎকালীন অভিজাত বংশীয় ব্যক্তি লর্ড সাকাই গিয়োতাকুর মাধ্যমে ধৃত মাছের ছবি আঁকাতেন। এ জন্য আঁকিয়ে ভাড়া করতেন তিনি। বর্তমানে গিয়োতাকু জাপানের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি। আর্টের এ ধারা দেশটি থেকে ছড়িয়ে পড়েছে বিশ্বব্যাপী। তা ছাড়া কানাডার রেড ডিয়ার কলেজে ‘মিক্সিং বিডেস এবং ফিশ স্কেল আর্ট’ নামে একটি কোর্স আছে। সেখানে ‘ফিশ স্কেল আর্ট’কে শিল্প হিসেবে গণ্য করা হয়।
নয়
 রূপচর্চায়ও আছে মাছের ব্যবহার। ২০১৫ সালে রাশিয়ার মেকআপ আর্টিস্ট এলিয়া বুলোচকা রূপসজ্জায় অ্যাঞ্জেল ও নিওন মাছ ব্যবহার করেন। তা ছাড়া লিপস্টিক ও নেইলপলিশ তৈরিতে লাগে মাছের আঁশ। তাতে থাকে গুয়ানিন যৌগ, যা প্রসাধনীর উজ্জ্বলভাব ও স্থায়িত্ব বজায় রাখে। কিছু মেকআপ ও ব্লাশ তৈরিতেও ব্যবহৃত হয় আঁশ। পোশাক তৈরিতে প্রাণীটির চামড়া এবং বিশেষ এক প্রকার মাছের নিঃসৃত লালাজাতীয় পদার্থ ব্যবহৃত হয়। যেমন মহাসাগরীয় মাছ হ্যাগফিশ। এটি একধরনের স্লাইম নিঃসরণ করে; যা ঘন ও আঠালো। তা থেকে পোশাক তৈরির সম্ভাবনা খুঁজে পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা। নিঃসৃত স্লাইম স্বচ্ছ, নমনীয় ও শক্তিশালী। এটি লম্বা করে টেনে শুকালে রেশমের কাপড়ের মতো হয়। কানাডার উইলফ বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন বিজ্ঞানী তা নিয়ে গবেষণা করে প্রোটিন সমৃদ্ধ শক্ত সুতা তৈরি করতে সক্ষম হয়েছেন। তা ছাড়া হেইলংজিয়াংয়ের তৎজিয়াং শহরের হ্যাজেন সম্প্রদায়ের মানুষেরা মাছের চামড়া দিয়ে পোশাক তৈরি করেন। সুগন্ধি তৈরিতে ব্যবহৃত হয় তিমির বমি। প্রাণীটির ক্ষুদ্রান্তে উৎপন্ন হয় ‘অ্যামবারগ্রিস’। সেটিকেই স্থানীয়রা বমি বলে। তা থেকে প্রথমে আঁশটে গন্ধ বেরোলেও পরে খুবই সুগন্ধ ছড়ায়। পদার্থটি এতই মোহময় যে বিশ্বের বিখ্যাত সুগন্ধি প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠানের সবচেয়ে দামি পারফিউমগুলো তৈরিতে তা ব্যবহৃত হয়। অলংকার তৈরিতেও মাছের ব্যবহার আছে। যেমন থাইল্যান্ডের ফুকেট সিটিতে মাছের আঁশ দিয়ে বিভিন্ন সজ্জার উপকরণ ও সামগ্রী তৈরি হয়। আরও যেসব সামগ্রী বানায় সেগুলো হলো: মাছের আঁশের ফুলদানি, ডোর বেল, গলার অলংকার হার, নেকলেস, দুল, আংটি, ব্রেসলেট, কৃত্রিম নখ, চুলের ফিতা ও আংটা, ঘর সাজানো বল, মানিব্যাগ ইত্যাদি।
রূপচর্চায়ও আছে মাছের ব্যবহার। ২০১৫ সালে রাশিয়ার মেকআপ আর্টিস্ট এলিয়া বুলোচকা রূপসজ্জায় অ্যাঞ্জেল ও নিওন মাছ ব্যবহার করেন। তা ছাড়া লিপস্টিক ও নেইলপলিশ তৈরিতে লাগে মাছের আঁশ। তাতে থাকে গুয়ানিন যৌগ, যা প্রসাধনীর উজ্জ্বলভাব ও স্থায়িত্ব বজায় রাখে। কিছু মেকআপ ও ব্লাশ তৈরিতেও ব্যবহৃত হয় আঁশ। পোশাক তৈরিতে প্রাণীটির চামড়া এবং বিশেষ এক প্রকার মাছের নিঃসৃত লালাজাতীয় পদার্থ ব্যবহৃত হয়। যেমন মহাসাগরীয় মাছ হ্যাগফিশ। এটি একধরনের স্লাইম নিঃসরণ করে; যা ঘন ও আঠালো। তা থেকে পোশাক তৈরির সম্ভাবনা খুঁজে পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা। নিঃসৃত স্লাইম স্বচ্ছ, নমনীয় ও শক্তিশালী। এটি লম্বা করে টেনে শুকালে রেশমের কাপড়ের মতো হয়। কানাডার উইলফ বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন বিজ্ঞানী তা নিয়ে গবেষণা করে প্রোটিন সমৃদ্ধ শক্ত সুতা তৈরি করতে সক্ষম হয়েছেন। তা ছাড়া হেইলংজিয়াংয়ের তৎজিয়াং শহরের হ্যাজেন সম্প্রদায়ের মানুষেরা মাছের চামড়া দিয়ে পোশাক তৈরি করেন। সুগন্ধি তৈরিতে ব্যবহৃত হয় তিমির বমি। প্রাণীটির ক্ষুদ্রান্তে উৎপন্ন হয় ‘অ্যামবারগ্রিস’। সেটিকেই স্থানীয়রা বমি বলে। তা থেকে প্রথমে আঁশটে গন্ধ বেরোলেও পরে খুবই সুগন্ধ ছড়ায়। পদার্থটি এতই মোহময় যে বিশ্বের বিখ্যাত সুগন্ধি প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠানের সবচেয়ে দামি পারফিউমগুলো তৈরিতে তা ব্যবহৃত হয়। অলংকার তৈরিতেও মাছের ব্যবহার আছে। যেমন থাইল্যান্ডের ফুকেট সিটিতে মাছের আঁশ দিয়ে বিভিন্ন সজ্জার উপকরণ ও সামগ্রী তৈরি হয়। আরও যেসব সামগ্রী বানায় সেগুলো হলো: মাছের আঁশের ফুলদানি, ডোর বেল, গলার অলংকার হার, নেকলেস, দুল, আংটি, ব্রেসলেট, কৃত্রিম নখ, চুলের ফিতা ও আংটা, ঘর সাজানো বল, মানিব্যাগ ইত্যাদি।
মাছের আছে নানামুখী ব্যবহার। একে কেন্দ্র করে অর্থনীতির একটি বৃহৎ অংশ বর্তায়। কিন্তু মানুষের উদাসীনতা ও অব্যবস্থাপনার কারণে প্রাণীটি দিন দিন কমতে শুরু করেছে। গ্রামবাংলার খালে-বিলে এখন আর আগের মতো মাছ মেলে না। এখানে গ্রাম্য বয়োবৃদ্ধদের একটি ভবিষ্যদ্বাণী উল্লেখ করা যেতে পারে। তাদের অনেকেই বলেন, এমন একদিন আসবে যেদিন মানুষ শুষ্কপ্রায় জলাশয়ের দিকে তাকিয়ে বলবে- হায়! কোনো এক সময় এই পানিতে নাকি মাছ পাওয়া যেত।
সহায়ক বই
১. ‘পৃথিবীর ইতিহাস’, লেখক: দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ও রমাকৃষ্ণ মৈত্র। প্রকাশকাল: আশ্বিন ১৩৬৩ সন।
২. ‘ভারতীয় আর্যজাতির আদিম অবস্থা’, লেখক: শ্রীলালমোহন বিদ্যানিধি ভট্টাচার্য্য। প্রকাশকাল: ১৮৯১ সাল।
৩. ‘এনসিয়েন্ট সোসাইটি’, লেখক: লুইস হেনরি মর্গান, বাংলা অনুবাদ ও সম্পাদনা: বুলবন ওসমান, অনুবাদ প্রকাশকাল: জুন, ১৯৭৫।
৪. ‘দ্য অরিজিন অব দ্য ফ্যামিলি, প্রাইভেট প্রোপার্টি অ্যান্ড দ্য স্টেট’, লেখক: ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস, বাংলা অনুবাদ: মন্মথ সরকার এম এ, অনুবাদ প্রকাশকাল: মে, ১৯৪৪।
৫. ‘হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি’, লেখক: গোলাম মুরশিদ।
ছবি: ইন্টারনেট