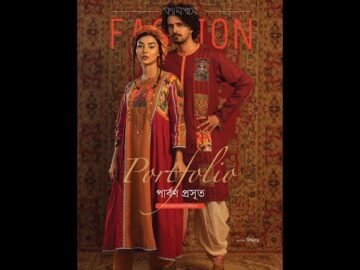বিশেষ ফিচার I আলো-ছায়ার আলোকমালা
নাসির আলী মামুন। কিংবদন্তি আলোকচিত্রশিল্পী। তার ক্যামেরায় ধরা পড়েছে অসংখ্য কীর্তিমানের মুখ। বাংলাদেশের শিল্প-ইতিহাসের তিন প্রবাদপ্রতিম চিত্রশিল্পীর বাছাই করা তিনটি প্রতিকৃতি তোলার নেপথ্য গল্প শোনাচ্ছেন তিনি
বিভিন্ন মাধ্যমে বিশিষ্ট ও সৃজনশীল মানুষদের ছবি তোলা শুরু করি ১৯৭১ সালে। মুক্তিযুদ্ধের প্রাক্কালে কিছু ছবি তুলেছিলাম সে বছরের ৩ মার্চ। এরপর টানা কয়েক দিন ছবি তুলেছি। এমনকি ৭ মার্চের ছবিও আছে আমার কাছে। সেই যে শুরু, ৫২ বছর ধরে এ কাজ করে চলেছি। বিখ্যাত মানুষ, যারা আমাদের কাছে আইকন, যাদের আরাধনা করি, মান্য করি, আমি তাদের ছবি তুলেছি এবং তুলছি।
 ছবি তোলা শুরু করেছিলাম ১৭ বছর বয়সে। তারও আগে খেয়াল করলাম, আমাদের দেশে যারা ফটোগ্রাফি করেন, তাদের মধ্যে একদল করেন সৃষ্টিশীল ফটোগ্রাফি; যেমন মনজুর আলম বেগ, আমানুল হক, নায়েব উদ্দিন আহমেদ, নওয়াজেশ আহমদ, আনোয়ার হোসেন, সাইদা খানম, গোলাম কাসেম ড্যাডি প্রমুখ। তারা ফ্রিল্যান্স কাজ করতেন; নিঃসর্গ ও প্রকৃতিভিত্তিক ফটোগ্রাফি করতেন। আরেক দল ফটোগ্রাফার বাণিজ্যিক ধারার ফটোগ্রাফি করতেন। সর্বশেষ যাদের কথা উল্লেখ করতে চাই, তারাও সৃষ্টিশীল ফটোগ্রাফার, যাদের সাংবাদিকতায় অনেক অবদান রয়েছে। সেই দলে আছেন রশীদ তালুকদার, গোলাম মাওলা, মোহাম্মদ আলম, শামসুল ইসলামের মতো বিখ্যাত আলোকচিত্রশিল্পী। বিখ্যাত ফটোগ্রাফারদের ছবি বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় দেখতাম। এ ছাড়া বিদেশের পত্রপত্রিকায় বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধান, কবি, লেখক, বুদ্ধিজীবীদের ছবি খেয়াল করে দেখতাম। জানতে চাইতাম, এসব ছবি কারা তুলেছেন, কীভাবে তুলেছেন, আর কীভাবেই তারা সেসব বিখ্যাত মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেছিলেন। ইন্টারনেট না থাকায় তখন এসব ব্যাপার চাইলেই জানা সম্ভব ছিল না। আমি কিন্তু বলছি সেই ১৯৬৩ সালের কথা, যখন আমার বয়স ছিল ১০ বছর।
ছবি তোলা শুরু করেছিলাম ১৭ বছর বয়সে। তারও আগে খেয়াল করলাম, আমাদের দেশে যারা ফটোগ্রাফি করেন, তাদের মধ্যে একদল করেন সৃষ্টিশীল ফটোগ্রাফি; যেমন মনজুর আলম বেগ, আমানুল হক, নায়েব উদ্দিন আহমেদ, নওয়াজেশ আহমদ, আনোয়ার হোসেন, সাইদা খানম, গোলাম কাসেম ড্যাডি প্রমুখ। তারা ফ্রিল্যান্স কাজ করতেন; নিঃসর্গ ও প্রকৃতিভিত্তিক ফটোগ্রাফি করতেন। আরেক দল ফটোগ্রাফার বাণিজ্যিক ধারার ফটোগ্রাফি করতেন। সর্বশেষ যাদের কথা উল্লেখ করতে চাই, তারাও সৃষ্টিশীল ফটোগ্রাফার, যাদের সাংবাদিকতায় অনেক অবদান রয়েছে। সেই দলে আছেন রশীদ তালুকদার, গোলাম মাওলা, মোহাম্মদ আলম, শামসুল ইসলামের মতো বিখ্যাত আলোকচিত্রশিল্পী। বিখ্যাত ফটোগ্রাফারদের ছবি বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় দেখতাম। এ ছাড়া বিদেশের পত্রপত্রিকায় বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধান, কবি, লেখক, বুদ্ধিজীবীদের ছবি খেয়াল করে দেখতাম। জানতে চাইতাম, এসব ছবি কারা তুলেছেন, কীভাবে তুলেছেন, আর কীভাবেই তারা সেসব বিখ্যাত মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেছিলেন। ইন্টারনেট না থাকায় তখন এসব ব্যাপার চাইলেই জানা সম্ভব ছিল না। আমি কিন্তু বলছি সেই ১৯৬৩ সালের কথা, যখন আমার বয়স ছিল ১০ বছর।
সেই সময় আমাদের বাসায় পত্রিকা রাখা হতো। বাবার পড়া হয়ে গেলে পত্রিকার ছবি কেটে জমিয়ে রাখতাম। ব্যাপারটি পরবর্তীকালে আমার বন্ধু সার্কেলে ছড়িয়ে পড়ে। সে সময় পাকিস্তান ও ঢাকাভিত্তিক বিভিন্ন পত্রিকা পড়ার চল ছিল। এসব পত্রিকায় ছাপা হওয়া বিভিন্ন ছবি দেখে আমি মুগ্ধ হয়ে পড়তাম। তখন থেকেই নতুন কিছু করার তাড়না অনুভব করতে থাকলাম। এরপরেই খ্যাতিমান ব্যক্তিদের পোর্ট্রেট তোলার আইডিয়া মাথায় আসে। তখন বিভিন্ন রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, খেলাধুলাবিষয়ক অনুষ্ঠানে যেতাম সেলিব্রিটিদের দেখার জন্য। সেই অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি বিভিন্ন ব্রশিয়ার, বই, প্রকাশনীতে ছাপা হওয়া ছবির সঙ্গে বাস্তবতার তফাত। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, মওলানা ভাসানীদের দেখতে পল্টন ময়দানে চলে যেতাম। সেই সময় আরেক বিখ্যাত রাজনীতিবিদ ছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির কমরেড নুরুল ইসলাম মুন্সী। ওনারাই ১৯৬০-৭০-এর দশকে মাঠকাঁপানো রাজনীতিবিদ ছিলেন। তারা কীভাবে স্টেজে উঠতেন, কীভাবে বক্তৃতা দিতেন, তা খেয়াল করার জন্য আমি স্টেজের সামনে চলে যেতাম। তখন আমার কাছে ক্যামেরা ছিল না। তা ছাড়া আমার মতো কম বয়সী ছেলেকে কেউ ক্যামেরা ধার দেওয়ার কথাও নয়। সেই পাগলামি এতটাই বেশি ছিল, দিনের পর দিন আমি বাসা থেকে না বলেই চলে যেতাম।
 আমি তখন থাকতাম গ্রিন রোড স্টাফ কোয়ার্টারে। বাংলা একাডেমি, ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ পরিষদ (বর্তমানে বিলুপ্ত), প্রেসক্লাবসহ নানা স্থানে সে সময় বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হতো। সেখানে গিয়ে দেখতাম, প্রেস ফটোগ্রাফাররা কীভাবে ছবি তোলেন। সেই সঙ্গে কবি, সাহিত্যিক, লেখক, গবেষক, চিন্তাবিদ, সংগীতশিল্পীরা কীভাবে তাদের কাজের বহিঃপ্রকাশ ঘটান, এসবও খেয়াল করে দেখতাম। ভাবতাম, আমি এমন ছবি তুলব, যেন তাদের হুবহু রিপ্রেজেন্টেশন হয়। ষাট-সত্তরের দশক বা তারও আগে সেলিব্রিটিরা তাদের প্রকাশনার জন্য ফটো স্টুডিওতে গিয়ে ছবি তুলতেন এবং সেই ছবিগুলো যথেষ্ট ফরমাল হতো। সেসব ছবিতে মুহূর্ত দান করা যেত না এবং একটি নির্দিষ্ট ফরমেটে ছবি তোলা হতো। আমি ছবি তোলার এ ধারা পরিবর্তন করতে চাইলাম।
আমি তখন থাকতাম গ্রিন রোড স্টাফ কোয়ার্টারে। বাংলা একাডেমি, ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ পরিষদ (বর্তমানে বিলুপ্ত), প্রেসক্লাবসহ নানা স্থানে সে সময় বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হতো। সেখানে গিয়ে দেখতাম, প্রেস ফটোগ্রাফাররা কীভাবে ছবি তোলেন। সেই সঙ্গে কবি, সাহিত্যিক, লেখক, গবেষক, চিন্তাবিদ, সংগীতশিল্পীরা কীভাবে তাদের কাজের বহিঃপ্রকাশ ঘটান, এসবও খেয়াল করে দেখতাম। ভাবতাম, আমি এমন ছবি তুলব, যেন তাদের হুবহু রিপ্রেজেন্টেশন হয়। ষাট-সত্তরের দশক বা তারও আগে সেলিব্রিটিরা তাদের প্রকাশনার জন্য ফটো স্টুডিওতে গিয়ে ছবি তুলতেন এবং সেই ছবিগুলো যথেষ্ট ফরমাল হতো। সেসব ছবিতে মুহূর্ত দান করা যেত না এবং একটি নির্দিষ্ট ফরমেটে ছবি তোলা হতো। আমি ছবি তোলার এ ধারা পরিবর্তন করতে চাইলাম।
১৯৭১ সালে থেকে ছবি তুললেও ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত আমার নিজের ক্যামেরা ছিল না। ১৯৭৮ সালে প্রথম একটি বক্স ক্যামেরা কিনি। সেই সময় বিখ্যাত ব্যক্তিদের বাসায় গিয়ে ছবি তোলা শুরু করি, যদিও বাংলাদেশে তখন বাসায় গিয়ে ছবি তোলার রেওয়াজ ছিল না। স্বাধীন বাংলাদেশে সে সময় পত্রিকা ছিল হাতে গোনা। বিভিন্ন দিবসে সেলিব্রিটিদের ছবি অহরহ ছাপা হতো না। ছাপলেও সংগ্রহ করে একটি পাসপোর্ট ছবি ছেপে দেওয়া হতো; কোনো ফটোগ্রাফারকে পাঠানো হতো না। আমি যখন কাজটা শুরু করলাম, দেখলাম, কেউ তেমন পাত্তা দিচ্ছেন না; উল্টো সন্দেহের চোখে দেখছেন। বাসা থেকে বের হওয়ার সময় অনেকেই ব্যাগ খুলে চেক করতেন। অবশ্য বয়সের বিশাল পার্থক্য থাকার পরও পরবর্তীকালে তাদের অনেকের সঙ্গে একধরনের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তারপর সবাইকে বলা শুরু করলাম, ‘আপনারা যে কষ্ট করে স্টুডিওতে যান, তাতে আপনাদের সময় ও টাকা ব্যয় হয়। তার পরিবর্তে স্টুডিও আপনার ঘরে চলে আসবে।’
বিখ্যাত মানুষদের বাসায় গিয়ে ছবি তুলে ২ থেকে ৫ দিনের মধ্যে তা আবার তাদের দিয়েও আসতাম। ফলে, আমার প্রতি তাদের আস্থা ও বিশ্বাস মুদ্রিত হতে থাকল। সেই সঙ্গে একধরনের ব্যক্তিগত সম্পর্ক গড়ে উঠতে থাকল; আর তাতে আমি উজ্জীবিত ও খুশি হলাম। কিন্তু দুই-তিন পর খেয়াল করলাম, আমি আর নতুনভাবে তালিকা করতে পারছি না, বিশেষ করে সংগীত, শিল্পকলা, সাহিত্য, ক্রীড়া, স্থাপত্য, রাজনীতিসহ বিভিন্ন সৃজনশীল ক্ষেত্রে অবদান রাখা ব্যক্তিদের তালিকা। তাই গেলাম বাংলা একাডেমিতে। এক দিন নয়; বহুদিন যাওয়ার পর পেলাম সাহিত্যিকদের তালিকা। বাংলা একাডেমির সঙ্গে একধরনের সখ্য গড়ে উঠল। সেখান থেকে তারা দিকনির্দেশনা দিল, কোথায় গেলে কী ধরনের তালিকা পাওয়া যাবে। এভাবে বিজ্ঞানীদের তালিকাও পেলাম। একে একে পরিচয় হতে থাকল অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ, জাতীয় অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাক, কবি শামসুর রাহমান, আল মাহমুদ প্রমুখের সঙ্গে। আমি ওনাদের কাছে গিয়ে তালিকা ঠিক করে নিতাম।
১৯৭৬ সালে উপলব্ধি করলাম, একটি এক্সিবিশন করা দরকার। বাংলাদেশে ল্যান্ডস্কেপ, নদী, পাখি, ফুল—এসবের ছবি নিয়ে এক্সিবিশন হয়; আমি পরিকল্পনা করলাম লেখকদের ছবি নিয়ে করার। ঝামেলা বাধল জায়গা নিয়ে। বাংলা একাডেমিতে প্রস্তাব দুই মাস নাকচ হওয়ার পর অনুমতি মিলল। নতুন ভবন—যেখানে ডিজি বসতেন, সেই ভবনের চতুর্থ তলায় এক্সিবিশন করা যাবে। ১৬-২১ ফেব্রুয়ারি হলো সেই এক্সিবিশন। প্রধান অতিথি ছিলেন রাজনীতিবিদ আকবর কবির; বিশেষ অতিথি কবি শামসুর রাহমান। দিনটি কবি শামসুর রাহমানের জন্য বিশেষ ছিল; কারণ, সেদিন তিনি দৈনিক বাংলার সম্পাদক হয়েছিলেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে কবি বলেছিলেন, ‘এ দেশে বইয়ের এক্সিবিশন ও মেলা হয়, এমনকি শাড়ি ও পোশাকের মেলাও হয়; কিন্তু লেখকদের ছবির এক্সিবিশন কখনো হয়নি। লেখকেরা সারা জীবনই বঞ্চিত!’ বাংলা একাডেমি পুরস্কারপ্রাপ্ত ৬৬ জন সাহিত্যিকের ছবি ছিল সেই এক্সিবিশনে; বহু দর্শনার্থী এসেছিলেন। কবি সুফিয়া কামাল অসুস্থ থাকার পরও এসেছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় তলায় ওঠার পর আর উঠতে পারছিলেন না। অবশেষে কবি আবদুস সাত্তারের সহায়তায় তিনি চতুর্থ তলায় ওঠেন। এমনকি সেদিন উপস্থিত হতে কবি বন্দে আলী মিয়া ঢাকায় এসেছিলেন।
মজার ব্যাপার হলো, উপস্থিত খাতায় সেদিন একজন লিখেছিলেন—“‘সব কিছু নিয়ে যেতে চাই জাদুঘরে”—এনামুল হক।’ তখনো আমি প্রত্নতাত্ত্বিক এনামুল হককে চিনতাম না। শুধু জানতাম, এই নামে একজন আছেন, যিনি জাদুঘরে কর্মরত। এরপর আমার জাদুঘরে কিছু করার ব্যাপারটি মাথায় আসে।
জয়নুল আবেদিন
 বাসার কাছে অবস্থানরত স্টুডিও নেহার কথা বলতেই হবে। সেই সময় ঢাকা শহরে সব মিলিয়ে ক্যামেরা ছিল ১৫০টি। স্টুডিও নেহার সঙ্গে আমার ১৯৬৩ সাল থেকে সম্পর্ক। ওদের ধার দেওয়া ক্যামেরা দিয়ে আমার প্রথম দিকের ছবি তোলা। প্রশিক্ষণ না থাকায় নিজের তাড়নায় ফটোগ্রাফি করেছি। আমার তেমন কোনো গুরু নেই। স্টুডিওভিত্তিক ফটোগ্রাফারদের কাছেই আমরা যেতাম। মনজুর আলম বেগ, আমানুল হক, নায়েব উদ্দিন, ড. নওয়াজেশ, আনোয়ার হোসেন, সাইদা খানম, গোলাম কাসেম ড্যাডি—সবার কাছ থেকেই শিখেছি। তবে সব ফটোগ্রাফারের চেয়ে আলাদা হওয়ার তাড়না ছিল আমার। সবাই বাইরের ছবি তোলেন; বিপরীতে, আমি ইনডোরে কৃত্রিম লাইট ছাড়া ন্যাচারাল ছবি তোলার পক্ষপাতী ছিলাম, যেখানে নরম মিষ্টি আলো-ছায়া খেলা করে। এমনও হয়েছে, কোনো বাসায় গিয়েছি যেখানে অনেক আলো; যেহেতু আমি আলো-ছায়া পছন্দ করি, তাই দরজা-জানালা বন্ধ করে দিয়ে শুধু একটি জানালা খোলা রেখে ছবি তুলতাম। শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের ছবিটি আমি এভাবেই তুলেছি। আলোর বিপরীতে যেখানে যাদের ছবি তুলতে গিয়েছি, তাদের মনে বীজ বপন করে এসেছি। এখনো সেই সব বাসায় গেলে তাদের সন্তান—যারা এখন বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছেন, নাতি-নাতনি যারা বড় হয়ে গিয়েছেন, তারা আমাকে সম্মান করেন। এর চেয়ে মহাকাব্য আমার মতো ক্ষুদ্র আলোকচিত্রশিল্পীর জীবনে আর কীই-বা হতে পারে!
বাসার কাছে অবস্থানরত স্টুডিও নেহার কথা বলতেই হবে। সেই সময় ঢাকা শহরে সব মিলিয়ে ক্যামেরা ছিল ১৫০টি। স্টুডিও নেহার সঙ্গে আমার ১৯৬৩ সাল থেকে সম্পর্ক। ওদের ধার দেওয়া ক্যামেরা দিয়ে আমার প্রথম দিকের ছবি তোলা। প্রশিক্ষণ না থাকায় নিজের তাড়নায় ফটোগ্রাফি করেছি। আমার তেমন কোনো গুরু নেই। স্টুডিওভিত্তিক ফটোগ্রাফারদের কাছেই আমরা যেতাম। মনজুর আলম বেগ, আমানুল হক, নায়েব উদ্দিন, ড. নওয়াজেশ, আনোয়ার হোসেন, সাইদা খানম, গোলাম কাসেম ড্যাডি—সবার কাছ থেকেই শিখেছি। তবে সব ফটোগ্রাফারের চেয়ে আলাদা হওয়ার তাড়না ছিল আমার। সবাই বাইরের ছবি তোলেন; বিপরীতে, আমি ইনডোরে কৃত্রিম লাইট ছাড়া ন্যাচারাল ছবি তোলার পক্ষপাতী ছিলাম, যেখানে নরম মিষ্টি আলো-ছায়া খেলা করে। এমনও হয়েছে, কোনো বাসায় গিয়েছি যেখানে অনেক আলো; যেহেতু আমি আলো-ছায়া পছন্দ করি, তাই দরজা-জানালা বন্ধ করে দিয়ে শুধু একটি জানালা খোলা রেখে ছবি তুলতাম। শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের ছবিটি আমি এভাবেই তুলেছি। আলোর বিপরীতে যেখানে যাদের ছবি তুলতে গিয়েছি, তাদের মনে বীজ বপন করে এসেছি। এখনো সেই সব বাসায় গেলে তাদের সন্তান—যারা এখন বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছেন, নাতি-নাতনি যারা বড় হয়ে গিয়েছেন, তারা আমাকে সম্মান করেন। এর চেয়ে মহাকাব্য আমার মতো ক্ষুদ্র আলোকচিত্রশিল্পীর জীবনে আর কীই-বা হতে পারে!
জয়নুল আবেদিনের এই ছবি ১৯৭৪ সালে তোলা। ওনার শান্তিনগরের বাসায়। জোনাকি সিনেমা হলের পাশের গলি দিয়ে একটু এগিয়ে গেলে হাতের বাঁয়ে ছিল ওনার বাসা। ১৯৭৪ সালের ৭ জুন ছিল সর্বাত্মক হরতাল। সেদিন আমি ক্যামেরা নিয়ে গ্রিন রোড থেকে তার বাসায় হেঁটে গিয়েছিলাম। তবে এর আগে থেকেই নানা জায়গায় ধরনা দিয়েছি, তাকে কীভাবে পাওয়া যায়। তিনি তখন অনেকটাই জীবনসায়াহ্নে। আমি যখন ছবি তুলতে যাই, তার শরীরে দানা বেঁধেছে ক্যানসার। যদিও তিনি তখনো সেটি বুঝতে পারেননি। লন্ডন থেকে সদ্যই চিকিৎসা নিয়ে ফিরেছেন। তেমন উন্নতি না হওয়ায় অপেক্ষা করছিলেন রাশিয়ার মস্কো যাওয়ার। শরীর ও কথা বলার গতি তখন ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেয়েছে তার। জীবনের শেষ বেলায় ছিলেন পিজি হাসপাতালে (বর্তমানে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়)। চিত্রশিল্পী শাহাবুদ্দিন আহমেদ ফোনে যোগাযোগ করিয়ে দিয়েছিলেন তার সঙ্গে। শাহাবুদ্দিন ছিলেন তার খুব প্রিয় ছাত্র।
বাসায় গিয়ে দেখি, শিল্পাচার্যের পরনে স্যান্ডো গেঞ্জি। অসুস্থতার কারণে তাকে শার্ট পরতে বলতে পারিনি। ভাবলাম, এমন ঘরোয়া পরিবেশে তাকে কেউ দেখেনি। সে সময় তিনি একটি সিগারেট ধরালেন; তাতেও নিষেধ করিনি। সেদিন এটি ছাড়াও আমি আরও কয়েকটি ছবি তুলেছিলাম তার। খেয়াল করলাম, তিনি অত্যন্ত অমায়িক মানুষ। আমাকে তখন তিনি কিছু উপদেশ দিয়েছিলেন, ‘তুমি বিখ্যাত মানুষের ছবি না তুইলা গ্রামে গিয়া ছোট বাচ্চা, বুড়া-বুড়ি, কৃষক, মাঝিসহ যেসব মানুষ আছে, তাদের সাথে থাইকা তারা যেই রকম চেহারায় থাকে, যে অবস্থায় থাকে তাদের পোর্ট্রেট তোলো। কোনো বাসায় যদি ফোকলোরের নিশানা পাও, চিহ্ন পাও, ছবি পাও, সেগুলোর ছবি তোলো। তোমার এক্সিবিশন আমি উদ্বোধন করতে আসব।’ উত্তরে বলেছিলাম, ‘স্যার, অনেক দূর তো আগায় গেছি, কয়েক বছর হয় কাজ শুরু করেছি। তবে আমি এটা করব।’ যদিও আমার আর সেসব করা হয়নি। দেখেছি পোর্ট্রেট জিনিসটি আমার মনের গভীরে বসবাস করে।
সেদিন দেখেছি, আবেদিন স্যার একটির পর একটি ক্যাপস্টান সিগারেট ধরাচ্ছেন। আমি তার কথা শুনতে চাইলে তিনি ‘হু, হুম, আচ্ছা, তাই তো…’ জাতীয় শব্দ দিয়ে কথা সারছিলেন। শরীরে ক্যানসার দানা বেঁধেছিল; তাই কথা বলা ছিল বেশ কষ্টের। সম্ভবত মেডিকেশনের ওপরও ছিলেন। হয়তো শাহাবুদ্দিনের রেফারেন্সের কারণেই এত কিছুর পরও আমাকে সময় দিয়েছিলেন। ছবি তুলে সেদিন চলে এসেছিলাম। তার পাশে দাঁড়িয়ে ছবি তোলার সাহস করিনি, ওই অসুস্থতা দেখে।
বাংলাদেশে শিল্পাচার্য তো একজনই। দেশের আধুনিক চারুশিল্প বা শিল্পকলা আন্দোলনে তিনি পথিকৃৎ। ১৯৪৮ সালে কলকাতা থেকে এসে জনসন রোডে ছোট প্রতিষ্ঠান গড়লেন একটি রুম নিয়ে। সঙ্গে ছিলেন চিত্রশিল্পী সফিউদ্দিন আহমেদ, কামরুল হাসান, আনোয়ারুল হক, শফিকুল আমিনসহ আরও কয়েকজন। দুঃখ একটাই, স্যার যে স্বপ্ন দেখেছিলেন, তা আজ অনেকটাই ভূলুণ্ঠিত! ব্রিটিশদের যে কারিকুলাম আমরা ফলো করতাম, ১৯৪৭ সালে কলকাতা আর্ট কলেজ থেকে আবেদিন স্যাররা পাস করেছেন, তা থেকে তিনি অনেক পরিবর্তন এনেছিলেন। কিন্তু সেই আমূল পরিবর্তনটা এখনো ঘটেনি। ফটোগ্রাফি সারা বিশ্বে একটি ইমার্জিং আর্ট। স্যার ১৯৪৮ সালে ফটোগ্রাফি বিভাগ খুলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সে সময় কোনো শিক্ষক না পাওয়ায় উদ্যোগটি আলোর মুখ দেখেনি। ১৯৬৩ সালে তিনি আবারও চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু পারেননি। আবেদিন স্যার তখন ২০ হাজার টাকার একটি বাজেট বের করেছিলেন, যা বর্তমানে প্রায় ৪০ লাখ টাকার সমতুল্য। সেই টাকা দিয়ে চিত্রশিল্পী মুস্তাফা মনোয়ার দুটি ক্যামেরা, সঙ্গে বেশ কিছু সরঞ্জাম কিনেছিলেন, যেন হাতেকলমে ফটোগ্রাফি শেখানো যায়। ১৯৬৩ অথবা ১৯৬৪ সালে তিনি পাকিস্তান টেলিভিশন ঢাকা কেন্দ্রে যোগ দেন। সেই সময় মনজুর আলম বেগ ইংরেজিতে কারিকুলাম টাইপ করে দিয়েছিলেন। কষ্টের ব্যাপার হলো, পরবর্তীকালে ওই কাগজগুলো আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। বলে রাখি, পেইন্টিংয়ের হাত ধরে ফটোগ্রাফি এসেছে। ফটোগ্রাফির ১৭৫ বছরের ইতিহাসের বিপরীতে পেইন্টিংয়ের ইতিহাস হাজার বছরের পুরোনো। চারুকলা ও শিল্পকলা পূর্ণাঙ্গ বিভাগ হওয়া উচিত ছিল, আর তা হলেই জয়নুল আবেদিন, কামরুল হাসান, এস এম সুলতানদের সর্বোচ্চ মর্যাদা দেওয়া হতো। শরীরের যেমন অসুখ হয়, তেমনি সময়ের অসুখ হয়, শিল্প-সাহিত্যের অসুখ হয়। আশা করি ৫০-১০০ বছর পর এই অসুখ সেরে যাবে।
কামরুল হাসান
 চিত্রশিল্পী কামরুল হাসানের এই ছবি ১৯৭৯ সালে তোলা। তখন তিনি থাকতেন ঢাকার গ্রিন সুপার মার্কেটের পেছনের দিকে। মার্কেটের গলি দিয়ে ঢুকলেই হাতের বাম পাশে ছিল ছোট চিকন বারান্দায় তার স্টুডিও। সেটি সাড়ে তিন ফুটের বেশি হবে না। সামনে কাচের সঙ্গে কাগজ লাগিয়ে কোনোরকম একটা ব্যবস্থা ছিল। আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম এত বড় শিল্পীর আর্থিক দৈন্য দেখে। তার বাসায় ছিল গুটিকয়েক ফার্নিচার; সেই সঙ্গে স্যাঁতসেঁতে দেয়াল।
চিত্রশিল্পী কামরুল হাসানের এই ছবি ১৯৭৯ সালে তোলা। তখন তিনি থাকতেন ঢাকার গ্রিন সুপার মার্কেটের পেছনের দিকে। মার্কেটের গলি দিয়ে ঢুকলেই হাতের বাম পাশে ছিল ছোট চিকন বারান্দায় তার স্টুডিও। সেটি সাড়ে তিন ফুটের বেশি হবে না। সামনে কাচের সঙ্গে কাগজ লাগিয়ে কোনোরকম একটা ব্যবস্থা ছিল। আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম এত বড় শিল্পীর আর্থিক দৈন্য দেখে। তার বাসায় ছিল গুটিকয়েক ফার্নিচার; সেই সঙ্গে স্যাঁতসেঁতে দেয়াল।
কামরুল হাসানের সঙ্গে আমার খুব ভালো সম্পর্ক ছিল। জীবদ্দশায় তিনি আমার প্রতিটি এক্সিবিশনে এসেছেন। ১৯৮৬ সালে বাংলা একাডেমিতে একটি এক্সিবিশন করেছিলাম। সেই সময় সেখানে তিনি নিয়মিত আসতেন এবং রাত আটটায় বইমেলা শেষ হলে একসঙ্গে বাসায় ফিরতাম। তখন আমরা দুজনই মণিপুরীপাড়ায় থাকতাম। তিনি ১ নম্বর বাসায় থাকতেন, আমি ১০৬/৭ নম্বরে। প্রায় দিনই ভোরবেলা একসঙ্গে সংসদ ভবন এলাকায় হাঁটতে যেতাম। সেখানে তার কাছে অনেকেই আসতেন; যাদের মধ্যে প্রথম বাঙালি মুসলিম চিত্রশিল্পী কাজী আবুল কাশেম, ফেরদৌস খান অন্যতম। সেই সূত্রে তাদের ছবিও আমি তুলেছি।
যাহোক, এই ছবিটা তোলার সময় এই জায়গায় একটি পেইন্টিং ঝোলানো ছিল। তিনি গেঞ্জি পরিহিত ছিলেন; পরবর্তীকালে অ্যাপ্রন পরে এলেন। এই অ্যাপ্রন পরেই তিনি ছবি আঁকতেন। আমার ছিল ওয়ান-টোয়েন্টি ক্যামেরা। এসব ক্যামেরার একটি সমস্যা ছিল। ফিক্সড লেন্স। এখন যেমন নানা ধরনের ক্যামেরা ও লেন্স ব্যবহার হয়, তখন ব্যাপারটি মোটেই তেমন ছিল না। সেই ক্যামেরা দিয়ে চাইলেই ক্লোজআপ শট নেওয়া যেত না, অথবা অনেক দূরে বা ওয়াইড অ্যাঙ্গেল করা যেত না। রুমে তেমন জায়গা না থাকায় কিছুটা প্রতিকূলতায় পড়তে হয়েছিল। আমার ক্যামেরা ও লেন্সের সর্বোচ্চ ব্যবহারের চেষ্টা করেছি এই ছবি তোলার ক্ষেত্রে। হয়তো কোনো ফ্রেম কমপ্যাক্ট হয়েছে, দূরে গেল ভালো লাগত—এমনটা আমার মনে হয়েছে পরবর্তীকালে।
সে সময়ে তার চুল ছিল পরিপাটি। আমি হাত দিয়ে চুল এলোমেলো করে দিয়েছিলাম। এটি করতে পেরেছিলাম; কারণ, তিনি আমাকে অনেক স্নেহ করতেন। ওই দিন তিনি আমার একটি পোর্ট্রেট এঁকে দিয়েছিলেন। তার প্যাডে আমার মোট দুটি পোর্ট্রেট করেছিলেন। আমার সম্পর্কে বেশ কিছু ভালো কথা লিখে দিয়েছিলেন নোটে।
কামরুল হাসান একা ও নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করতেন। আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে তার তেমন যোগাযোগ ছিল না। তবে ভাইদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন। এক ভাই তার বাসার ওপরের তলায় থাকতেন। অত্যন্ত অভিমানী মানুষ ছিলেন কামরুল হাসান। স্ত্রীর সঙ্গে সেপারেটেড ছিলেন। তার একজন কন্যা রয়েছে। অনেকটা সময় মেয়ের সঙ্গে যোগাযোগ না রাখলেও জীবনসায়াহ্নে সেই যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল। মেয়েই কামরুল হাসানের সবকিছু দেখভাল করতেন। এদের প্রত্যেকের জীবনই ভয়াবহ দুঃসময়ের মধ্য দিয়ে গিয়েছে।
এস এম সুলতান
 এই ছবিও ১৯৭৯ সালে তোলা, ডিসেম্বরে। এটি নড়াইলের চিত্রা নদীর পাড়ে মাসিমদিয়া গ্রামে তোলা। ১৯৭৮ সাল থেকে আমি নিয়মিত এস এম সুলতানের বাসায় যেতাম। ১৯৯২ সালে শেষবার গিয়েছিলাম। ১৯৯৪ সালের ১০ অক্টোবর তিনি মৃত্যুবরণ করেন। সেখানে গেলে আমি এই বাড়িতেই থাকতাম।
এই ছবিও ১৯৭৯ সালে তোলা, ডিসেম্বরে। এটি নড়াইলের চিত্রা নদীর পাড়ে মাসিমদিয়া গ্রামে তোলা। ১৯৭৮ সাল থেকে আমি নিয়মিত এস এম সুলতানের বাসায় যেতাম। ১৯৯২ সালে শেষবার গিয়েছিলাম। ১৯৯৪ সালের ১০ অক্টোবর তিনি মৃত্যুবরণ করেন। সেখানে গেলে আমি এই বাড়িতেই থাকতাম।
১৯৭৬ সালের ৫ সেপ্টেম্বর শিল্পকলা একাডেমিতে এস এম সুলতানের চিত্রকর্মের এক্সিবিশনে তার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়। কিন্তু ওনার সঙ্গে আমার তখনো যোগাযোগ স্থাপিত হয়নি। বিড়াল পোষা, বাঁশি বাজানোর মতো ব্যাপারগুলো আমাকে ভীত করত; কাছে গেলে হয়তো আমাকে চড়থাপ্পড় বসিয়ে দেবেন—এই ভয়েই প্রথমাবস্থায় তার বাসায় যাওয়া হয়নি। অনেকেই তাকে রাগী মানুষ মনে করলেও তিনি খুব কোমল হৃদয়ের ছিলেন। অনেকটা বোহিমিয়ান প্রকৃতির। হয়তো কথা দিলেন, আপনার সঙ্গে দেখা করবেন, কিন্তু তিনি এলেন না। হয়তো অন্য কোথাও চলে গিয়েছেন। কেন গিয়েছেন, সেটাও জানেন না।
যাহোক, তার সঙ্গে আমার সেন্টিমেন্টাল অ্যাটাচমেন্ট ছিল। বিভিন্ন সময়ে তিনি আমার আটটি ছবি এঁকেছিলেন। প্রতিবার গেলে ৮-১০ দিন আমি তার বাসায় থাকতাম। এমনকি একবার গিয়ে দুই মাস ছিলাম। আমি যখন এস এম সুলতান ভাইয়ের পাশে, মাটিতে বসে খাচ্ছিলাম, দেখলাম বিড়ালগুলো তার সামনে চলে এসেছে। সে সময় ছবিটি তোলার পরিকল্পনা করি। ফ্রেমে চারটি থাকলেও তার আরও অনেক পোষা বিড়াল ছিল। আমি ভাবলাম, এই দৃশ্য ধারণ করা দরকার। আঠালো হাত প্যান্টের ভেতর মুছে নিয়ে, কোনোরকমে ফোকাস করে, লো অ্যাঙ্গেলে ছবিটি তুলেছি। ছবিটি আদৌ উঠল কি না, তা নিয়ে সন্দেহ ছিল আমার। কারণ, সেখানে আলো ছিল না বললেই চলে। মজার ব্যাপার হলো, তিনি বিড়ালের সঙ্গে কথা বলতেন। ওই মুহূর্তে তিনি বলছিলেন, ‘আজকে বিরক্ত করিস না মেহমানকে, কালকে তোদের খেতে দেব।’ আর ঠিক তখনই এই ছবিটা তুলেছি। তখনই বুঝে গিয়েছিলাম, এস এম সুলতানের বাসায় খাবার নাই। ওই দিন উপলব্ধি করলাম, তিনিও দারিদ্র্যের মাঝে বসবাস করেন। এরপর তার বাসায় থাকতে গেলে কিছুটা কন্ট্রিবিউট করার চেষ্টা করতাম, যদিও সে সময় আমি ছিলাম বেকার। এত বড় শিল্পীর জীবনে যে দারিদ্র্য বিদ্যমান, সেদিনের সেই কথায় আমি তা বুঝতে পেরেছিলাম। আর ছবিটাও তেমন তোলার চেষ্টা করলাম—বিড়ালগুলো আসছে, মনিবের প্রতি ওদের যে একধরনের বিশ্বস্ততা—যা ছিল দেখার মতো, অন্যথায় ওরা খাবার থাবা দিয়ে নিয়ে যেত।
বিড়াল ছাড়াও তিনি কুকুর, বেজি, বনমোরগ, সাপ—এসব পুষতেন। আমি যে রুমে ঘুমাতাম, সেই ঘরে নেটের রেকের মধ্যেই সেসব প্রাণী থাকত। আমি নিচেই ঘুমাতাম। তার কোনো খাট ছিল না। বিছানা, লেপ, তোষক—কিছুই ছিল না। মাঘের শীতে প্যান্ট, শার্ট, জুতা, মোজা পরে ঘুমাতাম। মনে ভয় কাজ করত, আমি ঘুমিয়ে পড়লে ওই প্রাণীগুলো খাঁচা ভেঙে আমাকে ঠোকর দিয়ে খায় কি না! সে জন্য রাতে ঘুমাতে পারতাম না। একদিন আগাথা ক্রিস্টির সেই রহস্যময় চরিত্রের মতো এস এম সুলতান কালো আলখাল্লা পরে, হারিকেন নিয়ে ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে সকল প্রাণী চুপ মেরে গিয়েছিল; অথচ একটু আগেও এগুলো যে যার মতো চিৎকার-চেঁচামেচি করছিল। তার বাসায় সাপ্লাই পানি, বিদ্যুৎ—কিছুই না থাকায় এমনিতেই একটি ভুতুড়ে পরিস্থিতি বিরাজ করত। প্রতিটি খাঁচার সামনে গিয়ে তিনি সেদিন বলেছিলেন, ‘তোদের খাওয়া আজকে নাই। কালকে আশা করি তোদের খাওয়া দিতে পারব। মেহমান আসছে, একদম চুপ, ওনাকে ডিস্টার্ব করবি নে। মেহমান খুবই ভালো, তোদের ছবি তুলে দিবে।’ তিনি যতক্ষণ ছিলেন, সব প্রাণী চুপ করে ছিল। তিনি চলে যেতেই তারা আগের মতো আচরণ শুরু করে দিল!
অনুলিখন: ফুয়াদ রূহানী খান
ছবি: নাসির আলী মামুন/ফটোজিয়াম