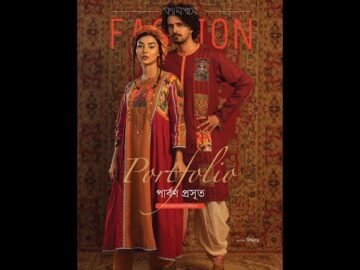ছুটিরঘণ্টা I নীল পাহাড় ছুঁয়ে নায়াগ্রার জলে
জগদ্বিখ্যাত জলপ্রপাত। তা সামনে থেকে দেখার আগে ও পরে ছড়ানো গভীরবোধী ভ্রমণবৃত্তান্ত। লিখেছেন বিধান রিবেরু
যাত্রা শুরু
যখন বায়ুযান আবিষ্কৃত হয়নি, কাঠের জাহাজে দাঁড়িয়ে থাকা নাবিকের হাতে কম্পাস ওঠেনি, নক্ষত্রখচিত আকাশ ও হাওয়ার শক্তিতে দুলে ওঠা পালই ছিল ভরসা, তখনো মানুষ দুর্বার টানে অভিযাত্রায় বের হতো। সেই যাত্রায় কি কেবল সম্পদ আহরণের মোহই থাকত? পথ পরিভ্রমণের আকর্ষণ কি থাকত না একেবারেই? নিশ্চয় থাকত, নয়তো এত এত পরিব্রাজক তৈরি হলো কোত্থেকে? পরিব্রাজকের মনন হয়তো আমরাও বহন করে চলেছি। আর এই কারণেই আমি ও আমার স্ত্রী মনি কানাডা ঘুরতে যাব বলে স্থির করি। কিন্তু আমাদের মতো মধ্যবিত্তের শুধু ঘুরতে যাওয়ার মতো বিলাসিতা করার সুযোগ নেই। তাই প্রায় এক বছর আগে থেকেই মনি তার বিজনেস মিটিং নির্ধারণ করে রাখে। আর আমি ঠিক করি, টরন্টো আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে যোগ দেব। রথ দেখা ও কলা বেচার তত্ত্বকে সামনে রেখে পরিকল্পনা করি কানাডা ভ্রমণের। ছেলে মনেকে সঙ্গে নিয়ে ঢাকা থেকে উড়াল দিই ৫ সেপ্টেম্বর ২০২৩।
 কানাডার উত্তরে আর্কটিক মহাসাগর, দক্ষিণে যুক্তরাষ্ট্র, পুবে অতলান্তিক আর পশ্চিমে প্রশান্ত মহাসাগর। মাঝখানের এই ভূখণ্ডকে বলা হয় পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম রাষ্ট্র। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ঠাসা এই দেশের প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য সর্বজনবিদিত। আর সবচেয়ে বেশি লোক জানে নায়াগ্রা জলপ্রপাতের কথা। আমরা নায়াগ্রাতে ছিলাম দুই রাত। তবে কানাডায় প্রথম ল্যান্ড করি মন্ট্রিয়লে। টরন্টোতে নামার টিকিট পাওয়া যাচ্ছিল না, তাই বাধ্য হয়ে অন্য শহরে নেমেছি। ওখানে এক রাত থেকে আমরা রওনা দিই টরন্টোর উদ্দেশে। সাত ঘণ্টার ড্রাইভ শেষে যখন টরন্টোতে এলাম, তখন ঘটল এক নাটকীয় ঘটনা।
কানাডার উত্তরে আর্কটিক মহাসাগর, দক্ষিণে যুক্তরাষ্ট্র, পুবে অতলান্তিক আর পশ্চিমে প্রশান্ত মহাসাগর। মাঝখানের এই ভূখণ্ডকে বলা হয় পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম রাষ্ট্র। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ঠাসা এই দেশের প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য সর্বজনবিদিত। আর সবচেয়ে বেশি লোক জানে নায়াগ্রা জলপ্রপাতের কথা। আমরা নায়াগ্রাতে ছিলাম দুই রাত। তবে কানাডায় প্রথম ল্যান্ড করি মন্ট্রিয়লে। টরন্টোতে নামার টিকিট পাওয়া যাচ্ছিল না, তাই বাধ্য হয়ে অন্য শহরে নেমেছি। ওখানে এক রাত থেকে আমরা রওনা দিই টরন্টোর উদ্দেশে। সাত ঘণ্টার ড্রাইভ শেষে যখন টরন্টোতে এলাম, তখন ঘটল এক নাটকীয় ঘটনা।
এয়ার বিএনবিতে আমরা যে বাসা ভাড়া নিয়েছিলাম, সেটি নাকি আমি ৪ সেপ্টেম্বর বাতিল করে দিয়েছি! প্লেনে ওঠার আগে কেন বুকিং বাতিল করব? আমার মাথায় বাজ পড়ল। কৃষ্ণাঙ্গ ভদ্রমহিলা বাতিলের মেইলও আমাকে দেখাতে পারলেন না। কিন্তু দয়া দেখালেন। জানালেন, এক রাত থাকতে পারব, যেহেতু এত দূর থেকে এসেছি! যাক, সে রাতটা থেকে পরদিনই আমরা আরেক জায়গায় থাকার ব্যবস্থা করে ফেলি। ভাগ্যিস, তারেক ভাই বলে একজন ছিলেন। তিনিই আমাদের মন্ট্রিয়ল থেকে টরন্টোতে ড্রাইভ করে এনেছেন। তো মাঝরাতের এই নাটক ট্র্যাজেডি হতে হতে হলো না ওনার কারণেই। উনি নিশ্চিন্ত করলেন, পরেরদিন আমরা বিকেল নাগাদ চলে যাব আরেকটি বাসায়। সেটি বাঙালি ভদ্রলোক ওয়ারেস ভাইয়ের বাসা। উনি পাতালের পুরো জায়গাটি ভাড়া দেন। দুটি শোয়ার ঘর, বৈঠকখানা, হেঁসেল—সব আছে। জায়গাটার নাম ইস্ট ইয়র্ক, ব্রেনটন স্ট্রিটের কাছে। প্রথম দিন চলচ্চিত্র উৎসবে কাটিয়ে দ্রুত ফিরতে হলো, যেহেতু বাসা বদল করব। তারপর এগারো দিন উৎসব চলল। ওদিকে মা-ছেলে নিজেদের মতো ঘোরাঘুরি করেছে, অফিসের মিটিংও সেরেছে।
 টরন্টোতে ঘোরাঘুরি
টরন্টোতে ঘোরাঘুরি
সব মিলিয়ে মোট চৌদ্দ দিন কাটিয়েছি টরন্টোতে। চলচ্চিত্র উৎসব শেষ করে হাতে আড়াই দিন সময় ছিল সেখানে। ওই সময়টাতেই টরন্টোর ছোটখাটো দর্শনীয় জায়গাগুলো একসঙ্গে ঘুরতে পেরেছি। অবশ্য উৎসব শেষের আগের দিন, ১৬ সেপ্টেম্বর, বিকেলে মনেকে নিয়ে সিএন টাওয়ারে যাই। মনে অনেক দিন ধরেই যেতে চাইছিল, কিন্তু আমার এ ধরনের টাওয়ারের ব্যাপারে খুব একটা কৌতূহল নেই। ছেলের আবদার বলে কথা! পড়ন্ত বিকেলে টিকিট কাটার জন্য লাইনে দাঁড়াই। তিনজনের খরচ পড়বে ১৩৬ কানাডীয় ডলার। এত পয়সা খরচ করে ওপর থেকে টরন্টো শহর দেখার কোনো অর্থ হয় না! কিন্তু মনের পীড়াপীড়ি। সে খুব উত্তেজিত। ‘বাবা, এটা কি দুবাইয়ের বুর্জ খলিফার চেয়ে বড়?’ বললাম, ‘না, এটা ২০০৭ সাল পর্যন্ত দুনিয়ার সবচেয়ে বড় মিনার হিসেবে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে ছিল। কিন্তু বুর্জ খলিফা এসে এই কানাডীয় ন্যাশনাল টাওয়ারকে ছাড়িয়ে গেছে। সিএন টাওয়ার বানানো শেষ হয় ১৯৭৬ সালে। তৈরির পর থেকে তিন দশকের বেশি সময় ধরে এই মিনারই সকলকে ছাপিয়ে আকাশে উঁকি মেরে ছিল একা।’
 যাহোক, টিকিট কেটে টাওয়ারের ভেতরে ঢোকা মানেই যে ওপরে উঠে গেলেন, তা নয়। সেখানে বিশাল লাইন। কমপক্ষে আধঘণ্টা পিঁপড়ার মতো সারিবদ্ধ হয়ে গুটিগুটি পায়ে এগোতে হবে লিফটের দিকে। লাইনের মাঝে এক জায়গায় আবার ছবি তোলার ব্যবস্থা রয়েছে। ফাঁকে ফাঁকে সিএন টাওয়ারের রেপ্লিকা, নির্মাণকালীন ছবি, নির্মাণসামগ্রী ও ভিডিও প্রেজেন্টেশন। আমরাও যথারীতি ছবি তুলে আবার লিফটের দিকে এগোচ্ছি। মনে কিছুটা অধৈর্য হয়ে উঠছে। কখন লিফটে চেপে ওপরে যাবে সে। ১৮১৫ দশমিক ৩ ফুট পর থেকে টরন্টো শহরকে সে দেখতে চায়। একসময় আমরা উঠলাম লিফটে। যখন সেটি ওঠা শুরু করল, তখন মনে বীরপুরুষ সেজে আমাদের বলে, ‘তোমরা কি ভয় পাচ্ছ? ভয় পাওয়ার কিছু নেই! এই তো আমরা এখনই নেমে যাব।’ বুঝলাম, সাত বছরের বালকটি নিজেকেই আসলে অভয় দিচ্ছে। আমরা বললাম, ‘একদম ভয় পাচ্ছি না, তুমি তো আছো।’ আসলে আমরাও কিছুটা ভয় পাচ্ছি! স্বচ্ছ কাচের ভেতর দিয়ে দেখা যাচ্ছে আমরা শাঁই শাঁই করে মাটি থেকে ওপরে উঠে যাচ্ছি। আর নিচে ছোট হয়ে যাচ্ছে মানুষ-দালানকোঠা-গাড়ি—সব। এক মিনিটের ভেতর আমরা পৌঁছে গেলাম চূড়ায়। সেখানে দেখলাম মানুষ অপার বিস্ময় নিয়ে নগর আর প্রকৃতির লীলা দেখছে। একদিকে অন্টারিও লেক, মাঝে ছোট্ট দ্বীপ ও দ্বীপের ভেতর বিলি বিশপ বিমানবন্দর, লেকের কোল ঘেঁষে গড়ে ওঠা আধুনিক নগরসভ্যতা।
যাহোক, টিকিট কেটে টাওয়ারের ভেতরে ঢোকা মানেই যে ওপরে উঠে গেলেন, তা নয়। সেখানে বিশাল লাইন। কমপক্ষে আধঘণ্টা পিঁপড়ার মতো সারিবদ্ধ হয়ে গুটিগুটি পায়ে এগোতে হবে লিফটের দিকে। লাইনের মাঝে এক জায়গায় আবার ছবি তোলার ব্যবস্থা রয়েছে। ফাঁকে ফাঁকে সিএন টাওয়ারের রেপ্লিকা, নির্মাণকালীন ছবি, নির্মাণসামগ্রী ও ভিডিও প্রেজেন্টেশন। আমরাও যথারীতি ছবি তুলে আবার লিফটের দিকে এগোচ্ছি। মনে কিছুটা অধৈর্য হয়ে উঠছে। কখন লিফটে চেপে ওপরে যাবে সে। ১৮১৫ দশমিক ৩ ফুট পর থেকে টরন্টো শহরকে সে দেখতে চায়। একসময় আমরা উঠলাম লিফটে। যখন সেটি ওঠা শুরু করল, তখন মনে বীরপুরুষ সেজে আমাদের বলে, ‘তোমরা কি ভয় পাচ্ছ? ভয় পাওয়ার কিছু নেই! এই তো আমরা এখনই নেমে যাব।’ বুঝলাম, সাত বছরের বালকটি নিজেকেই আসলে অভয় দিচ্ছে। আমরা বললাম, ‘একদম ভয় পাচ্ছি না, তুমি তো আছো।’ আসলে আমরাও কিছুটা ভয় পাচ্ছি! স্বচ্ছ কাচের ভেতর দিয়ে দেখা যাচ্ছে আমরা শাঁই শাঁই করে মাটি থেকে ওপরে উঠে যাচ্ছি। আর নিচে ছোট হয়ে যাচ্ছে মানুষ-দালানকোঠা-গাড়ি—সব। এক মিনিটের ভেতর আমরা পৌঁছে গেলাম চূড়ায়। সেখানে দেখলাম মানুষ অপার বিস্ময় নিয়ে নগর আর প্রকৃতির লীলা দেখছে। একদিকে অন্টারিও লেক, মাঝে ছোট্ট দ্বীপ ও দ্বীপের ভেতর বিলি বিশপ বিমানবন্দর, লেকের কোল ঘেঁষে গড়ে ওঠা আধুনিক নগরসভ্যতা।
 এবার মনে শুরু করল, তার ক্ষুধা লেগেছে। কারণ, ওপরের তলার রেস্তোরাঁ থেকে মন আকুল করা খাবারের মিষ্টি গন্ধ ভেসে আসছে। আমরা উঠতে গেলে সিঁড়িতে দাঁড়ানো রেস্তোরাঁর লোক জিজ্ঞেস করলেন, আমাদের আগে রিজারভেশন দেওয়া আছে কি না। বললাম, তা তো নেই। লোকটি বিনয় দেখিয়ে জানালেন, রেস্তোরাঁ কানায় কানায় পূর্ণ, রিজারভেশন ছাড়া কাউকেই তারা বসতে দিতে পারছেন না। অগত্যা ওই তলাতেই একটি কফি শপ ছিল, সেখান থেকে ড্রিংকস আর খোয়াজো কিনে দিলে মনের দিল ঠান্ডা হলো। এরপর সন্ধ্যা গড়াতে গড়াতেই নীলাভ আকাশের ক্যানভাসে টরন্টো ধরা দিল অপরূপ হয়ে। আমরা অনেক ছবিটবি তুললাম। নিচের ফ্লোরে আবার কাচের ওপর দাঁড়িয়েও ছবি তোলা যায়। মনের মা একেবারেই যায়নি সেটার ওপর। আমি ভয়ে ভয়ে এক পা দিয়েছি। আর মনে ভ্রুক্ষেপ ছাড়া সেই কাচের ওপর দিয়ে শহর দেখেছে, আর হেঁটে বেরিয়েছে। এরপর আবার ওপরের তলায় উঠে নিশ্চুপ বসে পাখির চোখে উপভোগ করলাম মনোরম ভূমির প্রান্তরেখা। সেখানে প্রায় রাত নয়টা পর্যন্ত থেকে আমরা ফিরে এলাম বাসায়।
এবার মনে শুরু করল, তার ক্ষুধা লেগেছে। কারণ, ওপরের তলার রেস্তোরাঁ থেকে মন আকুল করা খাবারের মিষ্টি গন্ধ ভেসে আসছে। আমরা উঠতে গেলে সিঁড়িতে দাঁড়ানো রেস্তোরাঁর লোক জিজ্ঞেস করলেন, আমাদের আগে রিজারভেশন দেওয়া আছে কি না। বললাম, তা তো নেই। লোকটি বিনয় দেখিয়ে জানালেন, রেস্তোরাঁ কানায় কানায় পূর্ণ, রিজারভেশন ছাড়া কাউকেই তারা বসতে দিতে পারছেন না। অগত্যা ওই তলাতেই একটি কফি শপ ছিল, সেখান থেকে ড্রিংকস আর খোয়াজো কিনে দিলে মনের দিল ঠান্ডা হলো। এরপর সন্ধ্যা গড়াতে গড়াতেই নীলাভ আকাশের ক্যানভাসে টরন্টো ধরা দিল অপরূপ হয়ে। আমরা অনেক ছবিটবি তুললাম। নিচের ফ্লোরে আবার কাচের ওপর দাঁড়িয়েও ছবি তোলা যায়। মনের মা একেবারেই যায়নি সেটার ওপর। আমি ভয়ে ভয়ে এক পা দিয়েছি। আর মনে ভ্রুক্ষেপ ছাড়া সেই কাচের ওপর দিয়ে শহর দেখেছে, আর হেঁটে বেরিয়েছে। এরপর আবার ওপরের তলায় উঠে নিশ্চুপ বসে পাখির চোখে উপভোগ করলাম মনোরম ভূমির প্রান্তরেখা। সেখানে প্রায় রাত নয়টা পর্যন্ত থেকে আমরা ফিরে এলাম বাসায়।
পরদিন চলচ্চিত্র উৎসব শেষ করে গিয়েছিলাম বন্ধু সৈকতের দাওয়াত রক্ষা করতে। টরন্টোর বাঙালি পাড়ায়। রেস্তোরাঁর নাম আড্ডা। আমরা ভালোই আড্ডা মারলাম সেদিন। মূল ঘোরাঘুরি শুরু হলো পরের দিন, ১৮ সেপ্টেম্বর থেকে। সকালে রওনা দিলাম ব্লু মাউন্টেইনের দিকে। ওখানে রয়েছে স্কি রিসোর্ট। শীতকালে লোকে ইচ্ছেমতো বরফের ওপর খেলাধুলা করে। নীল পাহাড়ের অবয়ব আমাদের দেশের যেকোনো মামুলি টিলার মতো। তবে একে ঘিরে যে পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছে, তাতেই পর্যটকেরা মুগ্ধ হয়ে যান। সারা দিন থাকার জন্য নানা ধরনের অ্যাডভেঞ্চার গেম, দোকানপাট, বাহারি রেস্তোরাঁ রয়েছে এখানে।
 মেঘ আর রোদের লুকোচুরিতে কখনো ঠান্ডা, কখনো সহিষ্ণু আবহাওয়া। ওদিকে মনে জোর করে পরে এসেছে হাফপ্যান্ট। এবার তার ঠান্ডা লাগছে। আমার জ্যাকেটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে হাঁটছে, কিন্তু পা ঢাকবে কী দিয়ে? পরে তার মা গজগজ করতে করতে চল্লিশ ডলার দিয়ে একটি ট্রাউজার কিনে দিল কলাম্বিয়া স্পোর্টসওয়্যার থেকে। ওখানে সবকিছুর দোকান মজুত রয়েছে। কাপড়চোপড় থেকে শুরু করে খেলনাপাতি, ক্যান্ডি থেকে স্মারক…কী নেই? মনে ট্রাউজার পরে বেশ আরাম বোধ করছে, আমাদেরও শান্তি।
মেঘ আর রোদের লুকোচুরিতে কখনো ঠান্ডা, কখনো সহিষ্ণু আবহাওয়া। ওদিকে মনে জোর করে পরে এসেছে হাফপ্যান্ট। এবার তার ঠান্ডা লাগছে। আমার জ্যাকেটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে হাঁটছে, কিন্তু পা ঢাকবে কী দিয়ে? পরে তার মা গজগজ করতে করতে চল্লিশ ডলার দিয়ে একটি ট্রাউজার কিনে দিল কলাম্বিয়া স্পোর্টসওয়্যার থেকে। ওখানে সবকিছুর দোকান মজুত রয়েছে। কাপড়চোপড় থেকে শুরু করে খেলনাপাতি, ক্যান্ডি থেকে স্মারক…কী নেই? মনে ট্রাউজার পরে বেশ আরাম বোধ করছে, আমাদেরও শান্তি।
নীল পাহাড়ের কাছে গিয়ে এর উচ্চতা দেখে যখন আমরা হতাশ, তখন রক্ষণাবেক্ষণে থাকা এক বুড়ো মহিলা বললেন, ‘নির্ভর করে তুমি কোথা থেকে এসেছ। তুমি যদি আল্পস পর্বতমালা দেখে আসো, তাহলে এটাকে খুবই মামুলি ঠেকবে।’ ওনাকে বললাম, ‘আমরা এসেছি হিমালয়ের কাছাকাছি দেশ থেকে।’ ভদ্রমহিলা এবার দুহাত তুলে হেসেই দিলেন! তারপরও বাগান ও পথবিন্যাস এত চমৎকারভাবে করা, তাতে ঘোরাঘুরি করে অনায়াসে কয়েক ঘণ্টা কাটিয়ে দেওয়া যায়। আমরা তা-ই করলাম। একটি পুরোনো স্যুভেনির শপে ঢুকলাম। তার ভেতরে আবার বানানো হচ্ছে দুধ ও ক্রিম দিয়ে গরম-গরম ক্যান্ডিবার। দুই রকমের দুটো কিনে আমরা গেলাম আরেক রেস্তোরাঁয়। মনের পছন্দ বার্গার। আমার স্যালাদ। মনির রুটির রোল। বিশাল বিশাল ডিশ। সময় নিয়ে আয়েশ করে খেলাম। সঙ্গে চড়ুই পাখির দল। পর্যটকদের কাছ থেকে পাওয়া খাবার খেয়ে বেশ মোটাতাজা ওরা। মনে আচ্ছাসে খাওয়াল পাখিগুলোকে।
 নীল পাহাড় থেকে ফিরতি পথে আমাদের ট্যুর গাইড তারেক ভাই নিয়ে গেলেন কলিংউডের চমৎকার সানসেট পয়েন্ট পার্কে। গাড়ি থেকে নামতেই কনকনে ঠান্ডা বাতাসের ঝাপটা। মনে বলে উঠল, সে গাড়িতেই বসে থাকবে। তারেক ভাইয়ের সঙ্গে বসে বসে সে গাড়িতেই গল্প করল। ঠান্ডা হাওয়া উপেক্ষা করে আমরা এগোলাম। নটাওয়াসাগা উপসাগরের হাড়কাঁপানো বাতাসের ঝাপটা সহ্য করে নিচ্ছি, ছবি তোলার জন্য। ছবি তুলতে তুলতে খেয়াল করলাম, অনেকগুলো পাথর থরে থরে এমনভাবে সাজানো, যেন একটি লোক হাত-পা ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সামনে থাকা পাথুরে ফলকে দেখলাম লেখা রয়েছে, এই ধরনের পাথরসজ্জাকে বলা হয় আইনুকশুক। এই আইনুকশুক হলো কানাডার একটি আইকনিক সিম্বল। এই অঞ্চলে এমন আইনুকশুক বহু দেখতে পাওয়া যাবে। এখানকার লোকে এভাবে পাথর সাজিয়ে রাখে। কিন্তু কেন? আর এর অর্থই-বা কী? আদিবাসী ভাষার আইনুকশুক মানে হলো ‘মানুষপ্রতিম’ বা মানুষের মতো। এভাবে মানুষের মতো বাহুপ্রসারিত করে প্রস্তরসজ্জার পেছনের কারণ হলো এটি বসিয়ে ল্যান্ডমার্ক বা সীমারেখা চিহ্নিত করা হয়, যেন আইনুকশুক বলছে কোন দিকে এগিয়ে যেতে হবে।
নীল পাহাড় থেকে ফিরতি পথে আমাদের ট্যুর গাইড তারেক ভাই নিয়ে গেলেন কলিংউডের চমৎকার সানসেট পয়েন্ট পার্কে। গাড়ি থেকে নামতেই কনকনে ঠান্ডা বাতাসের ঝাপটা। মনে বলে উঠল, সে গাড়িতেই বসে থাকবে। তারেক ভাইয়ের সঙ্গে বসে বসে সে গাড়িতেই গল্প করল। ঠান্ডা হাওয়া উপেক্ষা করে আমরা এগোলাম। নটাওয়াসাগা উপসাগরের হাড়কাঁপানো বাতাসের ঝাপটা সহ্য করে নিচ্ছি, ছবি তোলার জন্য। ছবি তুলতে তুলতে খেয়াল করলাম, অনেকগুলো পাথর থরে থরে এমনভাবে সাজানো, যেন একটি লোক হাত-পা ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সামনে থাকা পাথুরে ফলকে দেখলাম লেখা রয়েছে, এই ধরনের পাথরসজ্জাকে বলা হয় আইনুকশুক। এই আইনুকশুক হলো কানাডার একটি আইকনিক সিম্বল। এই অঞ্চলে এমন আইনুকশুক বহু দেখতে পাওয়া যাবে। এখানকার লোকে এভাবে পাথর সাজিয়ে রাখে। কিন্তু কেন? আর এর অর্থই-বা কী? আদিবাসী ভাষার আইনুকশুক মানে হলো ‘মানুষপ্রতিম’ বা মানুষের মতো। এভাবে মানুষের মতো বাহুপ্রসারিত করে প্রস্তরসজ্জার পেছনের কারণ হলো এটি বসিয়ে ল্যান্ডমার্ক বা সীমারেখা চিহ্নিত করা হয়, যেন আইনুকশুক বলছে কোন দিকে এগিয়ে যেতে হবে।
 ছবি তোলা শেষ হলে দৌড়ে এসে গাড়িতে বসি। যা ঠান্ডা! সন্ধ্যায় যেতে হবে চয়ন ভাইয়ের বাসায়, সেখানে বাঙালি খাবার প্রস্তুত। যাওয়ার পথে নামলাম এক খামারে, ফার্নউড ফার্মস মার্কেট। জমি থেকে সরাসরি সব শাকসবজি এই দোকানে এনে রাখা হয়। কোনো করপোরেট কোম্পানি নেই মাঝখানে। নিজেদের বানানো শরবত, চিজ, চিপস, মিঠাই…কী নেই! আমরা একটা শরবতের বোতল, আলুর চিপস আর ম্যাপেল সিরাপ দিয়ে বানানো ক্যান্ডি কিনলাম। খামারের সামনে হ্যালোইনের আবহ সৃষ্টি করা। জম্বিভূতও আছে। মনে খুব মজা করে ছবি তুলল। দুই দিকে বিস্তৃত মাঠ আর ভুট্টার খামার দেখতে দেখতে মাঝে মাঝে আপেলের বাগানও চোখে পড়ে। সবুজ গাছের নিচে অলস গড়াগড়ি খাচ্ছে লাল আপেল।
ছবি তোলা শেষ হলে দৌড়ে এসে গাড়িতে বসি। যা ঠান্ডা! সন্ধ্যায় যেতে হবে চয়ন ভাইয়ের বাসায়, সেখানে বাঙালি খাবার প্রস্তুত। যাওয়ার পথে নামলাম এক খামারে, ফার্নউড ফার্মস মার্কেট। জমি থেকে সরাসরি সব শাকসবজি এই দোকানে এনে রাখা হয়। কোনো করপোরেট কোম্পানি নেই মাঝখানে। নিজেদের বানানো শরবত, চিজ, চিপস, মিঠাই…কী নেই! আমরা একটা শরবতের বোতল, আলুর চিপস আর ম্যাপেল সিরাপ দিয়ে বানানো ক্যান্ডি কিনলাম। খামারের সামনে হ্যালোইনের আবহ সৃষ্টি করা। জম্বিভূতও আছে। মনে খুব মজা করে ছবি তুলল। দুই দিকে বিস্তৃত মাঠ আর ভুট্টার খামার দেখতে দেখতে মাঝে মাঝে আপেলের বাগানও চোখে পড়ে। সবুজ গাছের নিচে অলস গড়াগড়ি খাচ্ছে লাল আপেল।
সকাল থেকেই থেমে থেমে ইলশেগুঁড়ি। এখন পড়ন্ত বিকেলের হলদেটে রোদ। স্বচ্ছ নীল আকাশে তাই উঁকি দিয়েছে বিশাল এক রংধনু। আমরা গাড়ি থেকে আবার ছবি তুললাম। চয়ন ভাইয়ের বাসা পিকারিংয়ে। যাওয়ার রাস্তাটা ভীষণ সুন্দর। রাস্তার দুদিকে কনে দেখা আলোয় উদ্ভাসিত প্রকৃতি, তাতে কমলা রবির আলোকচ্ছটা। গাছে গাছে সবুজের ফাঁকে ফাঁকে লাল-হলুদের সমারোহ। প্রকৃতিকে কনস্টেবলের তুলির ছোঁয়া বলে ভ্রম হয়।
রাতের খাবারে চয়ন ভাই আর ভাবি আয়োজন করেছেন ইলিশ ভাজা, ভর্তা, করল্লা ভাজি, শুঁটকি…এসব। একেবারে ষোলোআনা বাঙালি খাবার। লাল দ্রাক্ষারস আছে। তো বিকেলটা কেবল আমরা শুরু করব, গ্লাসে তরল ঢালা হচ্ছে। তখনই খবর পেলাম, ঢাকায় মারা গেছেন চলচ্চিত্রকার সৈয়দ সালাহউদ্দীন জাকী। জাকী ভাইয়ের সঙ্গে আমার আলাপ-পরিচয় বহুদিনের। উনি স্নেহ করতেন আমাকে। ঢাকায় তখন রাত চারটার মতো বাজবে। আমি দ্রুত মোবাইল থেকেই খবর লিখে, ছবি সম্পাদনা করে আমাদের সংবাদ-দ্বারে প্রকাশ করে দিলাম।
সেদিনের নৈশভোজে দেখি, আমরা ছাড়াও চয়ন ভাই নিমন্ত্রণ করেছেন আরও একজনকে। জনৈক ভাবি, সঙ্গে এলেন তার এক বোন। তারা কানাডার অভিবাসন নিয়েছেন বহু বছর হলো। বাংলাদেশের বিত্তশালী মানুষ তারা; প্রভাবশালীও বটে। আমরা রাত নয়টা পর্যন্ত সিনেমা, রাজনীতি, ধর্ম—নানা বিষয়ে কথা বললাম। তারপর বিদায় নিয়ে উবারে করে চলে এলাম আমাদের ডস রোডের বাসায়। পরদিন সকালে আমাদের গন্তব্য ক্যাসা লোমা প্রাসাদ। মনে খুব উত্তেজিত। কিন্তু মনির শরীরটা বিশেষ ভালো যাচ্ছে না। এ নিয়ে আমি একটু বিচলিত; তবে মনি অভয় দিচ্ছে, সে বেরোতে পারবে।
 পরদিন সকালে হালকা মেঘের আনাগোনা থাকলেও, সকাল আটটার আগেই আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেল। ঝকঝকে রোদ। তারেক ভাই সময়মতো গাড়ি নিয়ে হাজির। আমরাও তৈরি হয়ে উঠে পড়লাম গাড়িতে। এটা-সেটা আলাপ করতে করতে চলে এলাম ক্যাসা লোমা প্রাসাদে। পাঁচ একর জায়গার ওপর প্রাসাদের মতো করে বানানো বাড়িটি আদতে প্রাসাদ নয়। এখানকার বাসিন্দারা রাজা-বাদশা ছিলেন না; তবে ঠাটবাট রাজন্যদের চেয়ে কোনো অংশে কম নয়।
পরদিন সকালে হালকা মেঘের আনাগোনা থাকলেও, সকাল আটটার আগেই আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেল। ঝকঝকে রোদ। তারেক ভাই সময়মতো গাড়ি নিয়ে হাজির। আমরাও তৈরি হয়ে উঠে পড়লাম গাড়িতে। এটা-সেটা আলাপ করতে করতে চলে এলাম ক্যাসা লোমা প্রাসাদে। পাঁচ একর জায়গার ওপর প্রাসাদের মতো করে বানানো বাড়িটি আদতে প্রাসাদ নয়। এখানকার বাসিন্দারা রাজা-বাদশা ছিলেন না; তবে ঠাটবাট রাজন্যদের চেয়ে কোনো অংশে কম নয়।
টরন্টোর সবচেয়ে উঁচু জায়গায় গড়ে তোলা এই প্রাসাদপ্রতিম বাড়িটির নির্মাণকাজ শেষ হয় ১৯১১ সালে। বিনিয়োগকারী ও সাবেক সেনা কর্মকর্তা স্যার হেনরি পেল্যাট পাতালসহ তেতলা বিশাল বাড়িটি বানাতে আহ্বান জানান সেকালের বিখ্যাত স্থপতি ই. জে. লেনক্সকে। তিন শ লোক দিয়ে টানা তিন বছরের প্রচেষ্টায় তিনি এডওয়ার্ডিয়ান স্টাইলে প্রাসাদতুল্য বাড়িটি বানিয়ে দেন। এটি পরিণত হয় কানাডার সবচেয়ে বড় ব্যক্তিগত আবাসিক ভবনে। দুই লাখ বর্গফুটের বাড়িটি বানাতে খরচ পড়ে তখনকার হিসাবে ৩৫ লাখ কানাডীয় ডলার।
এত দামি বাসভবনটি কিন্তু স্যার হেনরি ও তার স্ত্রী লেডি মেরি বেশি দিন ভোগ করতে পারেননি। মাত্র দশ বছরের ভেতরেই তাদের বাড়িটি ছেড়ে দিতে হয়। ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ার জন্য। পরে বাড়িটি টরন্টো শহরের সবচেয়ে বড় পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে ওঠে। স্যার হেনরি শুধু এ জন্যই গুরুত্বপূর্ণ নন যে, তিনি এত বড় একটি বাড়ি বানিয়েছেন। তিনিই প্রথম টরন্টোতে হাইড্রো ইলেকট্রিসিটির প্রচলন ঘটান। ঐতিহাসিকভাবে তাই স্থাপনাটি গুরুত্বপূর্ণ।
 আমরা এসে দেখি, এখানে বিয়ের শুটিং চলছে। প্রায়ই নাকি এমনটা দেখা যায়। নবদম্পতি ক্যাসা লোমার সামনে থাকা বাগান, ভেতরের বৈঠকখানা ও পুরোনো আসবাবের সামনে ছবি তোলে। আমরা টিকিট কেটে ভেতরে ঢুকলাম। প্রথম তলাতে রয়েছে বৈঠকখানা, পাঠাগার, পাঠকক্ষ, বাগানঘর, সকালের নাশতা ও রাতের খাবার খাওয়ার ঘর। পাঠাগারে মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত বই আর বই। চোখ জুড়িয়ে যায়। দু-একটি বইয়ের নাম পড়ার চেষ্টা করলাম। চামড়ায় বাঁধানো ক্ল্যাসিক ছাড়াও কিছু আধুনিক বই চোখে পড়ল। তার মানে রক্ষণাবেক্ষণ কর্তৃপক্ষ নতুন বই এনে রেখেছে এখানটায়। এই পাঠাগারের নিচেই পাতালঘর। সেটি সাজানো হয়েছে হরর মুভির আবহে। মনে খুব মজা পেয়েছে। রয়েছে রেস্তোরাঁও।
আমরা এসে দেখি, এখানে বিয়ের শুটিং চলছে। প্রায়ই নাকি এমনটা দেখা যায়। নবদম্পতি ক্যাসা লোমার সামনে থাকা বাগান, ভেতরের বৈঠকখানা ও পুরোনো আসবাবের সামনে ছবি তোলে। আমরা টিকিট কেটে ভেতরে ঢুকলাম। প্রথম তলাতে রয়েছে বৈঠকখানা, পাঠাগার, পাঠকক্ষ, বাগানঘর, সকালের নাশতা ও রাতের খাবার খাওয়ার ঘর। পাঠাগারে মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত বই আর বই। চোখ জুড়িয়ে যায়। দু-একটি বইয়ের নাম পড়ার চেষ্টা করলাম। চামড়ায় বাঁধানো ক্ল্যাসিক ছাড়াও কিছু আধুনিক বই চোখে পড়ল। তার মানে রক্ষণাবেক্ষণ কর্তৃপক্ষ নতুন বই এনে রেখেছে এখানটায়। এই পাঠাগারের নিচেই পাতালঘর। সেটি সাজানো হয়েছে হরর মুভির আবহে। মনে খুব মজা পেয়েছে। রয়েছে রেস্তোরাঁও।
এই ক্যাসা লোমাতে হলিউড ও কানাডার অনেক বিখ্যাত চলচ্চিত্রের শুটিং হয়েছে। সবচেয়ে বিখ্যাত ছবিটির নাম ‘এক্স-মেন’ (২০০০)। লাইব্রেরি ও স্টাডি রুমগুলো ব্যবহৃত হয়েছে এই সিনেমায়। সেসব দৃশ্য আবার সযত্নে এরা প্রচারও করছে প্রজেক্টরের মাধ্যমে। মানে পর্যটকদের আকৃষ্ট করার জন্য যা যা দরকার, তাই করে রেখেছে এরা। ‘এক্স-মেন’ ছাড়াও ‘স্ট্রেঞ্জ ব্রু’, ‘শিকাগো’, ‘দ্য টাক্সেডো’, ‘টাইটানস’ প্রভৃতি চলচ্চিত্রের দৃশ্যে দেখা যায় এই ক্যাসা লোমাকে। সেসব ছবির তারকাদের মোমের মূর্তিও গড়ে রাখা হয়েছে এখানে, যেন পর্যটকেরা ছবি তুলতে পারেন।
বাসভবনটি হরর মুভি বা সিরিজ নির্মাতাদের জন্য যে বেশ পছন্দের একটি জায়গা, তা এখানে শুটিংয়ের তালিকা দেখলেও বোঝা যায়। পাতালে গলিঘুপচিতে যে ভয়ের আবহ তৈরি করে রাখা হয়েছে, সেটা দেখলে মনে হয় সত্যিই কোনো হরর মুভির সেটে ঢুকে পড়েছি। ভবনের বাইরে একটি সুন্দর বাগানও রয়েছে।
আমরা দুপুরের খাবার ক্যাসা লোমার পাতাল রেস্তোরাঁয় খেয়ে বেরিয়ে এলাম। ঘড়িতে তখন আড়াইটা। আমরা ঠিক করে রেখেছিলাম, মনের জন্য অন্টারিও সায়েন্স সেন্টারে যাব। এখান থেকে বিজ্ঞান কেন্দ্রে যেতে লাগবে আধঘণ্টা। আর সেন্টারটি খোলা থাকে বিকেল চারটা পর্যন্ত। এক ঘণ্টা সময় হাতে থাকবে। নর্থ ইয়র্কের বিজ্ঞান কেন্দ্রে ঠিক তিনটাতেই পৌঁছালাম। গাড়ি থেকে নেমে দেখি বিশাল ভবন। মূল ফটকের কাছেই বাস দাঁড়িয়ে। ছোট সেই বাসে করে আমাদের নিয়ে যাওয়া হলো আরেকটি বিশাল ভবনে। যেহেতু সময় কম, আর মনের প্রিয় বিষয় মহাকাশ, তাই ঠিক করলাম, ওই শাখাতেই এক ঘণ্টা ব্যয় করব।
 মহাকাশ গবেষণায় কানাডার উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। তারই ছাপ দেখা গেল মহাকাশবিজ্ঞান শাখাতে। মঙ্গলগ্রহ থেকে আসা উল্কাপিণ্ডের খণ্ড রাখা আছে বেশ যত্ন করে। পাশাপাশি কৃষ্ণগহ্বর কীভাবে কাজ করে, তার একটি চমৎকার ইনস্টলেশন। মনে দীর্ঘক্ষণ মনোযোগ দিয়ে সেটা দেখল। কিছুটা ইন্টারেকটিভ হওয়ায় সে মজাও পেল। আশপাশের বর্ণনাগুলো অবশ্য তাকে পড়ে বুঝিয়ে দিতে হলো: নক্ষত্র কখন কৃষ্ণগহ্বরে পরিণত হয়; হলে তার প্রভাবে কী কী ঘটে…ইত্যাদি। আরেকটি আকর্ষণ হলো এই শাখায় সত্যিকারের মহাকাশযানের চেয়ার বসানো রয়েছে। সময় প্রায় শেষ। আমরা নিচে নেমে মানবশরীর নিয়ে সাজানো একটি কক্ষে ঢুকলাম। স্পিকারে তখন তাড়া দেওয়া হচ্ছে। সময় শেষ। আমরা বেরিয়ে যেন বাসে উঠে পড়ি। ভবনের বাইরে বাস দাঁড়িয়ে। সবাই সারি বেঁধে আবার বাসে উঠে গেলাম। আমাদের তিনজনের খরচ পড়েছিল ৭৫ কানাডীয় ডলার। এক ঘণ্টায় ঠিক পয়সা উসুল হয়নি। কারণ, আরও বহু কিছু দেখার বাকি ছিল। বাচ্চাদের খেলার জায়গাও ছিল। কিন্তু সময়ের অভাবে আর সেগুলোতে যাওয়া হলো না।
মহাকাশ গবেষণায় কানাডার উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। তারই ছাপ দেখা গেল মহাকাশবিজ্ঞান শাখাতে। মঙ্গলগ্রহ থেকে আসা উল্কাপিণ্ডের খণ্ড রাখা আছে বেশ যত্ন করে। পাশাপাশি কৃষ্ণগহ্বর কীভাবে কাজ করে, তার একটি চমৎকার ইনস্টলেশন। মনে দীর্ঘক্ষণ মনোযোগ দিয়ে সেটা দেখল। কিছুটা ইন্টারেকটিভ হওয়ায় সে মজাও পেল। আশপাশের বর্ণনাগুলো অবশ্য তাকে পড়ে বুঝিয়ে দিতে হলো: নক্ষত্র কখন কৃষ্ণগহ্বরে পরিণত হয়; হলে তার প্রভাবে কী কী ঘটে…ইত্যাদি। আরেকটি আকর্ষণ হলো এই শাখায় সত্যিকারের মহাকাশযানের চেয়ার বসানো রয়েছে। সময় প্রায় শেষ। আমরা নিচে নেমে মানবশরীর নিয়ে সাজানো একটি কক্ষে ঢুকলাম। স্পিকারে তখন তাড়া দেওয়া হচ্ছে। সময় শেষ। আমরা বেরিয়ে যেন বাসে উঠে পড়ি। ভবনের বাইরে বাস দাঁড়িয়ে। সবাই সারি বেঁধে আবার বাসে উঠে গেলাম। আমাদের তিনজনের খরচ পড়েছিল ৭৫ কানাডীয় ডলার। এক ঘণ্টায় ঠিক পয়সা উসুল হয়নি। কারণ, আরও বহু কিছু দেখার বাকি ছিল। বাচ্চাদের খেলার জায়গাও ছিল। কিন্তু সময়ের অভাবে আর সেগুলোতে যাওয়া হলো না।
পরবর্তী গন্তব্য বাসা। তবে বাসায় যাওয়ার পথে একটা পার্ক পড়ে, রোসেটা ম্যাকক্লেইন গার্ডেন, সেটা ঘুরে যাব। মনেও একটু দৌড়াদৌড়ি করতে পারবে। আমরা বাগানটিতে গিয়ে দেখলাম, সত্যিকার অর্থেই একে ফুলের বাগিচা বানিয়ে রাখা হয়েছে। মাঝখানে বিশাল এক পাথর আর ঝরনা। পাথরটি দেখে ওবেলিস্কের কথা মনে পড়ে গেল। এদিক-সেদিক প্রজাপতির ওড়াউড়ি। কাঠবিড়ালির ছোটাছুটি। রাজহাঁসও রয়েছে। মনে কাঠবিড়ালির সঙ্গে খেলায় মজে গেল। বাগানটির এক পাশ থেকে দেখা যায় অন্টারিও লেক। মৃদুমন্দ বাতাসে বাগানের নুড়ি বিছানো পথের পাশে পাতা রয়েছে বেঞ্চি। সেখানে আমরা দুজন খানিকটা বসলাম। মনে একবার এদিক, আরেকবার ওদিক মনের আনন্দে ছুটে বেড়াচ্ছে। না পেরে, আমিও কিছুক্ষণ ওর পিছু পিছু ছুটলাম। ঠিক সন্ধ্যা নামার মুখে বাগানের আরেক প্রান্তে গিয়ে দেখি হরেক রকমের গোলাপের সারি। কোনো গোলাপের কুঁড়ি ফুটেছে মাত্র, কোনোটি পুরোপুরি প্রস্ফুটিত। বিচিত্র গোলাপের বাগিচায় ভ্রমর আদানপ্রদান করছে পরাগরেণু। গোলাপের নামগুলোও কী সুন্দর: জুলিয়া চাইল্ড, ফ্লোরিবান্ডা, মডার্ন ব্লাশ, পার্কল্যান্ড শ্রাব, ল্যান্ডস্কেপ শ্রাব, ইননোসেন্সিয়া ভিগোরোসা, আরও কত কত নাম!
 সূর্য ডোবার মুহূর্তকে সঙ্গী করে আমরা ফিরে এলাম বাসায়। ফ্রেশ হয়ে হাতে নিয়ে বসি সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের (১৮৯১-১৯৫৪) লেখা বই ‘কানাডা’। ঢাকা থেকে আসার সময় সঙ্গে এনেছিলাম। সত্যেন্দ্রনাথ একসময় ‘আনন্দবাজার পত্রিকা’র সম্পাদক ছিলেন। বইটির গদ্যটা যেমন স্বাদু, তেমনি বেশ তথ্যবহুল। পাঠকৃত কিছু অংশ এখানে আমার মতো করে যদি তুলে দিই, তবে তা বাহুল্য হবে না। কানাডার ইতিহাস নিয়ে লেখা যেহেতু, পাঠক আগ্রহ পাবেন আশা করি।
সূর্য ডোবার মুহূর্তকে সঙ্গী করে আমরা ফিরে এলাম বাসায়। ফ্রেশ হয়ে হাতে নিয়ে বসি সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের (১৮৯১-১৯৫৪) লেখা বই ‘কানাডা’। ঢাকা থেকে আসার সময় সঙ্গে এনেছিলাম। সত্যেন্দ্রনাথ একসময় ‘আনন্দবাজার পত্রিকা’র সম্পাদক ছিলেন। বইটির গদ্যটা যেমন স্বাদু, তেমনি বেশ তথ্যবহুল। পাঠকৃত কিছু অংশ এখানে আমার মতো করে যদি তুলে দিই, তবে তা বাহুল্য হবে না। কানাডার ইতিহাস নিয়ে লেখা যেহেতু, পাঠক আগ্রহ পাবেন আশা করি।
বইতে দেখা যাচ্ছে, ১৫২৩ সালে ফ্রান্সের রাজা প্রথম ফ্রান্সিসের নির্দেশে গায়োভানি নামের এক ফরাসি নাবিক আমেরিকার দিকে রওনা দেন। প্রথম অভিযান ব্যর্থ হলেও দ্বিতীয়বারের চেষ্টায় তিনি আমেরিকার প্রধান ভূখণ্ডে উপস্থিত হন এবং হাজার দুয়েক মাইল পরিভ্রমণ করেন। ওখানেই ছিল যুক্তরাষ্ট্র আর কানাডার উপকূলভূমি। তিনি ধীরে ধীরে আমেরিকায় ফরাসি উপনিবেশ স্থাপনে মনোযোগ দেন। তবে অভিবাসনে ইচ্ছুক ফরাসিদের নিয়ে যাত্রা শুরু করলেও সলিলসমাধি ঘটে তার। তত দিনে অবশ্য উত্তর আমেরিকার এক অংশের নাম কানাডা হয়ে গেছে।
ফরাসিদের আগে থেকেই এই ভূখণ্ডে আনাগোনা শুরু হয় স্পানিয়ার্ডদের। স্পেন থেকে আগত নাবিক ও অভিযাত্রীদের দেখে উত্তর আমেরিকার আদিবাসীরা বলত ‘আকানাডা’ অর্থাৎ ‘এখানে কিছু নেই’। বোঝাই যাচ্ছে, বাইরের লোকেদের খোঁড়াখুঁড়ি ও লুটপাট নিবৃত্ত করতেই আদিবাসীরা বলার চেষ্টা করত, ‘বাবা, এখানে কিছু নেই, অন্যত্র দেখো।’ কিন্তু এই ইউরোপীয়রা নাছোড়বান্দা। আদিবাসীদের মুখে ‘আকানাডা’ শুনে তারা এই ভূখণ্ডকে আকানাডা বলে ডাকতে শুরু করে। পরে ওখান থেকেই কানাডা হিসেবে দেশটির নাম প্রতিষ্ঠা পেয়ে যায়। উত্তর আমেরিকা থেকে লোক ধরে ধরে নিয়ে স্পেন দাসব্যবসায় ফুলেফেঁপে উঠছে দেখে ফ্রান্স মরিয়া হয়ে ওঠে। তা ছাড়া স্পেনের ব্যবসায়ীরা কানাডা থেকে খুব কম দামে পালক কিনে ইউরোপের বাজার ছেয়ে ফেলছিল। এসব শুনে ফ্রান্সের রাজা যখন লোক ভর্তি করে জাহাজ পাঠানোর কথা ভাবলেন, তখনই তার কাছে এসে কানাডায় যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন ফরাসি নাবিক জ্যাক কার্টিয়ার।
 কার্টিয়ার লোকবহর নিয়ে ১৫৩৪ সালে নিউফাউন্ডল্যান্ড, মানে কানাডার পূর্বাঞ্চলে পা রাখেন। তিনি পৌঁছেই সেখানে ত্রিশ ফুট উঁচু বেদি নির্মাণ করে তার ওপর ফরাসি পতাকা উড়িয়ে দেন। তাতেই তিনি ক্ষান্ত হননি, ফরাসি রাজাকে উপহার দেওয়ার জন্য প্রচুর পালক সংগ্রহ করেন এবং ফ্রান্সে নিয়ে যান। সঙ্গে দুই রেড ইন্ডিয়ানকেও ধরেবেঁধে নিয়ে যান। রাজা এসবে বেজায় খুশি। এভাবেই কানাডায় যাতায়াত শুরু হয় ফরাসি কার্টিয়ার-গংয়ের। তারা আদিবাসীদের ওপর নানাবিধ অত্যাচার ও দাসব্যবসা শুরু করে। স্বভাবতই প্রতিবাদী হয়ে ওঠে আদিবাসীরা। ওদিকে স্পানিয়ার্ডরাও হাল ছাড়েনি। ফরাসিদের সঙ্গে তারাও যুদ্ধে লিপ্ত হয়। কানাডা নিয়ে এই দ্বিপক্ষীয় টানাটানি যখন কিছুটা কমে আসে, ব্যবসাবাণিজ্য বিস্তার লাভ করতে থাকে, তখন তাদের দেখে ওলন্দাজ ও ইংরেজরাও আগ্রহী হয়ে ওঠে এবং কানাডায় তাদের তরী ভেড়াতে থাকে। জনগাই, কাপ্তান রিচার্ড, হেনরি হাডসন প্রমুখ ইংরেজের যে নাম শোনা যায়, তারা কানাডায় ব্রিটিশ পতাকার ধ্বজাধারী হয়ে আসেন। এদের ভেতর হাডসন ছিলেন দুঃসাহসী। এক উপসাগর আবিষ্কার করার কৃতিত্বস্বরূপ সেটির নামকরণই করা হয় হাডসন বে। এই উপসাগর কানাডার উত্তরাঞ্চলে।
কার্টিয়ার লোকবহর নিয়ে ১৫৩৪ সালে নিউফাউন্ডল্যান্ড, মানে কানাডার পূর্বাঞ্চলে পা রাখেন। তিনি পৌঁছেই সেখানে ত্রিশ ফুট উঁচু বেদি নির্মাণ করে তার ওপর ফরাসি পতাকা উড়িয়ে দেন। তাতেই তিনি ক্ষান্ত হননি, ফরাসি রাজাকে উপহার দেওয়ার জন্য প্রচুর পালক সংগ্রহ করেন এবং ফ্রান্সে নিয়ে যান। সঙ্গে দুই রেড ইন্ডিয়ানকেও ধরেবেঁধে নিয়ে যান। রাজা এসবে বেজায় খুশি। এভাবেই কানাডায় যাতায়াত শুরু হয় ফরাসি কার্টিয়ার-গংয়ের। তারা আদিবাসীদের ওপর নানাবিধ অত্যাচার ও দাসব্যবসা শুরু করে। স্বভাবতই প্রতিবাদী হয়ে ওঠে আদিবাসীরা। ওদিকে স্পানিয়ার্ডরাও হাল ছাড়েনি। ফরাসিদের সঙ্গে তারাও যুদ্ধে লিপ্ত হয়। কানাডা নিয়ে এই দ্বিপক্ষীয় টানাটানি যখন কিছুটা কমে আসে, ব্যবসাবাণিজ্য বিস্তার লাভ করতে থাকে, তখন তাদের দেখে ওলন্দাজ ও ইংরেজরাও আগ্রহী হয়ে ওঠে এবং কানাডায় তাদের তরী ভেড়াতে থাকে। জনগাই, কাপ্তান রিচার্ড, হেনরি হাডসন প্রমুখ ইংরেজের যে নাম শোনা যায়, তারা কানাডায় ব্রিটিশ পতাকার ধ্বজাধারী হয়ে আসেন। এদের ভেতর হাডসন ছিলেন দুঃসাহসী। এক উপসাগর আবিষ্কার করার কৃতিত্বস্বরূপ সেটির নামকরণই করা হয় হাডসন বে। এই উপসাগর কানাডার উত্তরাঞ্চলে।
বইটি পড়তে পড়তে চোখ লেগে আসছিল। পরের দিন যাত্রা শুরু করব নায়াগ্রা জলপ্রপাতের দিকে। পথিমধ্যে ঢুঁ মারব আফ্রিকান লায়ন সাফারিতে। কাজেই তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়া প্রয়োজন।
নায়াগ্রার পথে
আগে থেকেই ঠিক করা ছিল, নায়াগ্রার কাছে গিয়ে আমরা দুই রাত থাকব। র্যাডিসনের কান্ট্রি স্যুটস অ্যান্ড ইনে দুই রাতের বুকিং দেওয়া ছিল। ওদের চেক-ইন বেলা দুটায়। কাজেই সকাল সকাল এসেও ওদের ওখানে উঠত পারব না। অতএব সিদ্ধান্ত হলো, তারেক ভাইয়ের গাড়ির পেছনে লাগেজ থাকবে, আমরা গাড়ি নিয়েই ঢুকে যাব আফ্রিকান লায়ন সাফারিতে। এটি নায়াগ্রা যাওয়ার পথেই পড়ে। ওখানে দুপুরে খেয়েদেয়ে চলে যাব নায়াগ্রাতে।
আমরা সাফারিতে গেলাম একটি গ্রামীণ পথ ধরে। দুপাশে ভুট্টাখেত, কখনো বিস্তীর্ণ সবুজ মাঠ, কখনোবা ঘন ম্যাপলের সারি। মাঝে মাঝে খামারবাড়ি চোখে পড়ে। ছবির মতোই সাজানো-গোছানো। আমরা দৃশ্যাবলি দেখতে দেখতে চলে এলাম আফ্রিকান লায়ন সাফারিতে। গাড়িসহ চারজনের ঢুকতে খরচ পড়ল এক শ কানাডীয় ডলারের কাছাকাছি। জন্তু-জানোয়ার সব খোলা ঘুরে বেড়াচ্ছে, মানুষের দল ধীরে ধীরে, সন্তর্পণে গাড়ি চালিয়ে আঁকাবাঁকা পথ ধরে এগোচ্ছে আর ওদের দেখছে। জিরাফ, জেব্রা, বুনো শূকর, হনুমান ইত্যাদির চেয়ে সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ সিংহের প্রতি। মনে জানালা অল্প একটু খুলে সিংহ আর সিংহীদের রৌদ্রস্নান দেখল। গাড়ির জানালা খোলাও এখানে নিষেধ। অদূরেই সাফারির নিরাপত্তাকর্মীরা গাড়ি নিয়ে বসে পর্যবেক্ষণ করছে সব। আমরা প্রতিটি প্রাণীর এলাকায় গিয়ে কিছুটা সময় থেমে ছবি তুললাম, গাড়িতে বসেই।
এরপর জানা গেল, এদের তিনটি অ্যানিমেল শো হয়। শো শুরুর আগে কিছুটা সময় রয়েছে। এই ফাঁকে আমরা সংক্ষিপ্ত ওয়াটার ক্রুজ আর টয়ট্রেনে রেলভ্রমণ করে নিলাম। দুটোই সাফারির ভেতর। জলপথ আর রেলপথ—দুই জায়গার ভ্রমণেই বিচিত্র প্রাণিকুলের দেখা মিলল, সঙ্গে নাম না জানা অপূর্ব লতাগুল্ম-ফুল। টয়ট্রেনে করে ঘোরার সময় দেখলাম কচ্ছপের ডিম আর ছানা। দুপাশে পেলাম বুনোফুলের অভিবাদন। মনে আমাদের সঙ্গে বসেনি। সে একা একা সামনে গিয়ে বসেছে। ওরা ট্রেনভ্রমণটার নাম দিয়েছে ‘ন্যাচার বয়: সিনিক রেলওয়ে’। নামকরণটি যথার্থই। কারণ, মনেকে আমি দেখলাম প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে সে পরিবেশটি উপভোগ করছে।
খেলনা স্টেশনের পাশেই রাখা রয়েছে হরেক রকম প্যাঁচা। আলাদা আলাদা খাঁচায়। কী তাদের রাশভারী চেহারা! চোখের দিকে তাকালে ভয়ই লাগে। আছে জায়ান্ট র্যাবিট, স্কুইরেল মাংকি, বাদুর—কত কী! একটা খুবই আদুরে প্রাণীর দেখা পেলাম: আলপ্যাকা। দক্ষিণ আমেরিকার গৃহপালিত এই জন্তুকে বাংলায় পেরুদেশীয় মেষও বলে। তবে মেষের মতো খর্বকায় নয়। অনেকটা উটের মতো দেখতে; উচ্চতা ঘোড়ার চেয়ে একটু কম। সাদা লোমশ প্রাণীটি ধুলো দিয়ে স্নান সারছিল, আমাদের দেখে গা ঝাড়া দিয়ে সামনে এসে দাঁড়াল। আর আমরা ধুলোয় ধূসরিত!
 এরপর দেখতে গেলাম পাখিদের নিয়ে করা একটি শো। কাক, মাছরাঙা, কাকাতুয়া ও ময়না—এইসব পক্ষীকুলকে নিয়ে এই খেলার আয়োজন। তারাও মানুষের মতো কথা বোঝে, নির্দেশনা মেনে কাজ করে, এমনকি নাচানাচিও করে। শো শেষে মনে গিয়ে কাকাতুয়ার সঙ্গে ছবি তুলল। এরপর আমরা দেখলাম শিকারি পাখিদের খেলা। সেটা আবার পাশের আরেক ভেন্যুতে। কত রকমের যে ঈগল, আর কী যে ক্ষিপ্রগামী তারা, ছোঁ মেরে সাফারির মেয়েদের হাত থেকে খাবার নিয়ে যায়! পোষমানা শকুনের খেলাও দেখা হলো। তবে সবচেয়ে আকর্ষণীয় ছিল সরীসৃপের শোটি। নানা ধরনের অ্যালিগেটর, কুমির, সাপের খেলা। এক রংচঙা বিশাল অজগর, ওজন ৭০ কেজি, তাকে নিয়ে এক তরুণী এলো। নির্বিকার চিত্তে সে পুরো শরীরে অজগর পেঁচিয়ে মাঠে ঘুরে বেড়াল। শো শেষে সব বাচ্চা অজগরটির সঙ্গে ছবি তুলতে ভিড় করল। মনেও দৌড়ে গেল। ছবি তোলার জন্য যে-ই না আমার দিকে তাকাল, অমনি ওই সর্পকন্যা মনের মাথার কাছে অজগরের মুখটি ধরল। মনে বুঝতেও পারল না আমি সেই ছবি তুলে নিয়েছি। পরে মোবাইলে যখন দেখালাম, সে খুব অবাক। আর তার মায়ের কথা কী বলব! সাপকে তার ভয়, তাই দূরে দূরেই রইল।
এরপর দেখতে গেলাম পাখিদের নিয়ে করা একটি শো। কাক, মাছরাঙা, কাকাতুয়া ও ময়না—এইসব পক্ষীকুলকে নিয়ে এই খেলার আয়োজন। তারাও মানুষের মতো কথা বোঝে, নির্দেশনা মেনে কাজ করে, এমনকি নাচানাচিও করে। শো শেষে মনে গিয়ে কাকাতুয়ার সঙ্গে ছবি তুলল। এরপর আমরা দেখলাম শিকারি পাখিদের খেলা। সেটা আবার পাশের আরেক ভেন্যুতে। কত রকমের যে ঈগল, আর কী যে ক্ষিপ্রগামী তারা, ছোঁ মেরে সাফারির মেয়েদের হাত থেকে খাবার নিয়ে যায়! পোষমানা শকুনের খেলাও দেখা হলো। তবে সবচেয়ে আকর্ষণীয় ছিল সরীসৃপের শোটি। নানা ধরনের অ্যালিগেটর, কুমির, সাপের খেলা। এক রংচঙা বিশাল অজগর, ওজন ৭০ কেজি, তাকে নিয়ে এক তরুণী এলো। নির্বিকার চিত্তে সে পুরো শরীরে অজগর পেঁচিয়ে মাঠে ঘুরে বেড়াল। শো শেষে সব বাচ্চা অজগরটির সঙ্গে ছবি তুলতে ভিড় করল। মনেও দৌড়ে গেল। ছবি তোলার জন্য যে-ই না আমার দিকে তাকাল, অমনি ওই সর্পকন্যা মনের মাথার কাছে অজগরের মুখটি ধরল। মনে বুঝতেও পারল না আমি সেই ছবি তুলে নিয়েছি। পরে মোবাইলে যখন দেখালাম, সে খুব অবাক। আর তার মায়ের কথা কী বলব! সাপকে তার ভয়, তাই দূরে দূরেই রইল।
এই শো দেখার ফাঁকে আমরা কানাডার সহজলভ্য খাবার পুটিন খেয়ে নিয়েছি। ফ্রেঞ্চ ফ্রাইয়ের ওপর চিকেনের গ্রেভি আর হোয়াইট চিজ। সুস্বাদু। তবে আপনি চাইলে টপিংস নিজের ইচ্ছেমতো যোগ-বিয়োগ করে নিতে পারবেন। কেউ বেকন যোগ করে, কেউবা টমেটো কেচাপ!
আমরা সাফারির পালা গুটিয়ে রওনা দিলাম নায়াগ্রার উদ্দেশে। আবার সেই চমৎকার সুনসান গ্রামীণ পথ ধরে এগোতে লাগলাম। অনন্ত গাছগাছালি। বিকেল পাঁচটা নাগাদ পৌঁছলাম নায়াগ্রার কাছের হোটেলটিতে। তারেক ভাই বিদায় নিলেন। আমরা রুমে গাট্টিবোঁচকা রেখেই বেরিয়ে পড়লাম। আগে এক ভারতীয় হোটেলে খাওয়াদাওয়া করলাম। পাঞ্জাবি রেস্তোরাঁয় আমরা ভাত, ঘন ডাল, ঝাল মুরগি, কাবাব আর পরোটা নিলাম। এদের খাবার মজাদার। ঠিক করলাম পরের দিনও এখানেই খাব। বিল মিটিয়ে পা বাড়ালাম জলপ্রপাতের দিকে। বিখ্যাত জলপ্রপাত, যা দেখতে পৃথিবীর দূরদূরান্ত থেকে লাখ লাখ পর্যটক ভিড় জমান।
খুব কাছেই, ১০ মিনিটের হাঁটা পথ। কাছাকাছি যেতেই জলের গর্জন আর জলপ্রপাতের রাজকীয় সৌন্দর্য দেখে বিমোহিত হলাম। মনে ও মনি ছবি তুলল। আমিও। এরপর ছবি তোলা বন্ধ রেখে আমরা তিনজনই নিষ্পলক তাকিয়ে রইলাম জলপ্রপাতের দিকে। ওই দিকটায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। আর এইদিকে কানাডা। একটি সেতু দিয়ে পার হওয়া যায়। তবে ভিসা লাগে। আমরা কানাডা প্রান্তে উদ্যান ঘেঁষে বানানো পথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে অনেক দূর চলে গেলাম। শুনলাম রাত দশটায় নাকি জলপ্রপাতের ওপর আতশবাজি পোড়ানো হবে। ঠিক করলাম এই আলোর খেলা দেখে হোটেলে ফিরব। যদিও বাতাসটা একটু ঠান্ডা। গরম জামা তো আনা হয়েছে, কাজেই চিন্তা নেই।
 পুরো সন্ধ্যা উদ্যানের বেঞ্চিতে বসে, হাঁটাহাঁটি করে কাটালাম। ঘড়ির কাঁটায় দশটা বাজতে চলল। আমরা রেলিংয়ের কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। দেখলাম হাজারো মানুষ একইভাবে প্রতীক্ষা করছে আতশবাজির। একদম কাঁটায় কাঁটায় শুরু হলো ফায়ারওয়ার্ক। দুমদুম শব্দে আকাশ প্রজ্বলিত করে, জলপ্রপাতকে আলোকিত করে ফুটতে লাগল আতশবাজি। কী যে সুন্দর! অপার্থিব বলে ভ্রম হয়।
পুরো সন্ধ্যা উদ্যানের বেঞ্চিতে বসে, হাঁটাহাঁটি করে কাটালাম। ঘড়ির কাঁটায় দশটা বাজতে চলল। আমরা রেলিংয়ের কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। দেখলাম হাজারো মানুষ একইভাবে প্রতীক্ষা করছে আতশবাজির। একদম কাঁটায় কাঁটায় শুরু হলো ফায়ারওয়ার্ক। দুমদুম শব্দে আকাশ প্রজ্বলিত করে, জলপ্রপাতকে আলোকিত করে ফুটতে লাগল আতশবাজি। কী যে সুন্দর! অপার্থিব বলে ভ্রম হয়।
টরন্টো থেকে ৬৯ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত এই জলপ্রপাত অন্টারিওর নায়াগ্রা অঞ্চলে পড়েছে। জলপ্রপাতে এত জল আসে কোত্থেকে? এমন প্রশ্ন মাথায় আসতেই পারে। কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্রের এই অঞ্চলটিতে বড় বড় হ্রদ রয়েছে প্রচুর। সেগুলোর পানিই এখানে এসে পড়ে। উত্তর আমেরিকার পাঁচটি দৈত্যাকার হ্রদকে একসঙ্গে গ্রেট লেক বলা হয়। সুপিরিয়র, লেক মিশিগান, লেক হুরন, লেক এরি ও লেক অন্টারিও মিলিয়ে পঞ্চহ্রদকে। আর নদী তো আছেই। প্রকৃতির খেয়ালে এই ভূখণ্ডে রয়েছে বিশাল জলাধার, যা থেকে গোটা দুনিয়ার কুড়ি শতাংশ বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করা সম্ভব। উত্তর মেরুর জমাট বরফই এই জলের উৎস। তুষার যুগে নায়াগ্রা অঞ্চলে বরফের ঘনত্ব ছিল গড় আনুমানিক তিন হাজার ফুট। এখন জলবায়ু পরিবর্তন হয়েছে। ভৌগোলিক অনেক কিছুই আগের মতো নেই। তারপরও এই অঞ্চলের আবহাওয়া বিগত পাঁচ হাজার বছরের তুলনায় খুব একটা পাল্টায়নি। জলবায়ুর এই সহযোগিতা ও জলের জোগান প্রায় অপরিবর্তিত থাকায় মানুষ এখনো জলপ্রপাত উপভোগ করতে পারছে।
আমরাও মন ভরে রাতের নায়াগ্রা জলপ্রপাত দেখে ফিরতে শুরু করি অন্যদের মতো। ফিরতি পথে রাস্তার দুধারে রয়েছে হরেক রকমের দোকান। রেস্তোরাঁ আর স্যুভেনির শপ তো রয়েছেই; আরও আছে গেমিং জোন। বিচিত্র আয়োজনে ভর্তি আলো-ঝলমলে দোকান। কোনোটা হরর থিমে তৈরি, কোনোটা আবার হলিউডের থিমে। রাত অনেক হয়ে গেছে, প্রায় এগারোটা। তাই আমরা হোটেলে ফিরলাম। সারা দিনের ক্লান্তি ভর করেছে। আফ্রিকান লায়ন সাফারি থেকে রাত অব্দি নায়াগ্রার আকাশে আতশবাজি, এক দিনে প্রচুর ঘোরা হলো; এবার ঘুম দরকার। আর পরের দিনটা তো রইলই।
 কান্ট্রি ইন হোটেলে সকালের নাশতা শুরু হয় ভোর সাড়ে ছয়টা থেকে। আমরা ঘুম থেকে উঠে আটটা নাগাদ চলে গেলাম ব্রেকফাস্ট ফ্লোরে। বেসিক ব্রেকফাস্ট। ইংলিশ নাশতা যেমন হয় আরকি। আমি সসেজ, ফলফলারি আর দইয়ের ওপর জোর দিলাম। মনে কর্নফ্লেকস আর দুধ। মনি পাউরুটি, চিজ, বাটার আর ফল। চা-কফি ছিল। দেশের বাইরে আমি ফলের রসই পছন্দ করি, চা-কফির বদলে। কারণ, আমি খাই লেবু-মধু দিয়ে বানানো রঙিন চা। এই চা এখানে বানানোর কোনো সুযোগ নেই। কাজেই ফলের রসই উত্তম।
কান্ট্রি ইন হোটেলে সকালের নাশতা শুরু হয় ভোর সাড়ে ছয়টা থেকে। আমরা ঘুম থেকে উঠে আটটা নাগাদ চলে গেলাম ব্রেকফাস্ট ফ্লোরে। বেসিক ব্রেকফাস্ট। ইংলিশ নাশতা যেমন হয় আরকি। আমি সসেজ, ফলফলারি আর দইয়ের ওপর জোর দিলাম। মনে কর্নফ্লেকস আর দুধ। মনি পাউরুটি, চিজ, বাটার আর ফল। চা-কফি ছিল। দেশের বাইরে আমি ফলের রসই পছন্দ করি, চা-কফির বদলে। কারণ, আমি খাই লেবু-মধু দিয়ে বানানো রঙিন চা। এই চা এখানে বানানোর কোনো সুযোগ নেই। কাজেই ফলের রসই উত্তম।
নাশতা খেয়ে আমরা ঠিক করলাম বোটে করে নায়াগ্রা জলপ্রপাতের হর্স-শু ফলসে যাব। ঘোড়ার নালের মতো দেখতে, তাই ওরকম নাম। আসলে হাজার বছর ধরে পানি পড়তে পড়তে ঘোড়ার নালের আকৃতি ধারণ করেছে, আর সেটাই নায়াগ্রার মূল আকর্ষণ। চমৎকার রোদ উঠেছে। আমরা হাঁটতে হাঁটতেই চলে গেলাম ফেরির টিকিট কাউন্টারে। তিনজনের জন্য টিকিট কেটে লাইন ধরে উঠে পড়লাম ফেরিতে। ওঠার আগে ধরিয়ে দেওয়া হলো পাতলা পলি, যেন জামাকাপড় পানির ঝাপটায় ভিজে না যায়। আমরা তিনজন ঠিকঠাক সেটা পরে নিলাম। অনেকটা বর্ষাতির মতোই।
ফেরিতে করে ঘোড়ার নালির কাছে নিয়ে যাওয়ার চলটি শুরু হয় ১৮৪০ সালে। এই ভ্রমণকে ওরা আদর করে বলে ‘মেইড অব দ্য মিস্ট’। আমরা বেশ উত্তেজনা নিয়ে ফেরিতে চড়লাম। বেশ লাগছে। জলপ্রপাত দেখছি। প্রথমে যুক্তরাষ্ট্রের অংশটি। সেখান থেকে পানির ঝাপটা এসে লাগছে। মৃদু ঝাপটা। কিন্তু একটু পর কী হতে যাচ্ছে, সেটা আমরা আগে ভাবতেই পারিনি। যখন ফেরি হর্স-শুয়ের কাছাকাছি গেল, ওরে বাবা, মনে হলো তীব্র বৃষ্টিপাতের ভেতর পড়ে গেছি, আর সেকি বাতাস! সামান্য বর্ষাতি দিয়ে কাপড় ঢাকা যাচ্ছে না। ভিজেটিজে একাকার অবস্থা। আমাদের ভুল হয়েছে। সুইমিংপুলের জন্য কাপড় এনেছিলাম, সেগুলো পরে আসা উচিত ছিল। যাহোক, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের এত কাছে গিয়ে প্রকৃত রূপকে অবলোকন করা যায় না। এই সত্য নতুন করে আবিষ্কার করলাম। পানির ঝাপটার চোটে চোখই ভালো করে খোলা রাখা যাচ্ছে না। আমি শুধু ভয় পাচ্ছিলাম ফেরির ইঞ্জিন যদি, ধরা যাক বন্ধ হয়ে গেল, আর আমরা জলপ্রপাতের ঠিক নিচে চলে গেলাম, সাধের জীবন শেষ!
ভালোয় ভালোয় ফেরি তার নাক ঘোরাতে শুরু করল। একটু দূরে আসতেই নায়াগ্রা জলপ্রপাতের শক্তি ও সৌন্দর্যকে বোঝা গেল হাড়ে হাড়ে। মনের অবস্থা তো আরও খারাপ। ওর দিকে তাকিয়ে দেখি চুলটুল ভিজে চুপচুপ করছে। আমি শুধু ওর হাত ধরে রেখেছিলাম, যেন পিছলে পড়ে না যায়। অন্য হাতে সামলেছি আমার পলিথিন। ভয়ংকর সুন্দর অভিজ্ঞতা বলতে যা বোঝায় আরকি, সেটা এখানেই হলো। ঘাটের কাছে ফিরে এলো ফেরি। সব মিলিয়ে কুড়ি মিনিটের রাইড। যখন ডাঙায় পা ফেললাম, তখন আমরা তিনজনেই ভেজাকাক। ঘাটের পাশেই একটি খোলা চত্বর, চেয়ার-টেবিল পাতা। আমরা সেখানে মিষ্টি রোদে বসলাম। পায়ের জুতো খুলে শুকাতে দিলাম রোদে। আশ্চর্য! রোদটা অসম্ভব ভালো লাগছিল। আমরা আবারও ভিন্ন ধরনের পুটিন অর্ডার করলাম। আর ব্যাগে করে আনা হয়েছিল আপেল, চিপস ও পানীয়। সেসব খেলাম। গল্প করলাম। সামনে জগদ্বিখ্যাত জলপ্রপাত। তার সৌন্দর্য দেখতে দেখতে গায়ের জল শুকালাম। ঘণ্টা দুয়েক থেকে আমরা গাত্রোত্থান করলাম। ওপরে স্যুভেনির শপের পাশে একটা বসার জায়গা রয়েছে। সেখান থেকে ভিন্ন কোণে জলপ্রপাত দেখা যায়। আমরা ওখানে গিয়ে আইসক্রিম কিনে বসলাম আবার। তারপর দুচোখ ভরে প্রকৃতির অপার লীলা দেখলাম।
 দুপুরে খেতে গেলাম সেই ভারতীয় রেস্তোরাঁয়। ঠিক দুপুর বলা যাবে না। ততক্ষণে ঘড়িতে তিনটা বেজে গেছে। খাওয়াদাওয়া সেরে আর হোটেলে ফিরলাম না। মনে সেই আগের দিন থেকে বায়না ধরেছে, সে গেমিং জোনে খেলবে। অগত্যা তাকে নিয়ে বিকেলে ঢুকতে হলো একটি বিশাল গেমিং জোনে। মন ভরে ঘণ্টা দেড়েক নানাবিধ খেলা সে খেলল। আমরা দুজন তার দর্শক। খেলা শেষ হলো। বেরিয়ে আবারও কিছু ঘোরাঘুরি। আর ঘণ্টা দুয়েক পর আতশবাজি পোড়ানো হবে। আর আজই আমাদের শেষ রাত কানাডায়। ঠিক করলাম দ্বিতীয় রাতেও আতশবাজির হুল্লোড় দেখব। সময় কাটাতে ঢুকলাম স্টারবাকসে। আমি নিলাম আর্লগ্রে টি। আমার সব সময়ের পছন্দ। আর মা-ছেলে নিল কফি।
দুপুরে খেতে গেলাম সেই ভারতীয় রেস্তোরাঁয়। ঠিক দুপুর বলা যাবে না। ততক্ষণে ঘড়িতে তিনটা বেজে গেছে। খাওয়াদাওয়া সেরে আর হোটেলে ফিরলাম না। মনে সেই আগের দিন থেকে বায়না ধরেছে, সে গেমিং জোনে খেলবে। অগত্যা তাকে নিয়ে বিকেলে ঢুকতে হলো একটি বিশাল গেমিং জোনে। মন ভরে ঘণ্টা দেড়েক নানাবিধ খেলা সে খেলল। আমরা দুজন তার দর্শক। খেলা শেষ হলো। বেরিয়ে আবারও কিছু ঘোরাঘুরি। আর ঘণ্টা দুয়েক পর আতশবাজি পোড়ানো হবে। আর আজই আমাদের শেষ রাত কানাডায়। ঠিক করলাম দ্বিতীয় রাতেও আতশবাজির হুল্লোড় দেখব। সময় কাটাতে ঢুকলাম স্টারবাকসে। আমি নিলাম আর্লগ্রে টি। আমার সব সময়ের পছন্দ। আর মা-ছেলে নিল কফি।
একটি স্যুভেনির শপের ভেতরেই কফি শপটা। কাজেই আমরা একটু গল্প করি, আবার একটু দোকানে ঢুঁ মারি। টুকটাক এটা-সেটা কিনি। ঠিক পৌনে দশটা বাজলে হাঁটা শুরু করলাম নায়াগ্রা ফলসের দিকে। শেষ রাতের আতশবাজি। সেই আগের মতোই, ঠিক ঘড়ি ধরে শুরু হলো আলোর ঝলকানি। জলপ্রপাতের পানিতে আলো ফেলে সেটিকে করা হচ্ছে নানা রঙে রঞ্জিত। আর আকাশে ফুটছে পটকা। ফুলের মতো ছড়িয়ে-ছড়িয়ে তারা পড়ছে পানিতে। রাতের এই অপরূপ মনকাড়া দৃশ্য বেশিক্ষণ নয়, স্থায়ী হয় মাত্র পাঁচ মিনিট। আর এই মিনিট পাঁচেকের জন্যই রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে পড়ে লাখো মানুষ। অনেক বৃদ্ধ আসেন শুধু ওপার, মানে যুক্তরাষ্ট্র থেকে। বাঙালি এক যুগলকেও দেখলাম। বাংলায় কথা বলছিল। ভারতীয় পর্যটকও আছে। আছে ইউরোপীয় ভ্রমণপিপাসু মানুষ। রাতের এই মুহূর্ত যে কাব্যিক ব্যঞ্জনা তৈরি করে তা বর্ণনাতীত। কানাডা আসার আগে ননীগোপাল দেবনাথের একটি বই ‘বৈচিত্র্যময় কানাডা: প্রাগৈতিহাসিক থেকে বর্তমান’ উল্টেপাল্টে এসেছিলাম। সেখানে নায়াগ্রা জলপ্রপাতের সৌন্দর্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে দেবনাথ লিখেছেন: ‘রবীন্দ্রনাথ এর পাড়ে এসে বসলে তাঁর কলমের কালি নিঃশেষ হয়ে যেত নিশ্চয়।’
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নায়াগ্রা পর্যন্ত না এলেও, কানাডা সফর ঠিকই করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের ভ্যাঙ্কুভার ভ্রমণ হয় ১৯২৯ সালে। তিনি এসেছিলেন শিক্ষা শীর্ষক বক্তৃতা দিতে। ভ্রমণ শেষে ভারতে ফিরে গিয়ে ‘অভিযান (কানাডার প্রতি)’ শিরোনামে একটি কবিতাও লিখেছিলেন। সেটির অনুবাদ কবি করেছিলেন ইংরেজিতে, যা সম্প্রচারিত হয় অটোয়া রেডিওতে, ১৯৩৬ সালে। কবিতার দুটি পঙ্ক্তি এমন: ‘দুর্গমেরে পেরোতে হবে বিশ্বজয়ী রথে,/ পরান দিয়ে বাঁধিতে হবে সেতু।’
 বিশ্বকে জয় করার মতো রথ আমাদেরই বানাতে হবে এবং সেটি দিয়ে দুর্গমকে পেরোনোর দুঃসাহসী অভিযান আমাদেরকেই করতে হবে। তবেই বিশ্ববাসীর সঙ্গে আত্মিক সেতু তৈরি করা সম্ভব। কিন্তু সেই বিশ্বজয়ী রথ বানানোর যে আয়োজন রাষ্ট্রের করে দেওয়ার কথা, সেটি কি আছে আমাদের দেশে? নেই বলেই কি বছর বছর অজস্র তরুণ-তরুণী এই কানাডায় চলে আসছেন না? দেশ ছেড়ে কানাডা শুধু নয়, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়াতে যে যুবশক্তি চলে যাচ্ছে, সেদিকে কি আমরা গুরুত্বের সঙ্গে নজর দিয়েছি কখনো? কানাডায় যে সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশি রয়েছেন এবং আরও আসতে যাচ্ছেন, তাতে হয়তো এই কানাডার একটি রাজ্য ভরেই যাবে বাংলাদেশিতে। কিন্তু তাতে বাংলাদেশের কোনো উপকার হবে কি? এসব প্রশ্ন মাথায় নিয়ে, পরের দিন ২২ সেপ্টেম্বর আমরা টরন্টো আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের দিকে রওনা দিই।
বিশ্বকে জয় করার মতো রথ আমাদেরই বানাতে হবে এবং সেটি দিয়ে দুর্গমকে পেরোনোর দুঃসাহসী অভিযান আমাদেরকেই করতে হবে। তবেই বিশ্ববাসীর সঙ্গে আত্মিক সেতু তৈরি করা সম্ভব। কিন্তু সেই বিশ্বজয়ী রথ বানানোর যে আয়োজন রাষ্ট্রের করে দেওয়ার কথা, সেটি কি আছে আমাদের দেশে? নেই বলেই কি বছর বছর অজস্র তরুণ-তরুণী এই কানাডায় চলে আসছেন না? দেশ ছেড়ে কানাডা শুধু নয়, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়াতে যে যুবশক্তি চলে যাচ্ছে, সেদিকে কি আমরা গুরুত্বের সঙ্গে নজর দিয়েছি কখনো? কানাডায় যে সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশি রয়েছেন এবং আরও আসতে যাচ্ছেন, তাতে হয়তো এই কানাডার একটি রাজ্য ভরেই যাবে বাংলাদেশিতে। কিন্তু তাতে বাংলাদেশের কোনো উপকার হবে কি? এসব প্রশ্ন মাথায় নিয়ে, পরের দিন ২২ সেপ্টেম্বর আমরা টরন্টো আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের দিকে রওনা দিই।
সকাল সকাল তারেক ভাই চলে এসেছিলেন হোটেলে। তিনিই আমাদের নামিয়ে দেন এয়ারপোর্টে। চমৎকার সময় কাটল কানাডায়। তারেক ভাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিলাম। আর কয়েক ঘণ্টা বাদেই দুবাইগামী বিমানে উঠব। দুবাই থেকে ঢাকা। বায়ুরথে উঠতে উঠতে ভাবছিলাম, বিশ্বজয় করার মতো ‘রথ’ বা কর্ম কি আমরা একেবারেই রচনা করিনি? স্বীকৃতি মিলেছে কি?
ছবি: লেখক ও ইন্টারনেট